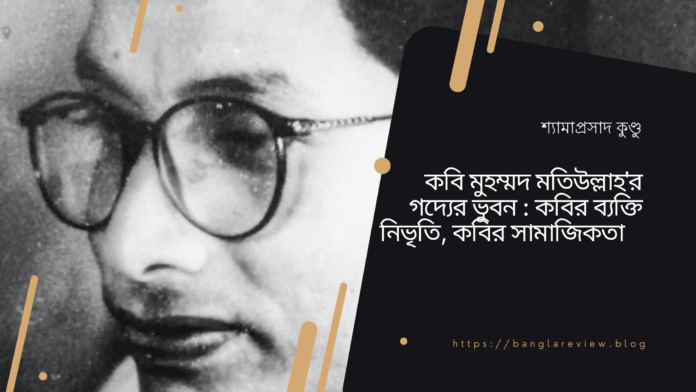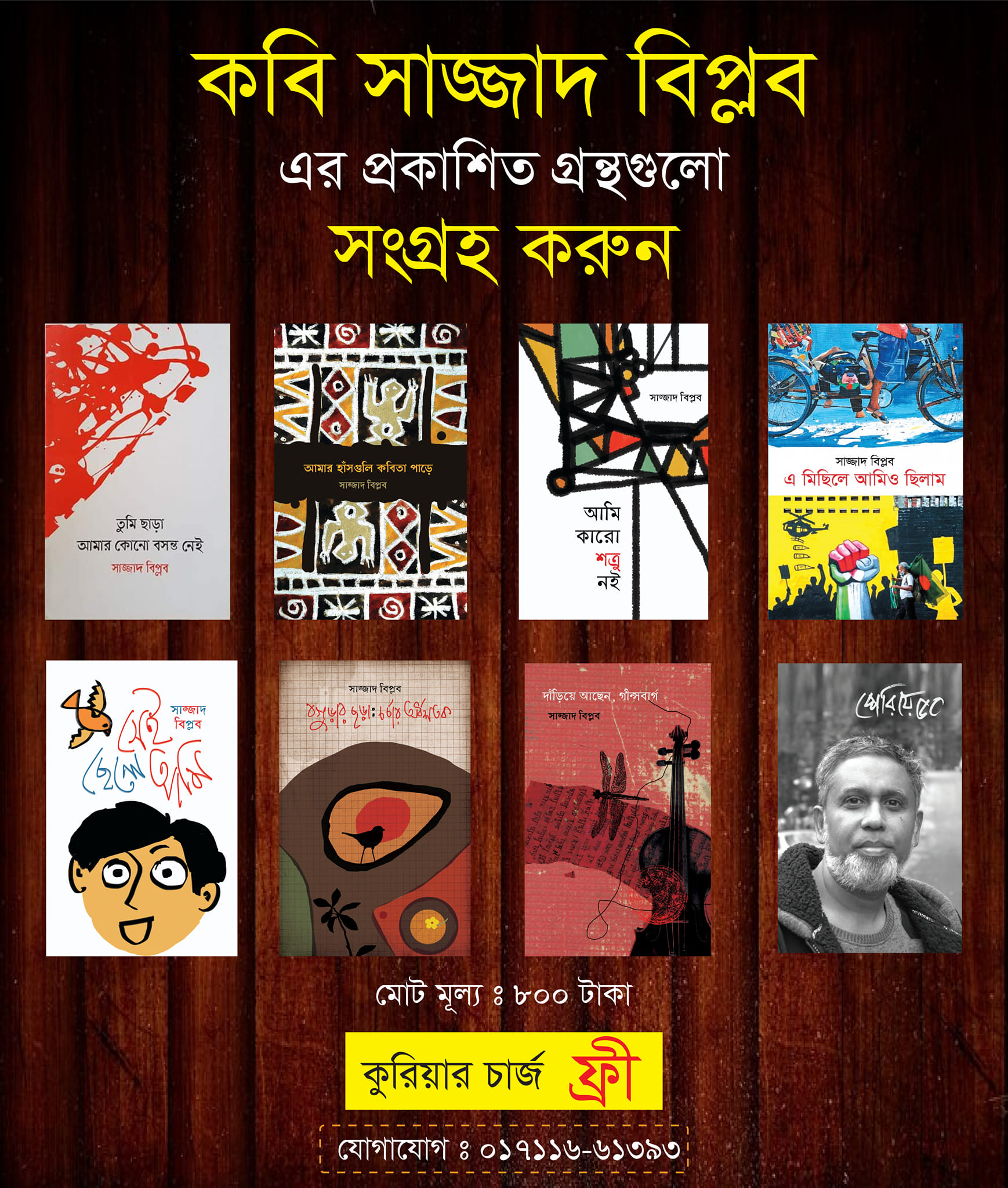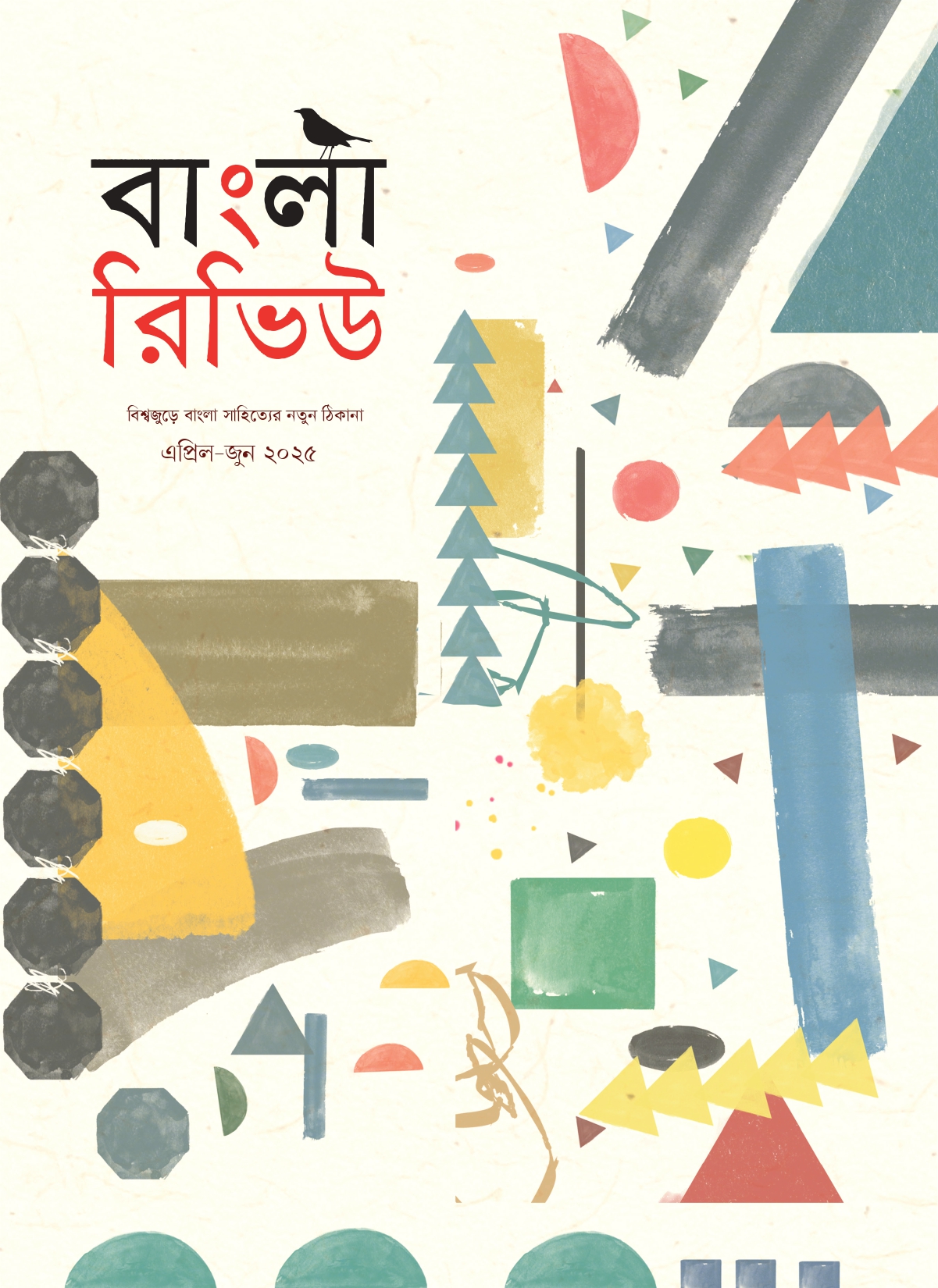শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু
গদ্য ও কবিতার মধ্যে সীমারেখা কোনখানে টানা যাবে? টানা কি যাবে? আছে কি সত্যিই এমন কোনো প্রান্তসীমা যেখানে পৌঁছে বলা যাবে এই গণ্ডী কেটে দেওয়া হোল-এর এপারে গদ্যের খটমট বাস্তব যুক্তিনির্ভর আটপৌরে পৃথিবী আর এই খড়ির গণ্ডীর ওপারে ধুসর মায়াময় স্বপ্নিল কবিতার ভুবন? বলা যাবে? বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের হাত ধরে বাংলা গদ্য যখন রীতিমত ঋজু ও সবল হয়ে উঠলো তখন সদর্পে ঘোষণা রটে গেল যে বাংলাভাষা এবার সাবালকত্ব অর্জন করেছে; এখন জ্ঞানবিজ্ঞানের দুরূহতম আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও যুক্তিবিস্তার এইভাষাতেই করা যাবে। কবিতা থাকুক তার কল্পনার আবেশী স্বপ্নের জগতে। গদ্য ও কবিতার জগত ভিন্ন; এ দুয়ের মধ্যে মেলবন্ধন অসম্ভব । সত্যই কি অসম্ভব এই মেলবন্ধন? আমার তো তা মনে হয় না । মতির ( আমি এই নামেই কবিকে সম্বোধন করি; আশাকরি কবি রুষ্ট হবেনা না) গদ্যের বই পড়তে পড়তে আরো একবার এই কথাগুলো মনে পড়ে গেলো এবং বলতে ইচ্ছে হোল।
আমি কবিতার নিয়মিত পাঠক। প্রতিদিন প্রিয় কবিতার কাছে ফিরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। অবশ্যই কিছু প্রিয় কবি আছেন আমার পছন্দের তালিকায়। মুহম্মদ মতিউল্লাহ সেই তালিকায় প্রথম সারিতেই আছেন। মতির গদ্য তেমনভাবে পড়া হয় নি এতদিন। মতি সব্যসাচী জানতাম। তার প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা দেখেছি আমি। নিয়মিত গদ্য লেখে মতি। আমার পড়া হয় নি এতদিন সে আমার দুর্ভাগ্য। অনেক অনেক দিন ভালো গদ্য পড়ার সুযোগ পাই না। অহনা বিশ্বাস আমার একজন প্রিয় লেখিকা। ওর গদ্যের অনুরাগী পাঠক আমি অনেকদিন যাবৎ । নলিনী বেরা আর একজন প্রিয় লেখক। অম্লান দত্ত প্রিয় প্রবন্ধকার। মতির গদ্য পড়ার সুযোগ আমার ঘটে নি তেমন নিবিড়ভাবে। অথচ গদ্যপড়তে আমি খুব ভালোবাসি। আমার সামান্য লেখালেখিও মূলতঃ গদ্যে। বাংলায়। ঠেকায় পড়লে কখনো সখনো আটপৌরে ইংরেজি লিখতে বলতে হয় । ভালো লাগে না কারণ স্বচ্ছন্দ বোধ করি না।
বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিভুতিভূষণ এবং সত্যজিৎ রায় কতখানি প্রিয়। আরো পুরোনো দিনের কথা বলতে গেলে অবন ঠাকুরের কথা না বললে আমার পাপ লাগবে। রবীন্দ্রনাথ চারটি মাত্র শব্দে অবনীন্দ্রনাথকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন একজন গদ্য লেখক হিসেবে। “অবন ঠাকুর ছবি লেখেন”। এর অতিরিক্ত আর কিই বা বলার থাকতে পারে? এ প্রসঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলবো না । ঠাকুর সকল আলোচনার সীমানার বাইরের মানুষ।
সম্প্রতি মতি আমাকে দুখানি প্রবন্ধ্ সঙ্কলন পড়ার জন্য পাঠিয়েছে। এ ছাড়াও আরো কিছু অন্য রকমের বই। সেসব কথা থাক এখানে। যে দুটি প্রবন্ধ সঙ্কলনের কথা বলছি আমি তা হোল– কবির ব্যক্তি নিভৃতি/ কবির সামাজিকতা। এবং আলোক সরকার স্মারক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি মতি সম্পাদনা করেছেন। আলোক সরকার আমারও প্রিয় কবি। অনেক বছর আগে ‘ভাবনাচিন্তা’ শারদ সংখ্যায় পরপর দুবছর তিনি দুটি কবিতা পাঠিয়ে আমাদের ঋণী ও সমৃদ্ধ করে গেছেন। এই স্মারক গ্রন্থটিতে যারা লিখেছেন তাঁরা বাংলা সাহিত্যের এক এক জন দিকপাল। মাইলফলক। এই স্মারক গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই। ‘কবির ব্যক্তিনিভৃতি/ কবির সামাজিকতা’ গ্রন্থটি সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা বলার জন্যই এই কথাগুলির অবতারণা ।
আলোচ্য গ্রন্থটিতে মোট ১১টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন কাল-খণ্ডে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে লেখক জানিয়েছেন। সব প্রবন্ধগুলিই কবিতা এবং কবি বিষয়ক। ব্যক্তি কবিরুল ইসলাম ও তার কবিতা বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। কবিরুলদা সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। আমাদের সাথে বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের বাড়িতে রাত্রি যাপন করেছেন মাঝেসাঝে। এমন আন্তরিক সদালাপী সুভদ্র মানুষ খুব কমই চিনিজানি। আমাদের মধ্যে একটা মজা প্রচলিত ছিল। যখনই আসতেন আমি হেসে জিজ্ঞাসা করতামঃ “নিশ্চয়ই নতুন বই বেরিয়েছে এবং আপনি এখন ফিরিওয়ালা?” কবিরুলদা প্রথমে প্রবলভাবে এ কথা অস্বীকার করার ব্যর্থ চেষ্টা করতেন। পরে চলে যাবার সময় হলে খান দশেক বই বেরোতো তার ঝোলা থেকে। কবিতার বই বিক্রি করা যে কত কঠিন বুঝতে পারতাম। মানুষটা খুব আপন ছিলেন আমাদের শুধু নয় যাদের সংগে মিশেছেন তাদের সকলেরই। আমার অনেক বন্ধু সিউড়ি কলেজে তার ছাত্র ছিল। খুবই জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন কবিরুলদা। মতি অতি চমৎকারভাবে কবিরুলদার কাব্যজগৎ ও ব্যক্তি মানস নিয়ে লিখেছে। কবিরুলদার কবিতা বুঝতে সাহায্য করবে মতির আলোচনা পড়লে। আমিও সমৃদ্ধ হলাম।
আর একজন কবির কবিতা নিয়ে এবং অবশ্যই কবিকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছে মতি । কবি সুব্রত চক্রবর্তী। বিজ্ঞানের অধ্যাপক এই একান্ত নিভৃতলোকে বাস করা কবির সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সুযোগ হয়েছিল আমার সেকথা ভাবলে মন আবেগী ও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। ‘ভাবনাচিন্তা’ শারদ সংখ্যায় সুব্রতাদার কবিতা ছাপার সুযোগ হয়েছিল আমাদের।
এসব কথা বলার উদ্দেশ্য নয় আমার। আমি মতির গদ্যের মাধুর্য ও কাব্যময়তা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম। ‘গদ্যের কাব্যময়তা’ শব্দবন্ধটি কি খুবই বেসুরো শোনাচ্ছে শ্রবণে? আসলে আমি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছি। অবনীন্দ্রনাথে রাজকাহিনী পড়তে পড়তে আমি খুব ধন্ধে পড়েছিলাম। আমি কি কবিতা পড়ছি? আমি কি গদ্য পড়ছি? কহলিল গ্রীব্রানের (জিব্রান?) লেখা পড়তে পড়তে (ইংরেজি অনুবাদে) আমার এরকমই মনে হোত। আল্বেয়ার ক্যামুর রচনা ইংরেজি অনুবাদে পড়েছি। শুধু গল্প উপন্যাস নয় ক্যামুর প্রবন্ধ পড়তে পড়তেও মনে হয়েছে কবিতা ও গদ্যের সীমারেখা মুছে মুছে গেছে অনেক সময়। শেষ অবধি এই অমীমাংসিত প্রশ্নটাই মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকেঃ গদ্যের ভাষা ও কবিতার ভাষার মধ্যে সীমারেখা বলে কিছু আছে নাকি? অনেকে ‘গদ্যকবিতা’ বলে একটা নতুন রচনা শৈলীর উল্লেখ করেন। আমার কেমন থতমত লাগে। ‘শেষের কবিতা’ আমার কাছে কবিতাই। ( সেই রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির হয়ে গেলেন অনিবার্যভাবেই।)। মতির গদ্য পড়তে পড়তে মাঝেমাঝেই আমার মনে হয়েছে মতি বুঝি বিলম্বিত চালে কবিতাই লিখেছে। দুএকটা উদাহরণ দিতে ইচ্ছে।
রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার পরিচয় ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতাটি কন্ঠস্থ করার মাধ্যমে। তখন আমি চতুর্থ শ্রেণীর অমনোযোগী ও স্কুলপালানো ছাত্র। বুঝতাম না কিছুই কিন্তু কবিতাটি সঙ্গে রয়েই গেল চিরদিনের জন্য। মতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হচ্ছে গীতাঞ্জলির সূত্রে। মতির কথাতেই বলিঃ
“শৈশবে একটি নিবিড় গ্রামীণ পরিবেশে এক নিস্তরঙ্গ ভাবোচ্ছ্বাস্ময় একটি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলি’র সাথে আমার প্রথম পরিচয়। স্কুলের নীচু ক্লাশের সিক্স কিম্বা সেভেনের ছাত্র তখন।” কিভাবে এই পরিচয় ঘটেছিল সে আখ্যানের বিবরণ এখানে অপ্রয়োজনীয়। শৈশবের সেই পরিচয় কিভাবে মতির মনের গহনে বীজাকারে রয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে কিভাবে গীতাঞ্জলির মূল সুরটি তার কানে ধরা পড়েছিল সেই কথা কি আশ্চর্য মায়াময়তা ও বোধের গভীরতা দিয়ে লেখক আত্মস্থ করেছিলেন তারই ভাষারূপ মতির ‘তোরা শুনিস কি তার পায়ের ধ্বনি’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিধৃত। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ‘গীতাঞ্জলি’র গভীর অনুরাগী আমি কোনোকালেই ছিলাম না। আমার পছন্দ ভিন্নতর। গীতাঞ্জলির কিছু রচনা আমার খুব প্রিয় কিন্তু সামগ্রিকভাবে আই গীতাঞ্জলির প্রতি মোহমুগ্ধ হতে পারিনি। মতির এই আলোচনাটি পড়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি পুনরায় গীতাঞ্জলির কাছে ফিরে যাবো। নতুন করে অনুভব করার চেষ্টা করবো রবীন্দ্রনাথের পূজা ও সমর্পণকে গীতাঞ্জলির রচনার মাধ্যমে। মতি, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই অশেষ। মতি লিখেছেন কবিরের দোঁহা ও রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির রচনাগুলির মধ্যে মূল পার্থক্যের সীমারেখা এই ভাষায় :
“কিন্তু কি আছে কবীরের দোহায়? কবীর মূলত এবং প্রধানত ভক্ত। কবিত্ব তাঁর গৌণ অস্তিত্ব। ভক্তের ভক্তির নির্যাসটুকু বড় একরূপতায় ফুটে আছে কবীরের দোঁহায়। আর রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ প্রধানত রূপরসগন্ধঋদ্ধ এক কবির সৃষ্টি। কবীরের দোঁহায় ভক্ত আকূল-আত্ম নিবেদন করেন। একপক্ষীয় সে নিবেদন। আত্মনিবেদিনের আত্মহীনতায় তার সার্থকতা। ‘গীতাঞ্জলি’র গীতিকবিতায় আঁচে আত্মনিবেদন সহজ শুভ্রতা,প্রেমের সাতসমুদ্র;প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি নিয়ে ভক্তেরও দাবী, আছে আকাংখ্যা প্রত্যাশা। ‘গীতাঞ্জলি’র কবি কবিরের দোঁহার মত আত্মবিস্মৃত নন। রূপদক্ষ কবির হাতে নির্মিত হয়েছে ‘গীতাঞ্জলি’র গানের ভুবনখানি।” উদ্ধৃতি দীর্ঘতর করতে চাইছি না । কবিতা অনুরাগী পাঠকপাঠিকাদের অনুরোধ করবো সংগ্রহে না থাকলে বইটি খুঁজে বার করে নিন। আমি শুধু আরো কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনামের উল্লেখ করতে চাই । একজন স্বভাবকবি যখন গদ্য লেখেন তার গদ্যও কিভাবে কাব্যসুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে তারই উদাহরণ এগুলি।
জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দাস ও তার কাব্যের ভুবন নিয়ে লেখা প্রবন্ধটির নাম : ’শেফালি গাছ, নদীপাড়ের ঝাউবীথি, কুসুমকুমারী দাস : দিনলিপির কাব্যবাণী।
দুখি মানুষের মায়াবী দর্পণ : সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতা
নাসের হোসেন : বর্ণের পাশে থাকে বর্ণহীনতা
বইটির প্রকাশক- বার্ণিক প্রকাশনী , বর্ধমান। (যোগাযোগ-৮৩৯১০৫৮৫০১) এরা ডাকে বই পাঠান। মূল্য-১৫০ টাকা।