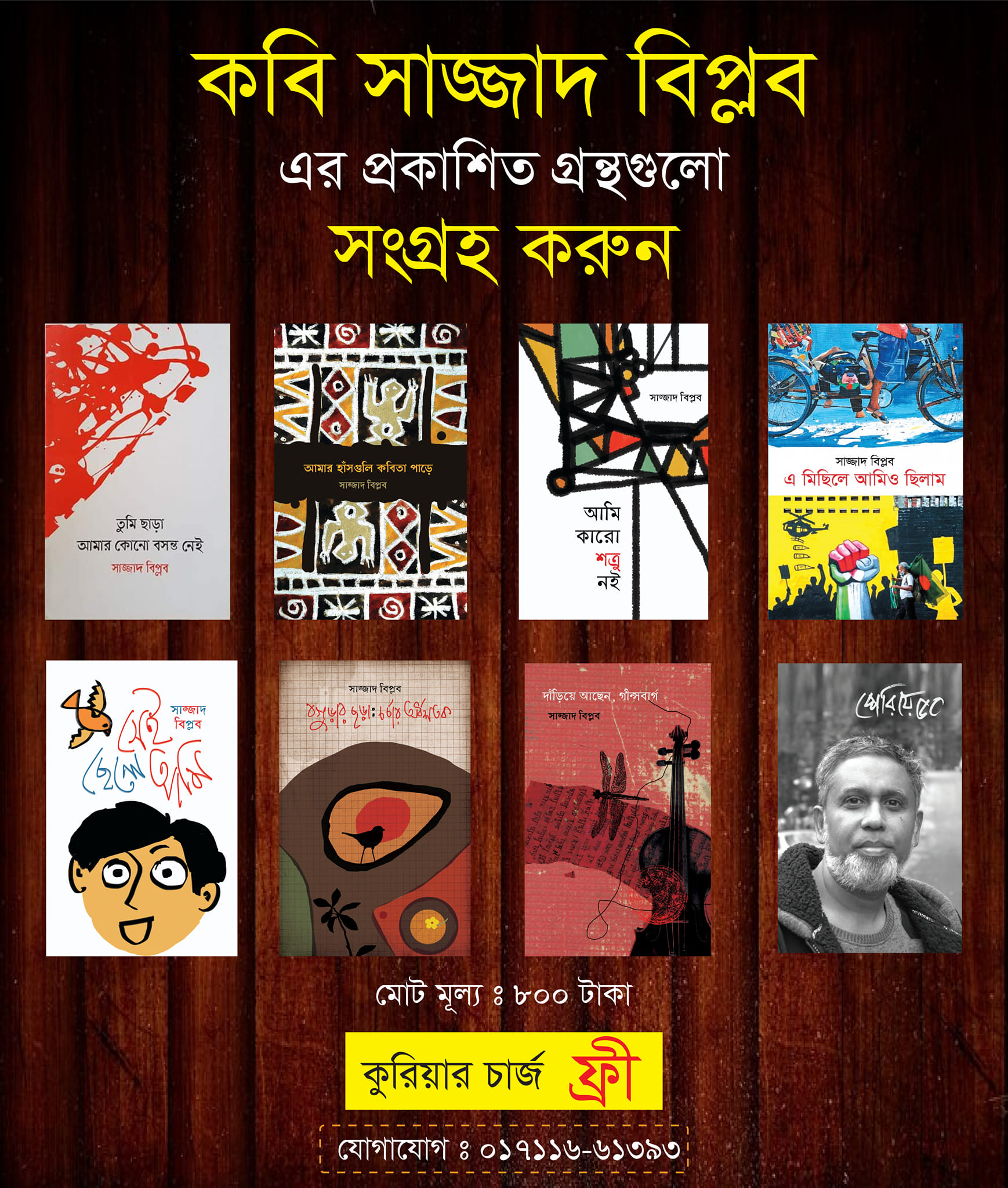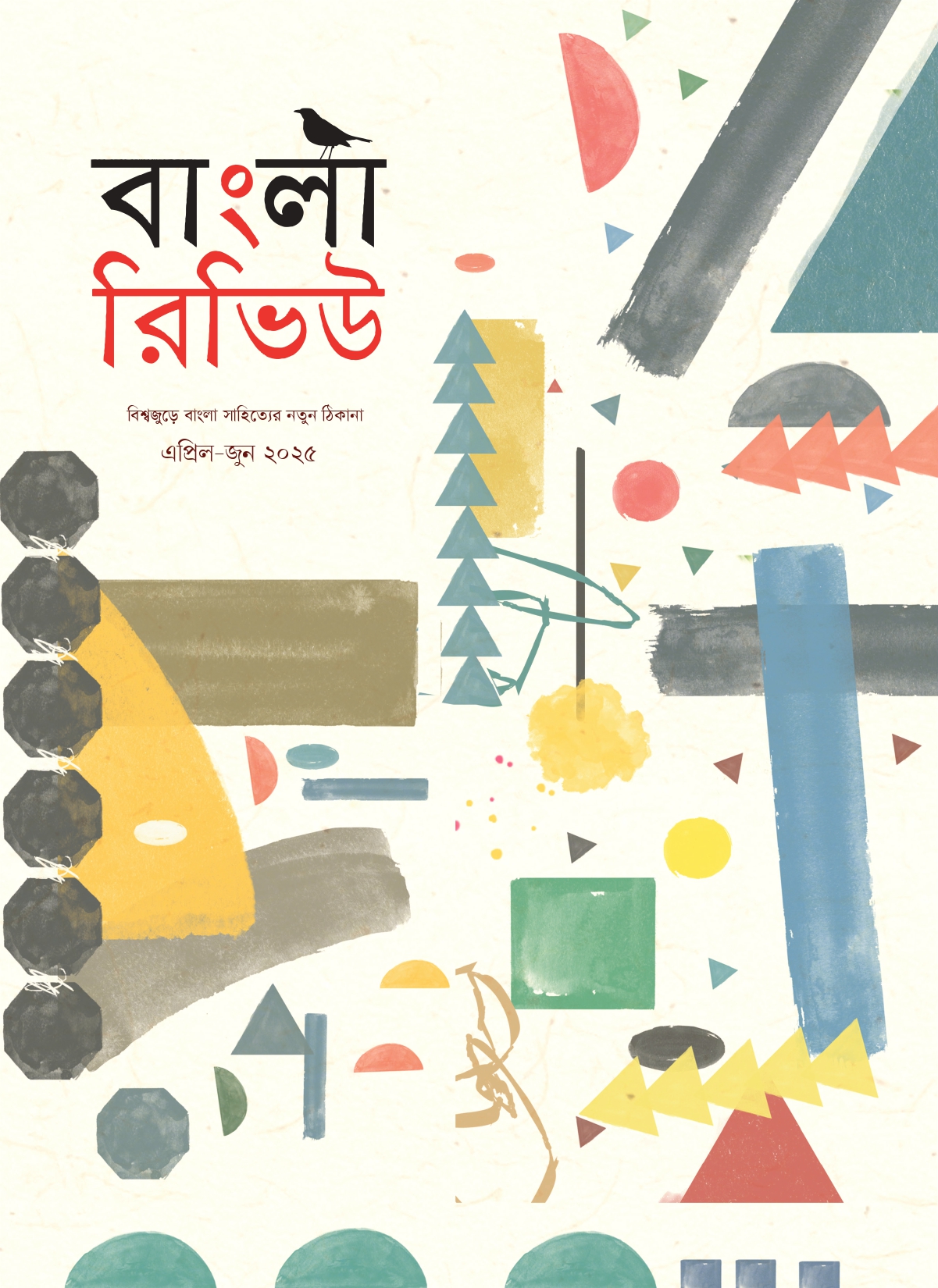তৈমুর খান
১৫
জোরে জোরে সাইকেলের বেল্ বাজাই
—————————————————–
রামপুরহাট কলেজ থেকে অনার্স পাশ করেও এম এ পড়ার জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ নিতে পারছিলাম না। বার কয়েক রবীন্দ্রভারতী থেকে ফিরে এসে সব আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। শহরে থেকে পড়াশোনা করলে অনেক খরচ। বাড়িতে দিশেহারার মতো অভাব। সুতরাং ও পথে আর না যাওয়াই ভালো। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ প্রায় বছর তিনেক রামপুরহাটে কয়েকটি টিউশন পড়াতে শুরু করেছি। সারাদিন টিউশন করে বিকেলবেলা বাড়ি ফিরি অবেলার হাটে কিছু সবজিপাতি কিনে। পরিচয় হয় রামপুরহাট হাটতলায় ধূলিকণা নামে এক শাঁখা-সিঁদুরের দোকানদারের সঙ্গে। তিনি শঙ্করলাল রায়। উত্তরবঙ্গে কুচবিহার জেলার কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চার বছর বয়সেই পিতা-মাতাকে হারিয়ে বাউণ্ডুলের মতো পথেঘাটে, হাটেবাজারে, শ্মশানে-মশানে জীবন কাটান। বহুদিন ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে কোনো তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে তারাপীঠে এসে পৌঁছান। সেখানকার শ্মশানে শবদেহ বহন করা খাটিয়ার বাঁশগুলি থেকে নানা রকম আসবাব তৈরি করে বিক্রি করেন। এমনি করে করে একদিন রামপুরহাটে ওই ধূলিকণা দোকানের মালকিনের সংস্পর্শে আসেন। সেই ভদ্রমহিলারও সাতকুলে কেউ ছিলেন না। খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা যত্ন করেন এবং শেষ জীবনটা তাঁর নিরীক্ষণেই কাটে। তখন এই দোকানটি তিনি তাকেই সম্প্রদান করে যান। তখন থেকেই এই রামপুরহাটে তাঁর স্থিতি। অনেকটা বয়স পেরিয়ে গেছে তখন। বিয়ে-শাদী কিছুই হয়নি। তড়িঘড়ি হাওড়ার একটা উদ্বাস্তু মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কার্যটিও সম্পন্ন হয়। বছর কয়েকের মধ্যেই ৪-৫ টি সন্তান তাঁর সংসারে আসে। ধীরে ধীরে তারা বড় হতে থাকলে সংসার খরচও বেড়ে যায়। এদিকে দোকানের আয়ও কমতে থাকে। কিন্তু তবুও ‘পদাতিক’ নামে একটি দেয়াল পত্রিকা একক প্রচেষ্টায় প্রকাশ করতেন। দোকানে বসেই পত্রিকাটির অলংকরণ করতেন। রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে এবং পোস্ট অফিসে তা টাঙিয়েও দিতেন। রবিবারের দিন একটা পুরনো সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহে। জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের স্থানগুলি যেমন চিহ্নিত করতেন, তেমনি বীরভূমের সুফি সাধকরা কোথায় কোথায় এসেছেন এবং কী তার চিহ্ন রয়েছে সেসব নিয়ে অনুসন্ধান চলত। ‘বীরভূম নামের উৎস সন্ধানে’ নামে একটি বইও লিখেছিলেন, যেটি কাঞ্চিদেশ প্রকাশ করেছিল। আবার রামপুরহাটের ‘কাঞ্চিদেশ’ পত্রিকার নামকরণও তিনি করেছিলেন।
টিউশনি করে হাটতলা যাবার পথেই তাঁর দোকানের সামনে অন্তত একঘন্টা না বসলেই নয়। তিনি এক প্রকার ভালবেসেই কাছে ডাকতেন। নতুন সাহিত্যের খবরা-খবর দিতেন। আগামী রবিবার কোথায় যাবেন তার পরিকল্পনা শোনাতেন। কোনো সাঁওতাল রমণী তাঁর দোকানে এলে তাদের সঙ্গে অনর্গল সাঁওতালি ভাষাতেই কথা বলতে পারতেন। কোনো বিদেশি পর্যটক এলে তাদের সঙ্গে সমানতালে ইংরেজিতেও কথা বলতেন। অবাক হয়ে ভাবতাম, মানুষটা এত কিছু জানলেন কী করে? কবিতা লিখে তাঁর সামনে পাঠ করলেই, তিনি শুনেই বলে দিতেন কোথায় ছন্দপতন ঘটেছে। কোন শব্দটা পরিবর্তন করা দরকার। কবিতাটিতে কার প্রভাব আছে। কালিদাসের ‘মেঘদূতম’ সলমান রুশদির ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ এবং মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’ থেকে তিনি নানা উদ্ধৃতি বলতে পারতেন। এসব কখন পড়লেন?
কথা শুনে তিনি হাসতেন।জয় গোস্বামী, পিনাকী ঠাকুর, শঙ্খ ঘোষ তাঁরা যে অত্যন্ত ছন্দ সচেতন কবি এবং কত নিখুঁত মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহার করতে পারেন তা আবৃত্তি করে শোনাতেন। শুনতে শুনতে সময় জ্ঞান আর থাকত না। তখন গুরুগম্ভীর গলায় পাশের চায়ের দোকানদারকে ডাক দিতেন—
“নারায়ণ, দুটো চা!”
চা পর্ব শেষ হলে লাল সুতোর বিড়ি বের করে দিতেন। লাইটারে আগুন জ্বেলে বলতেন— “টানো!”
৭১ বছরের মানুষ ২৪-২৫ বছরের যুবককে এইভাবেই উষ্ণতায় দীক্ষিত করতে থাকেন। কবিতার ছন্দ যা এতদিন ডিগ্রি অর্জন করেও শিখতে পারিনি, তা অতি সহজেই শিখে ফেলি। আশ্চর্য! মানুষটি কোনোদিন স্কুলে যাননি। কোনো সার্টিফিকেট নেই তাঁর। জীবনের নব্বই শতাংশ আয়ু রাস্তাঘাটেই কেটেছে। একবার এক আত্মীয়ের হেপাটাইটিস বি এর মতো মারাত্মক অসুখ হয়েছে বলে বেজায় বিড়ম্বনায় পড়েছি। তাঁকে সে-কথা বলতেই তিনি একটা ওষুধ কিনে এনে দিলেন। তিনদিন সেবন করাতেই সেই অসুখ ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল। আত্মীয়টি পুরোপুরি সুস্থ হল। কিন্তু
তিনি নিজেই যখন অসুস্থ হলেন, তখন সংসার প্রায় অচল। একদিন দোকানে বসে নানা কথার পর বললেন:
—কাউকে বলতে পারছি না, খুব সংকটে পড়েছি। গত দুদিন থেকে দোকান খুলতে পারিনি। উনুনও জ্বলেনি। আজ একটা পয়সারও বেচাকেনা হয়নি।
বলতে বলতেই তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। এরকম একটা মানুষকে এভাবে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি। সেদিনই আমি টিউশনি পড়া ১০০০ টাকা মাইনে পেয়েছি। কিছু আনাজপাতি কেনার জন্য এবং বাবার জন্য নতুন একজোড়া চপ্পল কিনব এটাই মনে মনে সংকল্প। কিন্তু সেই দুঃখ আর সইতে পারলাম না। টাকাটি তাঁর হাতে দিয়ে বললাম: —আপাতত এটা রাখুন,কিছুটা তো উপকার হবে!
—আমাকে দিলে তোমার কী হবে?
—আমি তো আবার পাব! আমার ঠিক চলে যাবে।
—যদি না শোধ করতে পারি?
—তা নিয়ে ভাববেন না, শোধ নেব বলে আপনাকে দিচ্ছি না। এ তো সামান্য টাকা!
টাকাটা হাতে নিয়ে তিনি আবার কাঁদলেন, কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “আমার যে এরকম দিন আসবে তো কোনোদিন ভাবিনি! জীবন যে কত রহস্যময়, কত উত্থান পতনে তার গতিপথ তা কেহই বলতে পারে না।”
২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মারা যান। মৃত্যুর দু’বছর আগে থেকেই অসুস্থতার কারণে দোকানের পুঁজিও তিনি আর রাখতে পারেননি। প্রায় নির্বাক জ্ঞান শূন্য হয়ে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ীও ছিলেন। তিনি আমাদের কাছে একটা জীবন্ত কিংবদন্তি। সব বিষয়ের সংবিধান হিসেবেই তাঁকে জীবনে পেয়েছিলাম।
রামপুরহাটে সাহিত্যের আরেকজন অভিভাবক আমাদের মন-প্রাণ জুড়ে অবস্থান করেছেন, তিনি সত্যসাধন চট্টোপাধ্যায়। শ্যামপাহাড়ি ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিত। ইংরেজি ও অর্থনীতি দুটি বিষয়েই একইসঙ্গে তিনি মাস্টার ডিগ্রি করেছিলেন। অন্তর্মুখী নিভৃতচারী মানুষটি কখনো বাহিরে কোথাও উচ্চকিত হতেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর শোনাও ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। ছাত্রজীবনেই তাঁর সম্পাদিত ‘ডানা’ পত্রিকায় কবিতা বিষয়ক একটি গদ্য পাঠালে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পত্রিকার প্রথমেই সেটি ছাপান। তারপর একদিন আমাকে ডেকেও পাঠান। ছাত্রজীবনে রামপুরহাটেই পেয়েছিলাম বাপ্পা ব্যানার্জি ও অনিমেষ মণ্ডলকে। তাদের মারফতই জানতে পারি ‘ডানা’ পত্রিকার কথা। প্রথম দিনেই সত্যসাধন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বুঝেছিলাম, মানুষটি কত বড় মানুষ। অন্তঃপুরের গোপনচারী সন্ন্যাসী বলেই মনে হয়েছিল আমার। প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বক্ষে আকর্ষণ করেছিলেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, “তোমার গদ্য পড়ে বুঝেছি তোমাকে কতটা প্রয়োজন আমাদের। এতদিন যেন তোমাকেই খুঁজছিলাম!”
শুধু মুখের কথা নয়, সেই দিন থেকে ‘ডানা’র সহ-সম্পাদকীয় বিভাগে আমার নাম লেখা হয়েছিল।
তাঁর গৃহ-লাইব্রেরিতে অসংখ্য পুস্তক সংগ্রহ দেখে অবাক হয়েছিলাম। ইংরেজি সাহিত্য, ফরাসি সাহিত্য থেকে হাল আমলের পত্রপত্রিকা পর্যন্ত পাঠ করার অঢেল আয়োজন। কোন বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হয় তা শুধু জানালেই হবে। তৎক্ষণাৎ তিনি তা পরিষ্কার করে দেবেন। তিনি নিজেই জীবনানন্দ দাশের ভক্ত। মানুষের হৈ-হল্লায় সামিল হতে পারেন না। একাকী নির্বাসিত জীবন কাটান। বিষয় আসক্তিও নেই তাঁর। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁরই বংশের লোক। অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে প্রায় আত্মগোপনেই রয়ে গেছেন। নিজের পত্রিকাতেই দু-একটা কবিতা প্রকাশিত হয়, আর অন্য কোথাও তেমন পাঠান না। পত্রিকার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে লেখা এলে সেগুলো পড়ে দেখে বিভিন্ন মতামত সাপেক্ষে নির্বাচন করি। ভালো লেখা যাতে একটাও বাদ না যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকি। এতদিনে মনে হয় সঠিক পথে চলার মতো একজন অভিভাবককে আমরা পেয়েছি। কবিতা নিয়ে আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে কোনো কোনোদিন রাত হয়ে যায়। রামপুরহাট থেকে শুনশান ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে সাইকেলের রাস্তা। অন্ধকারে খেজুর গাছকেও ভূত মনে হয়। তখন শুধু কবিতাতেই সাহস যোগায়। জোরে জোরে সাইকেলের বেল্ বাজাই আর দ্রুত বাড়িমুখী অগ্রসর হতে থাকি। বাংলা সাহিত্যে কত বিদেশি লেখকের প্রভাব আছে, কবিতার বাঁক কিভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে তা বুঝতে পারি তখন।
শঙ্কলাল রায় এবং সত্যসাধন চট্টোপাধ্যায় দুই মহীরূহ জীবনের দুই মেরুতে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। আজও আমাকে কবিতার ছন্দ শেখাচ্ছেন। আজও আমাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন কোন কবিতাটিতে বিদেশি কোন কবির ছায়া পড়েছে। মানুষ যখন মানুষ হতে ভুলে যাচ্ছে, তখন আমি এই দুই মহীরুহের কাছেই মানুষ হবার দীক্ষা পাচ্ছি। কবিতা লিখতে গেলে যে মানুষও হতে হয়, সহনশীল, নিভৃতচারী, তথাকথিত যশ-খ্যাতিকে তোয়াক্কা না করে দ্রুত বেল্ বাজিয়ে অন্ধকার ভেদ করে চলতে হয় তা অনেক আগেই শিখেছিলাম।