আবু তাহের সরফরাজ
আশির দশকে বাংলা কবিতার বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখে পড়ে। প্রথমত, প্রথা ভাঙার প্রবণতা। এই দশকের কবিরা আগের দশকের বিবৃতি কিংবা স্লোগানধর্মী কবিতার ঘেরাটোপ ভেঙে নতুন একটি ধারা সৃষ্টির চেষ্টা চালান। সত্তরের দশকটি ছিল রাজনৈতিক কারণে উত্তাল ও সহিংস। একাত্তরের শেষদিকে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গঠন করলেন নতুন দেশের সরকার। পুনর্গঠন করতে শুরু করলেন পাকিস্তানিদের ধ্বংস করে দিয়ে যাওয়া সোনার বাংলা। কেবল রাষ্ট্রই নয়, রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতর যা যা আছে, সবই এই সময়ে নতুনভাবে নতুন স্বপ্নের রেশ নিয়ে উজ্জীবিত হতে শুরু করলো। কবিতাও এর বাইরে ছিল না। চোখের সামনে মৃত্যুর মিছিল দেখতে দেখতে কবিসম্প্রদায় আরদশটা সাধারণ মানুষের মতোই শিহরিত। তবে কবিরা একটু বেশিই। কারণ, সাধারণ মানুষ থেকে তারা বেশি সংবেদনশীল। স্বাধীনতার পরপরই দেশের অর্থনীতিতে নেমে এলো চরম ধস। পঁচাত্তরে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। একমুঠো খাবারের জন্য মানুষের হাহাকার। দেশের মানুষের ভেতর তৈরি হতে শুরু করে হতাশা আর ক্ষোভ। সত্তরের দশকটা আসলে নানা অভিঘাতে টালমাটাল একটি সময়। বোধের অতলান্তিক অবগাহন এই সময়ের কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই তেমন একটা উঠে আসেনি। যেমনটি উঠে এসেছে প্রতিদিনের গ্লানিময় জীবনের টুকরো টুকরো ছবি। মানুষের বেঁচে থাকার দরকারে জটিল ও সঙ্কটময় যে পরিস্থিতি সে সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল, ওই পরিস্থিতির অগ্নিবলয় কবিদেরকেও ঘিরে ছিল। গণমানুষের ক্ষোভের আগুন ঝলছে দিতো কবিতার শব্দগুচ্ছকে।
আশির দশকে এসে কবিতা নতুন প্রকরণ ও আঙ্গিকে নির্মিত হতে শুরু করল। এই দশকের কবিদের ভেতর প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এই মনোভাব থেকেই ছোটকাগজ চর্চা ছড়িয়ে পড়ে বৃহৎ পরিমণ্ডলে। এই চর্চা এতটাই গতিশীল হয়ে ওঠে যে, প্রতিষ্ঠানের সিলমারা সাহিত্য-বলয় থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে ও ছোটকাগজ-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা বেশ একটা আন্দোলনের রূপ পায়। এই ধারা আশির কবিদের শিল্পভিত্তি তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সত্তরের দশকের বিবৃতিধর্মী ধারা থেকে আশির দশকের কবিতার খুব বেশি পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে না। এরপরও অগ্রজ কবিদের থেকে আশির কবিতাকে আলদাভাবে চিহ্নিত করার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সত্তরের মতো আশির দশকের কবিতায় রাজনীতি উপজীব্য হয়নি। তবে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক ঘটনার স্ফূরণ পাঠককে তাড়িত করে। নব্বইয়ের থেকে আশির দশকের কবিতার যে স্বাতন্ত্র্য সেটি আসলে ছোটকাগজ চর্চার কারণেই তৈরি হয়। বেশ কয়েকটি ছোটকাগজকে কেন্দ্র করে আশির কবিরা গোষ্ঠিবদ্ধ হতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, দৈনিক খবরের কাগজের সাহিত্যপাতা সাহিত্যের নামে পাঠকদের কাছে যা পরিবেশন করে তা আসলে ভূষিমাল। ভূষি গরু-ছাগলের খাদ্য, মানুষের নয়। এই অনুপ্রেরণায় তাদের কাব্যযাত্রা বন্যার স্রোতের মতোই বেগবান হয়ে ওঠে। গোষ্ঠিভিত্তিক ছোকাগজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: গাণ্ডীব, পেঁচা, একবিংশ, অনিন্দ্য, পূর্ণদৈর্ঘ্য, প্রসূন, লিরিক, ছাঁট কাগজের মলাট ও নিসর্গ।
আশির দশকের উল্লেখযোগ্য কবি মাসুদ খান। তার কবিতা পাঠে আশির দশকের কবিতার রূপবৈচিত্র্য সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কেননা, ওই দশকের যে ক’জন কবি আগের দশকের বলয় ভেঙে কবিতায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেন, মাসুদ খান তাদের অগ্রগণ্য। আমরা দেখেছি, সত্তরের দশকের কবিতায় ঐতিহ্য ও মিথের ব্যবহার খুবই কম এসেছে। কিন্তু আশির দশকের কবিরা আবারও সেই ধারা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয়সহ কারো কারো কবিতায় ইসলামি মিথের ব্যবহার আমাদের চোখে পড়ে। ‘একজন বর্ণদাসী ও একজন বিপিনবিহারী’ কবিতায় মাসুদ খান লিখছেন:
বনের কিনারে বাস, এক ছিল রূপবর্ণদাসী
আর ছিল, বনে বনে একা ঘোরে, সেই এক বিপিনবিহারী।
কন্যা তো সে নয় যেন বন্য মোম, নিশাদল মাখা, বন্য আলোর বিদ্রুপ
রাতে মধ্যসমুদ্রে আগুন-লাগা জাহাজের রূপ
অঙ্গে অঙ্গে জ্বলে।
পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন শকুন্তলার মতো কোনো আখ্যান পড়ছি। মাসুদ খানের বেশিরভাগ কবিতাই এরকম আখ্যানসূত্র দিয়ে লেখা। পড়তে গেলে কাহিনির ভাঁজ খুলতে হয়। সেই ভাঁজের ভেতর লুকনো থাকে জীবনের শিল্পসৌন্দর্য। এই যে কবিতাটি, এখানে আমরা পাচ্ছি একজন মেয়ের বর্ণনা। রাতে মাঝ-দরিরায় জাহাজে আগুন ধরে গেলে তীর দেখে আগুনের যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, মেয়েটির দেহে সেই রকম আগুনের হলকা। গোটা কবিতার শরীরে মাখানো রয়েছে ভারতীয় আখ্যানের নির্যাস। কবিতাটির শব্দ বুনন খেয়াল করলে দেখা যাবে, বলার কথার সাথে শব্দেরা আশ্চর্যভাবে দণ্ডায়মান। সত্যি যে, মাসুদ খানের কবিতার শব্দেরা বেশ সম্ভ্রান্ত। এক ধরনের গাম্ভীর্য নিয়ে তার কবিতায় শব্দেরা দাঁড়িয়ে থাকে। সত্তর দশকের কবিতার পেলব ও গেরস্থালি শব্দের সাথে মাসুদ খানের কবিতার শব্দের প্রভেদ সহজেই পাঠক ধরে ফেলতে পারে। যেহেতু শব্দ দিয়েই নির্মিত হয় কবিতার অবয়ব, সেহেতু শব্দ-বিন্যাসের নিজস্ব কৌশল তৈরি করা যে কোনো কবির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। মাসুদ খান সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই করে চলেন তার প্রতিটি কবিতা নির্মাণের সময়।
মাসুদ খানের কবিতায় আমাদের যাপিত জগতের পাশাপাশি আরেকটি জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সেই জগৎ আমাদের বোধের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমাদের পরিচিত অনুষঙ্গই মাসুদের কবিতায় ভিন্নভাবে উদ্ভাসিত হয়। তাত্ত্বিকরা হয়তো এটাকেই বলেন শিল্পের মোড়ক। নব্বইয়ের দশকের কবি মজনু শাহ’র কবিতাতেই এ ধরনের ব্যাপার পাঠকের চোখে পড়ে। কবিতার ভেতর দিয়ে পাঠককে ঘোরগ্রস্থ করে ফেলেন মাসুদ খান। জাদুকর যেমন হাতের তেলেসমাতি খেলায় দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে তোলে, মাসুদ খানও একইভাবে কবিতার ভেতর দিয়ে এক ধরনের চমক সৃষ্টি করেন। এজন্যই তার কবিতার শব্দেরা গাম্ভীর্য সহকারে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চমক দেখাতে গিয়ে মাসুদ খানের কবিতা কোত্থাও টলে যায় না। শিল্পসৌন্দর্যের ঘাটতিও কোত্থাও ঘটে না। বরং মনে হয়, মাসুদের বয়ানকৃত আখ্যানে চমক না থাকলেই বরং কবিতা হিসেবে সেটি ব্যর্থ হতো। তা কিন্তু কখনো হয় না। আশির দশকের পর এই ধারা নব্বইয়ের দশকের কবিতায় বহুলভাবে চর্চিত হয়েছে। তবে আশির কবিদের থেকে নব্বইয়ের কবিদের পার্থক্য হচ্ছে, তারা কবিতার ভেতর চমক সৃষ্টির কৃৎকৌশল শৈল্পিক উপায়ে ঢোকাতে পারেননি। নব্বইয়ের বেশিরভাগ কবির কবিতায় চমক হয়ে পড়েছে খেলো। যেন, ওই চমকটাই কবিতা। কিন্তু মাসুদের কবিতায় চমকটাই কবিতা নয়। তার কবিতার ভেতর চমক ছাড়াও থাকে অনুক্ত নানা ইশারা। কবিতা পাঠে চমকিত হওয়ার সাথে-সাথে পাঠককে ওইসব ইশারার মানে খুঁজে নিতে নিজের ভেতর ডুব দিতে হয়। ‘কৌতুকবিলাস’ কবিতার কয়েক পঙক্তি পড়া যাক:
ঈশ্বর ছুড়েছে ঢিল ঈশ্বরীর দিকে, কৌতুকবিলাসে।
গ্রহটিকে মাটির ঢেলা বানিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের একপ্রান্ত থেকে
ক্ষেপণ করেছে ভগবান, অন্যপ্রান্তে থাকা ভগবতীর দিকে।
মহাকাশ জুড়ে প্রসারিত মহাহিম শূন্যতা, লক্ষ-ডিগ্রি নিস্তব্ধতা—
তারই মধ্য দিয়ে একপিণ্ড ছোট্ট শ্যামল কোলাহল হয়ে
ধেয়ে যাচ্ছে এই ঢিল।
আমাদের অভিজ্ঞতায় ঈশ্বর ধারণা মাত্র। ধারণা করা ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা কোনোভাবেই আমাদের অনুভূতির জগতে আনতে পারি না। সেই ঈশ্বর তার স্ত্রীর দিকে ঢিল ছুড়ছেন। বলা দরকার, সৃষ্টিকর্তা স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু আমাদের কাছে ধারণামাত্র, সেহেতু মাসুদ খান সেই ধারণাকে কেন্দ্র করেই ধারণা করছেন যে, ঈশ্বর কৌতুক করে ঈশ্বরীর দিকে ঢিল ছুড়ছেন। খ্রিষ্ট ধর্মে ঈশ্বর বলে, হিন্দু ধর্মে ভগবান বলে, আর ইসলাম ধর্মে আল্লাহ বলে। সকল নামই সেই একজনের, মহাবিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা। মাসুদ খান বলছেন, গ্রহকে মাটির ঢেলা বানিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের একপ্রান্ত থেকে ভগবান আরেক প্রান্তে থাকা ভগবতীর দিকে ছুড়ে দিচ্ছেন। এরপর মাসুদ বর্ণনা দিচ্ছেন মহাকাশের মহাস্পেসের। মহাহিম শূন্যতার ভেতর দিয়ে একপিণ্ড কোলাহল হয়ে ঢিলটি ছুটে যাচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের আরেক প্রান্তে। ঢিল ছুটে যাচ্ছে, এই অবসরে মাসুদ খান পারিপার্শিক অবস্থা পাঠকের চোখে ছবির মতো এঁকে চলেন। যে বিষয় আমাদের ধারণা সেই বিষয়য়ের দৃশ্যকল্প এঁকে মাসুদ খান ধারণাকে বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। কবিতাসহ যে কোনো শিল্পমাধ্যমের শক্তি আসলে এখানেই। পাঠক বুঝতে পারছে, এটি বাস্তব নয়, এরপরও বাস্তবের প্রতিরূপ হিসেবে নির্মিত শিল্পমিথকে বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিতে পাঠক আগ্রহ বোধ করে। যাপিত বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে শিল্পের বাস্তবতায় পাঠক আসলে নিজের জীবনের দিকেই দৃষ্টিকে অভিক্ষেপ করে।
ঢিল ছুটে যাচ্ছে, একইসাথে আরও যা-যা ঘটছে সেসবের দিকে পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আটকে থাকে। কবিতার শেষদিকে মাসুদ খান লিখছেন, ‘ছিটকে পড়ার ভয়ে ভয়ার্ত শিশুর মতো ছুটন্ত ঢেলার গা আঁকড়ে ধ’রে চাম-উকুনের মতো চিমসা দিয়ে পড়ে থাকে প্রাণপণ তটস্থ ও অসহায় প্রাণীকুল।’ ঢিলটি যে গ্রহ, কবিতার শুরুতেই সেটা আমরা জেনেছি। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে আলবার্ট আইনস্টাইনের মহাকর্ষ সূত্র। সূত্রমতে, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই একটি আরেকটিকে আকর্ষণ করছে। সৌরজগতের যে গ্রহটিতে আমরা বসবাস করছি সেই গ্রহটিকে ঢিল হিসেবে কল্পনা করে নেওয়ার সুযোগ মাসুদ খান আমাদেরকে করে দিচ্ছেন। ঢিলটির মতোই আমাদের আবাসভূমি পৃথিবী সূর্যকে মাঝখানে রেখে মহাশূন্যে বন্দুকের গুলির চেয়েও কয়েক কোটি গুণ তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। অথচ পৃথিবীর ওপর অবস্থান করে আমরা তা এতটুকু টেরও পাচ্ছি না। কিন্তু মাসুদ খান বর্ণিত ঢিলরূপ গ্রহটিতে সকল প্রাণী ভয়ে তটস্থ। প্রাণীকুলের এই আতঙ্কই মহাবিশ্বের বাস্তবতা। কিন্তু ওই ঢিলের ওপর অবস্থান করে আমাদের যে রকম নির্বিকার ভাবভঙ্গি, তা যে কতটা অবাস্তব সে কথাই যেন মাসুদ খান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক কোনো সত্যকে ভিত্তি করে মাসুদ খান কবিতার সূত্র বয়ান করেননি। বরং এক্ষেত্রে তিনি তার স্বভাবগত আখ্যানকেই নির্ভর করেছেন। দেখা যাচ্ছে, এখানেও রয়েছে কাহিনিসূত্র। বোধকে তাড়িত করার মতো গূঢ়ার্থ ইশারাও রয়েছে। কবিতার শেষ বাক্য দুটি এবার পড়া যাক:
খেলা করে ভগবান ভগবতী— বিপদজনক ঢিল ক্ষেপণের খেলা।
আর রোমাে ও ত্রাসে শিউরে-শিউরে কেঁপে ওঠে তাদের সন্তানরা।
এইখানে এসে আমাদের মনে পড়ে কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিখ্যাত গানটির কথা, ‘খেলিছ এই বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।’ নজরুলের এই গানের সাথে মাসুদ খানের এই কবিতার সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। তবে সত্যি বলতে কি, নজরুলের কল্পদৃশ্য ও ভাষারীতি ঈর্ষণীয়। আর মাসুদ খানের বর্ণনা ও ভাষারীতি সম্পূর্ণ মাসুদ খানীয়। আগেই লিখেছি, মাসুদ খানের কবিতার শব্দগুলো ভাব-গাম্বীর্যে টানটান একটা ভঙ্গি বজায় রাখে। এই কবিতাতেও তেমনটাই লক্ষ্য করা যায়। মহামহিম নজরুলের সঙ্গে তুলনা করলেও এটাও সত্য যে, নজরুল যে ভাষ্য ও ইশারা তার গানের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন সেই ভাষ্য ও ইশারা মাসুদ খান ব্যক্ত করেনি। মাসুদের বলার কথা ভিন্ন, সেটা বুঝে নিতে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের খুব বেশি তকলিফ করতে হয়নি। অবশ্যি মাসুদ খানের কবিতার যারা পাঠক তারা প্রাজ্ঞ পাঠক। গড়পড়তা পাঠক মাসুদের কবিতার সঙ্গে আত্মীয়তা তৈরি করতে পারবে না। পাঠকের শিল্প-সক্ষমতার বিষয়ে মাসুদ খান একটি গদ্যে লিখেছেন, “যে কোনো নন্দনশিল্পের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত থাকে নিমগ্ন সাধনা। সস্তা মনোরঞ্জন শিল্পের অভীষ্ট নয়। তবে শিল্পীর যেমন চাই সাধনা, তেমনই সমঝদারিত্বের জন্য শিল্প-উপভোক্তারও চাই কিছুটা দীক্ষা, কিছুটা প্রস্তুতি। এ কথাগুলি কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভাব ও ভাষার কোন জাদুকরি কম্পোজিশন, কোন রুহদারি বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে যে কোনো প্রকারের ফুল, সে-এক রহস্যই বটে। তবে এও সত্য— সহজ-স্বাভাবিক অথচ লাগসই শব্দমালায়র বিশেষ বিন্যাসে কোনো ভাবস্তুকে মৌলিক ও হৃদয়গ্রাহী করে ফুটিয়ে তোলাটাই কৃতিত্বের।”
সেই কৃতিত্বের পরিস্ফুটন মাসুদ খানের প্রতিটি কবিতার শরীরেই পষ্ট হয়ে জেগে থাকে। বাস্তবতা ও প্রতিবাস্তবতার মাঝখানে যে সাঁকো তিনি নির্মাণ করেন সেই সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে পাঠক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, কী নিপুণ শিল্প-কুশলতায় মাসুদ খান অন্তর্বোধের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন তার কবিতায়। কবিতা কি কেবলমাত্র পড়ার জন্যই? না, তা নয়। কবিতা হচ্ছে আয়না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমরা নিজের যে রূপ দেখি তা কিন্তু আমি নই, আমার প্রতিবিম্ব। মাসুদ খানের কবিতা ঠিক সেই রকম যাপিত-জীবনের প্রতিবিম্ব নির্মাণ করে। ‘জ্বরের ঋতুতে’ কবিতায় তিনি লিখছেন:
তখন আমাদের ঋতুবদলের দিন। খোলসত্যাগের সময়। সুস্পষ্ট কোনো সর্বনাশের ভেতর ঢুকে পড়তে চেয়েছিলাম আমরা দুজন। তার আগেই তোমার জ্বর এলো। ধস নামানো জ্বর। তুমি থার্মোমিটারের পারদস্তম্ভ খিমচে ধরে ধরে উঠে যাচ্ছ সরসর করে একশো পাঁচ ছয় সাত আট … ডিগ্রির পর ডিগ্রি পেরিয়ে… সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী তাপের সহগ হয়ে উতরে উঠছ তরতরিয়ে সেইখানে, যেইখানে আর কোনো ডিগ্রি নাই, তাপাঙ্ক নাই… তাপের চূড়ান্ত লাস্যমাত্রায় উঠে ঠাস করে ফারেনহাইট ফাটিয়ে বেরিয়ে আসছে থার্মোমিটারের ফুটন্তঘন তরল আগুন…
আপাতপাঠে কবিতাটি জটিল মনে পারে। কিন্তু শব্দ ধরে ধরে যদি এগোনো যায় তাহলে কবিতার ভেতরে লুকনো রহস্য উদ্ঘাটনে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। বলা দরকার, এখানে প্রতিটি শব্দই যেন এক –একটি ইশারা। মাসুদ খান যেহেতু প্রাজ্ঞ পাঠক আশা করেন সেহেতু প্রজ্ঞার দ্যুতি এই কবিতার ওপর ছড়িয়ে দিতে পারলেই কবিতার বক্তব্যের অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাবে। কাহিনির একটি ঢং এই কবিতাতেও রয়েছে। যৌনতাকে যে এমন কৌশলে ও শিল্পের সৌন্দর্যে রাঙিয়ে উপস্থান করা যায়, এরকম উদাহরণ আশির দশকের আর কোনো কবির কবিতায় আমাদের চোখে পড়ে না। প্রতিটি শব্দকে মাসুদ খান যেভাবে ব্যঞ্জনা দিয়েছেন সেই ব্যঞ্জনা কবিতার প্রসাদগুণ বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। মাসুদ খান যতই প্রাজ্ঞ পাঠক দাবি করুন না কেন এও ঠিক যে, কবিতা পড়তে গিয়ে মাথা-খাটানোর মতো যথেষ্ট সময় আজকের সময়ের পাঠকের নেই। বাংলা কবিতার ইতিহাসে দেখা গেছে, শব্দের গাম্ভীর্য পাঠককে খুব বেশি ধরে রাখতে পারেনি। যতটা ধরে রাখতে পেরেছে সুললিত পরিচিত শব্দের বৈভব। আর এ কারণেই হয়তো কবিসমাজের বাইরে সাধারণ পাঠকের কাছে মাসুদ খানের কবিতা এখনো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তবে জনপ্রিয় হওয়ার যোগ্য অনেক কবিতাই মাসুদ খান লিখেছেন। সেসব কবিতার শব্দ ও নির্মিতি সহজ ও প্রাঞ্জল। সাম্প্রতিক সময়ে ফেসবুকে তিনি ‘সম্প্রীতি’ শিরোনামের একটি কবিতা পোস্ট দিয়েছেন। কবিতাটি পড়া যাক:
পাহাড়, সমতলের মানুষ
শিশু, কিশোর, নারী, পুরুষ
পশু, পাখি, পাখপাখালি
বিড়াল এবং কাঠবিড়ালি
সবাই তো এই জল-টলমল
অবাক দেশের অবাক নাগরিক।
উৎসবে আর রোগে-শোকে
দুর্যোগে আর দুর্বিপাকে
সুসময়ে, দুঃসময়ে
সাহসে ও ভয়-অভয়ে
একই সুরে সমস্ত প্রাণ
উঠছে বেজে, এটাই স্বাভাবিক।
স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় ভাসছে দেশ। বানভাসী মানুষের অসহায় আর্তনাদ বাংলার বাতাসে ঘূর্ণি তুলছে। এই অবস্থায় দেশের সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বন্যার্তদের সাহায্যে কাজ করে যাচ্ছে। সম্ভবত এই দৃশ্য দেখেই মাসুদ খান ‘সম্প্রীতি’ কবিতাখানি লিখেছেন। একই সুরে সমস্ত প্রাণ বেজে ওঠাকে তিনি প্রকৃতির স্বাভাবিক রীতি বলেই মনে করেন। মাত্র কয়েকদিন আগে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনাকে হটাতে এভাবেই বাংলার আপামর জনগন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। প্রবল গণরোষের সামনে সর্বোচ্চ বল প্রয়োগ করেও তিষ্টতে পারেননি তিনি। বাধ্য হন তার সুহৃদ মোদির কাছে আশ্রয় নিতে। এর পরপরই ভারত বাঁধ খুলে বাংলাদেশকে তলিয়ে দেয়ার কূটকৌশলে মেতে উঠেছে। হাসিনা ও মোদিও এই শয়তানি শেষপর্যন্ত বাংলাদেশকে খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারবে না। কারণ, বাংলার মানুষ একই সুরে বেজে উঠতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই এই মাটির বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করেছে তখনই বাংলার মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে সকল শয়তানি নস্যাৎ হয়ে বানের জলের মতো ভেসে গেছে। যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হাসিনা ও মোদি দেখাচ্ছেন, তার বিষাক্ত ফলাফল তারা প্রকৃতির নিয়মেই একটা সময়ে ভোগ করবেন। সেটা সময়ের থাবা। কবি হিসেবে মাসুদ খান রাজনৈতিক কোনো ঝাণ্ডা উঁচু করে তুলে ধরেননি। তিনি কেবল কবিতার ভেতর দিয়ে মানুষের বাংলার মানুষের জয়গান গেয়ে উঠেছেন। আরসব কবিতা থেকে মাসুদ খানের এই কবিতাটির শব্দ ও বাক্যগঠন কিন্তু আলাদা। গাম্ভীর্য ভেঙে এই কবিতায় শব্দগুলো আমাদের খুব ঘনিষ্ট হয়ে বুকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। পাঠক হিসেবে আমরা কবিতাটির সাথে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি। ফলে বলতেই হয়, বহুমাত্রিক কবিতা লেখার যে কৃৎকৌশল সেটা মাসুদ খানের স্বভাবজাত। যেন তিনি শিল্পের সন্তান। শিল্পকে ইচ্ছেমতো প্রকাশ ঘটাতে পারেন। সহজাত এই নৈপুণ্য যে কোনো শিল্পীর থাকে না। থাকে কেবল তাদেরই যারা ব্যুৎপত্তি বিশেষভাবে অর্জন করেন।



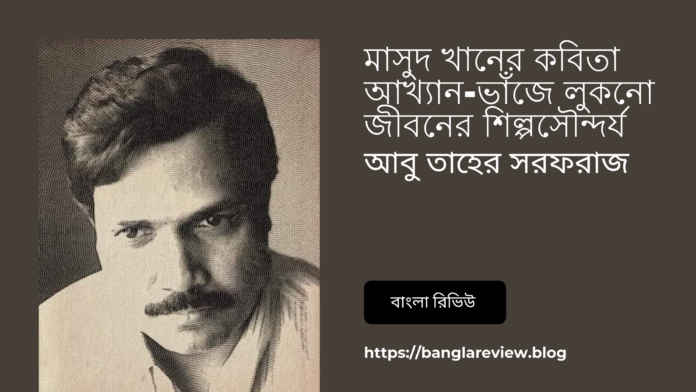




‘ মাসুদ খানের কবিতা আখ্যান-ভাঁজে লুকনো জীবনের শিল্পসৌন্দর্য’ — প্রবন্থটির নামকরণ সুন্দর। পুরো আলোচনাটি এই নামকরণকে কেন্দ্রে রেখে গড়ে উঠেছে। মাসুদখানের কবিতা পড়ে আসছি অনেকদিন থেকেই। আমার লেখা কবিতাবিষয়ক দুএকটি মুক্ত আলোচনায় তার কবিতার প্রসঙ্গ এসেছে। আবু তাহের সরফরাজ মাসুদ খানের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে তার কবিতার শিল্পসৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। মাসুদ খানের কবিতায় শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আবু তাহের সরফরাজের অভিমতের সঙ্গে সহমত পোষণ করি আমিও। আলোচনাটি একজন গুণী কবিতা সমঝদারের–একথা পাঠক মেনে নিবেন পড়ার সাথেসাথেই।