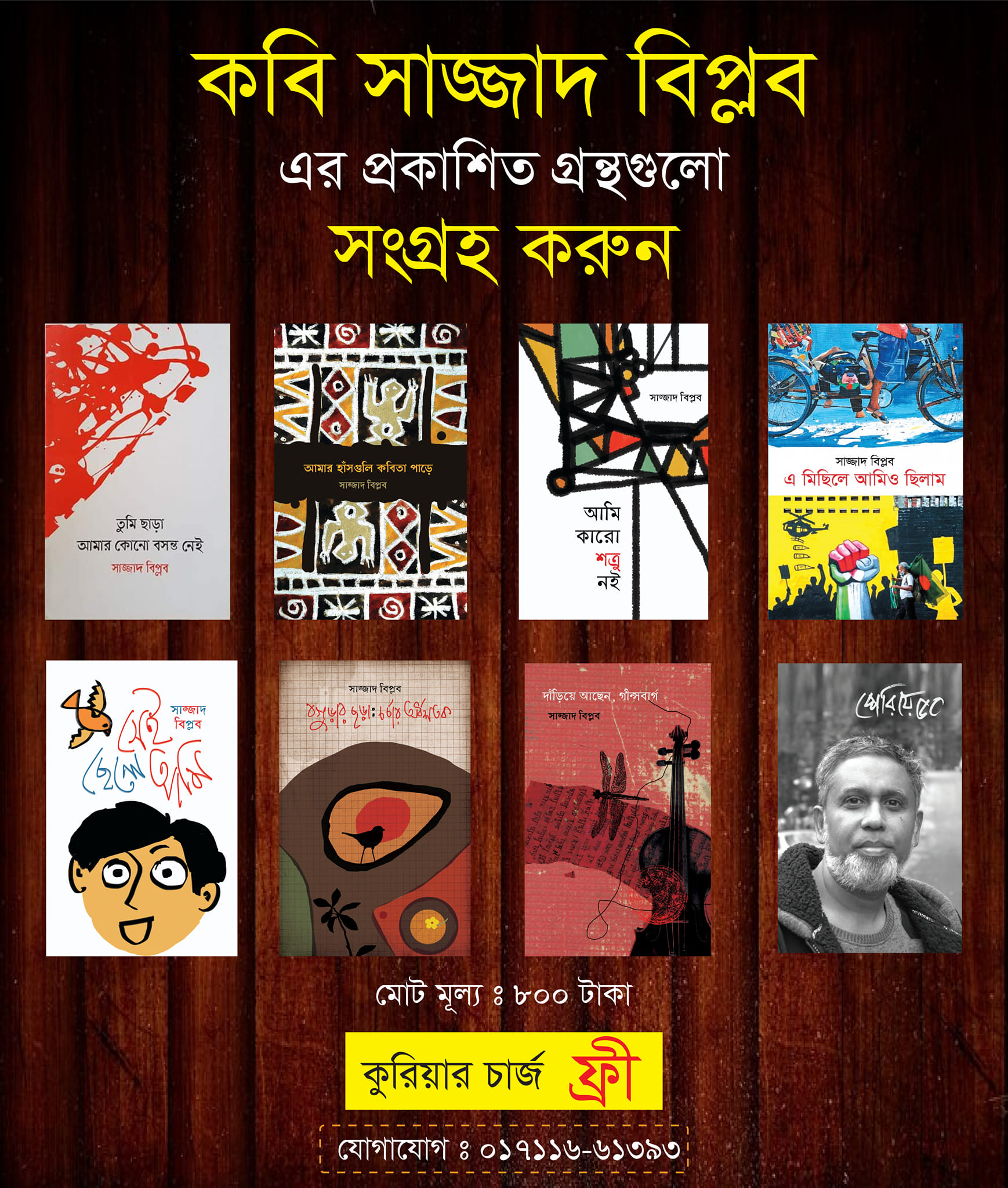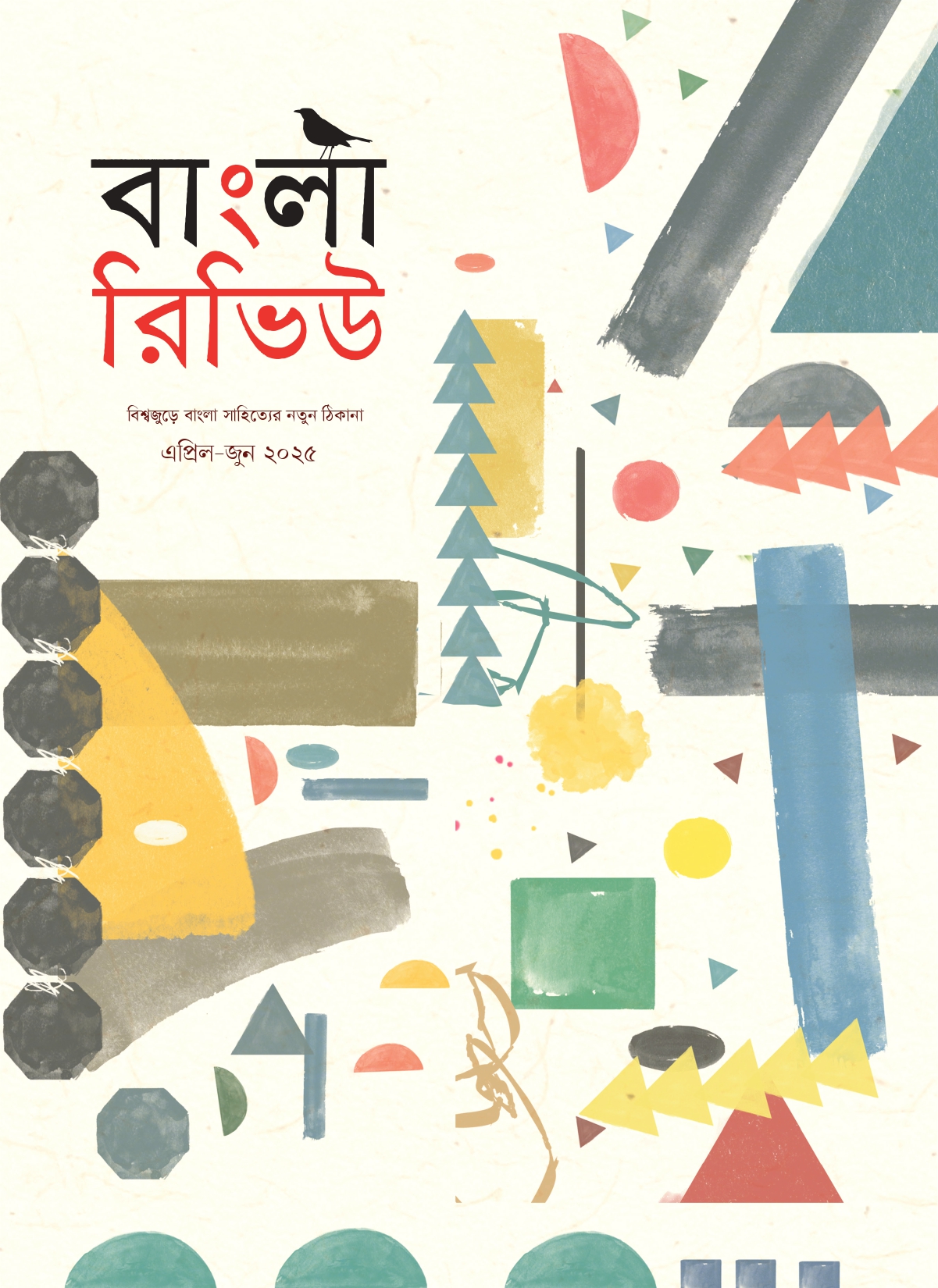আহমাদ মাযহার
আবুল হাসনাতের আগে আমার মাহমুদ আল জামানের সঙ্গে পরিচয়। সত্তরের দশকের প্রথম দিকেই জানতাম মাহমুদ আল জামান কবিতা লিখতেন, লিখতেন ছোটদের জন্যও। এটুকু জানতাম কিশোর বয়সেই দৈনিক বা সপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী ছিলাম বলে। তবে মাহমুদ আল জামানই যে সম্পাদক ও শিল্পকলা বিষয়ক লেখক আবুল হাসনাত সেটা জানতে আমার কিছু দেরি হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে একাধিক নামে লেখার ইতিহাস আছে। কিন্তু সে ধারা পশ্চিমবঙ্গে চালু থাকলেও বাংলাদেশ তা বেশ ক্ষীণ।
সবচেয়ে বেশি মনোযোগ কেড়েছিল ছোটদের জন্য লেখা তাঁর উপন্যাস ‘ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায়’। বইটির নাম জানলেও পড়া হয়েছিল অনেক পরে। তবে তাঁর লেখা ‘ছোটদের জসীমউদ্দীন’ খুবই ভালো লেগেছিল কৈশোরোত্তীর্ণ বয়সেই! বইটির গদ্য যেমন ছিল সহজ সরল তেমনি ছিল আমার সেই বয়সের কাঙ্ক্ষিত মাধুর্যমণ্ডিত ভাষা! জসীমউদ্দীন নিজে যেমন গ্রামীণ অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিতে কথা বলতেন মাহমুদ আল জামানের কথন ভঙ্গি ঠিক তেমন নয়, কিন্তু তাহলেও যেন গল্পচ্ছলে জসীমউদ্দীনের জীবনকথা ও সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন ছোট্ট অথচ সামগ্র্যস্পর্শী ঐ বইয়ে। বইটির বর্ণনায় আধুনিকতা-উন্মুখ বিকাশমান কৈশোরক একটা চেতনাপ্রবাহ আছে যা আমাকে তখন স্পর্শ করেছিল; এখনও আবার পড়তে গিয়ে দেখলাম এখনো পাঠস্বাদু লাগছে। সম্ভবত অন্যতর পরিচয় বেশি থাকায় ছোটদের জন্য বেশ কটি বই লিখলেও শিশুসাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা কথা উল্লিখিত হয়েছে কম। এমনকি আমার নিজের লেখা বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য বিষয়ক বইয়েও তাঁর কথা যথেষ্ট উল্লেখ করার কথা মনে ছিল না।
গত কয়েক বছরের কথা বাদ দিয়ে তাঁর লেখালিখির হদিস নিতে গেলে দেখা যাবে তিনি মূলত ছোটদের জন্যই বই লিখেছেন বেশি। বাঙালি মুসলমান সমাজে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বামপন্থা প্রভাবিত বঞ্চিত মানবতার প্রতি দরদ মিশ্রিত অসাম্প্রদায়িক চেতনাজাগর আধুনিকতার যে বোধ কিশোর তরুণদের মধ্যে জেগে উঠছিল মূলত মাহমুদ আল জামানের শিশুসাহিত্য তারই প্রতিভূ।
ছোটদের জন্য লেখা তাঁর জসীমউদ্দীন, সূর্যসেন বা চার্লি চ্যাপলিনের জীবনীতে তাঁর মানবদরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণলক্ষণ তাঁর ছোটদের জন্য লেখা কল্পনাপ্রধান কথাসাহিত্যে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। ছোটদের উপন্যাস ‘ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায়’ কিংবা ‘টুকু ও সমুদ্রের গল্প’ অথবা ‘রানুর দুঃখ-ভালোবাসা’-র বেলায় যেমন একথা সত্য তেমনি সত্য মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা ‘যুদ্ধদিনের ধূসর দুপুর’ বা ‘যুদ্ধদিনের পোড়োবাড়ি’-র বেলায়ও!
চিত্রসমালোচনা ছিল তাঁর অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম। ছিলেন চিত্র সংগ্রাহকও। তাঁর অবহিতি ও নৈকট্য ছিল দুই বাংলার সেরা শিল্পীদের সঙ্গে। কামরুল হাসান কিংবা কাজী আবদুল বাসেতের শিল্পজীবনী আর ‘জয়নুল, কামরুল, সফিউদ্দীন ও অন্যান্য’ বইয়ে তাঁর চিত্ররসিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। চিত্র প্রদর্শনীর তাৎক্ষণিক আলোচনা যেমন লিখেছেন তেমনি লিখেছেন গভীর পর্যালোচনামূলক লেখাও।
২০২০-এর বাংলা একাডেমি বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথা হারানো সিঁড়ির চাবির খোঁজে বইটি। ঢাকার গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ছবি উঠে এসেছে এ বইয়ে। বাংলাদেশের ঐ সময়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য বোঝার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটি। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ততার সূত্রে লাবণ্যময় ও স্মৃতিমেদুর গদ্যে মুক্তিযুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন ও শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের নানা প্রগতিশীল কার্যক্রমের বিবরণ দিয়েছেন তিনি এই বইয়ে। এ ছাড়াও ঢাকায় ১৯৬১ সালের রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন, ছায়ানটের জন্মকথা ও বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার প্রথম দিককার অনেক অনালোচিত দিকও বইটিতে উঠে এসেছে ।
মূলত সম্পাদক হিসেবেই আবুল হাসনাতের পরিচিতি। সবেচেয়ে বেশি খ্যতি ছিল সম্পাদনায়। তাঁর খ্যাতির শুরু দৈনিক সংবাদ সাময়িকীর সম্পাদকতা সূত্রে সত্তরের দশকের শেষের দিক থেকে। বাম রাজনীতির কর্মী হিসেবে ঐ ধারার সাহিত্যের প্রতি পক্ষপাত থাকলেও সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন উদার দৃষ্টির। ডাকে আসা অপরিচিত লেখকের লেখাও অনেক সময় গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছেন। উপেক্ষিত অনেক লেখক সম্পর্কে তরুণদের উদ্বুদ্ব করেছেন লিখতে। তাঁর সম্পাদকতায় সংবাদ-এর সাহিত্য সাময়িকী খ্যাতির চূড়ায় উঠেছিল।
ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার ঠিক ওঠা-বসা না থাকলেও দু একবার টুকটাক কথা হয়েছে নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে বিভিন্ন সময়। কিন্তু তাঁকে একটু ভালো ভাবে জানা-বোঝা খুবই সাম্প্রতিক ব্যাপার। তাঁর সঙ্গে ভাববিনিময় হয়েছে নিউইয়র্কে। নিউইয়র্কেই তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আড্ডা দেয়ার সুযোগ পেয়েছি। লেখালিখি ও তাঁর কর্মজীবনের কথা যা জানা ছিল তার মধ্য দিয়ে তাঁকে ঠিক মতো চেনা যায় না। এমনকি তাঁর সম্পাদকীয় নীতি, যা সর্বত্রই প্রশংসিত, তার আলোকেও তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে পুরোপুরি বোঝা যায় না। তাঁর সমকালে যে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি (যাকে প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত করা হতো) ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর নেতৃত্ব ও বিচরণের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করলে তাঁকে যেমন আদর্শনির্দিষ্ট মনে করার কথা তিনি ছিলেন তারও ঊর্ধ্বে, তার চেয়ে উদার। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নিজে যেমন শুভবুদ্ধি ভিত্তিক জীবনের অনুশীলন করতেন তেমনি আস্থাশীল ছিলেন অন্য মানুষের শুভবুদ্ধির ওপরও; এমনকি বহুক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সুখকর না হলেও তিনি শুভবুদ্ধির ওপর থেকে কখনো আস্থা হারাননি।
সভাসমিতিতে বা গণমাধ্যমে কথা বলতেন না বলে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমার কাছে দীর্ঘকাল পরিচিত ছিল না। সংবাদ-এ কখনো লেখা দেয়া হয়নি বলেও তা হয়ে ওঠেনি; এ ছাড়াও তাঁর সঙ্গে আমার কর্মসূত্রে নৈকট্য লাভের সুযোগ না থাকায় সরসসরি কথা বলার সুযোগ হয়েছে কম। আমার নিউইয়র্কে বসবাস করতে আসার আগে ঢাকায় তাঁর ‘কালি ও কলম’ অফিসে কয়েকবার ও ঢাকা-কলকাতা যাতায়াতের সময় বিমানবন্দরে কথাবার্তা সূত্রে তাঁর ব্যক্তিস্বভাব খানিকটা অনুভব করতে পারি। এরপর থেকে আগে যেমন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধান্বিত থাকতাম তা দূর হয়ে যায় এবং তিনি যে আমাকে বেশ স্নেহই করেন তা অনুভব করে তাঁর কাছে আমার নানা রকম দাবির মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে! শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শহিদ মিনারের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান চ্যানেল আইয়ে সরাসরি প্রচারের কালে ক্যামেরার সামনে তাঁকে কথা বলাতে সমর্থ হই। এর আগে কয়েকবার অনুরোধ করেও তাঁকে ক্যামেরার সামনে আনতে পারিনি। ২০১৭ সালে নিউইয়র্ক বইমেলায় আসতে পারেননি। তিনি এসেছিলেন মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরে। মেয়ের বাড়িতে মাসখানেক ছিলেন সেবার। বেঙ্গল পাবলিকেশন্সের বই নিয়ে আলাদা মেলার আয়োজন করেছিলেন বিশ্বজিত সাহা তাঁর মুক্তধারা নিউইয়র্কে। তখনও লম্বা সময় ধরে আড্ডা হয়েছে। আগে তাঁকে যেমন স্বল্পবাক মনে হতো পরে আর তা মনে হয়নি। পরে আমি যেমন তাঁকে ঢাকায় ফোন করেছি, তেমনি তিনিও লেখা চেয়ে নিউইয়র্কে ফোন করেছেন আমাকে। এ বছর বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলায় তারিক সুজাতের জার্নিম্যান স্টলে কিছুক্ষণের আড্ডাই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখার স্মৃতি। করোনার মধ্যেও একাধিক দিন তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। বারবার সাবধানে থাকতে বলেছেন আমাকে। করোনা পরিস্থিতিতে তিনে নিজেও যে নানা উদ্বেগে আছেন সে কথা বলেও বারবার আমাকে অনুরোধ করেছেন তাঁর কন্যা দিঠির সঙ্গে যেন এসব উদ্বেগের কথা নিয়ে আলোচনা না করি!
সাহিত্য সম্পাদনায় তিনি যে রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন তা বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলের কাছে দীর্ঘকাল ধরে উৎকর্ষের পরিচায়ক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সম্পাদনা কর্মের আরো উৎকর্ষের নমুনা ‘মুক্তিযুদ্ধের গল্প’ ও ‘মুক্তিযুদ্ধের কবিতা’ সংকলন; সংকলনদুটি ছিল বাংলাদেশের সাহিত্যে যথার্থ প্রতিনিধিত্বশীল; এই ধারার সৃষ্টিকর্ম বিচারে সংকলন দুটির তাৎপর্য দীর্ঘ কাল ধরে অনুভূত হবে।
মাহমুদ আল জামান নামে তিনি যেমন প্রধানত কবিতা লিখতেন তেমনি লিখতেন ছোটদের জন্যও! আবুল হাসনাত নামটি ছিল তাঁর সাহিত্যিক অভিভাবকত্বের পরিচায়ক; পক্ষান্তরে মাহমুদ আল জামান সৌকুমার্যের–যেন গাছের একটি কাণ্ডের দুটি শাখা! আমাদের সাহিত্যাঙ্গনের সত্যিকারের এই সজ্জন মানুষটির বিয়োগজনিত শূন্যতা অনুভূত হবে অনেক দিন!
★
[রচনাটির আরেকটু উন্নীত পাঠ থাকছে আমার প্রকাশিতব্য ‘স্মৃতিতে ও সান্নিধ্যে’ বইয়ে। বর্তমান পাঠ তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখেছিলাম। আমার পুরোনো ফেসবুক একাউন্টের সঙ্গে হারিয়ে গেছে।]