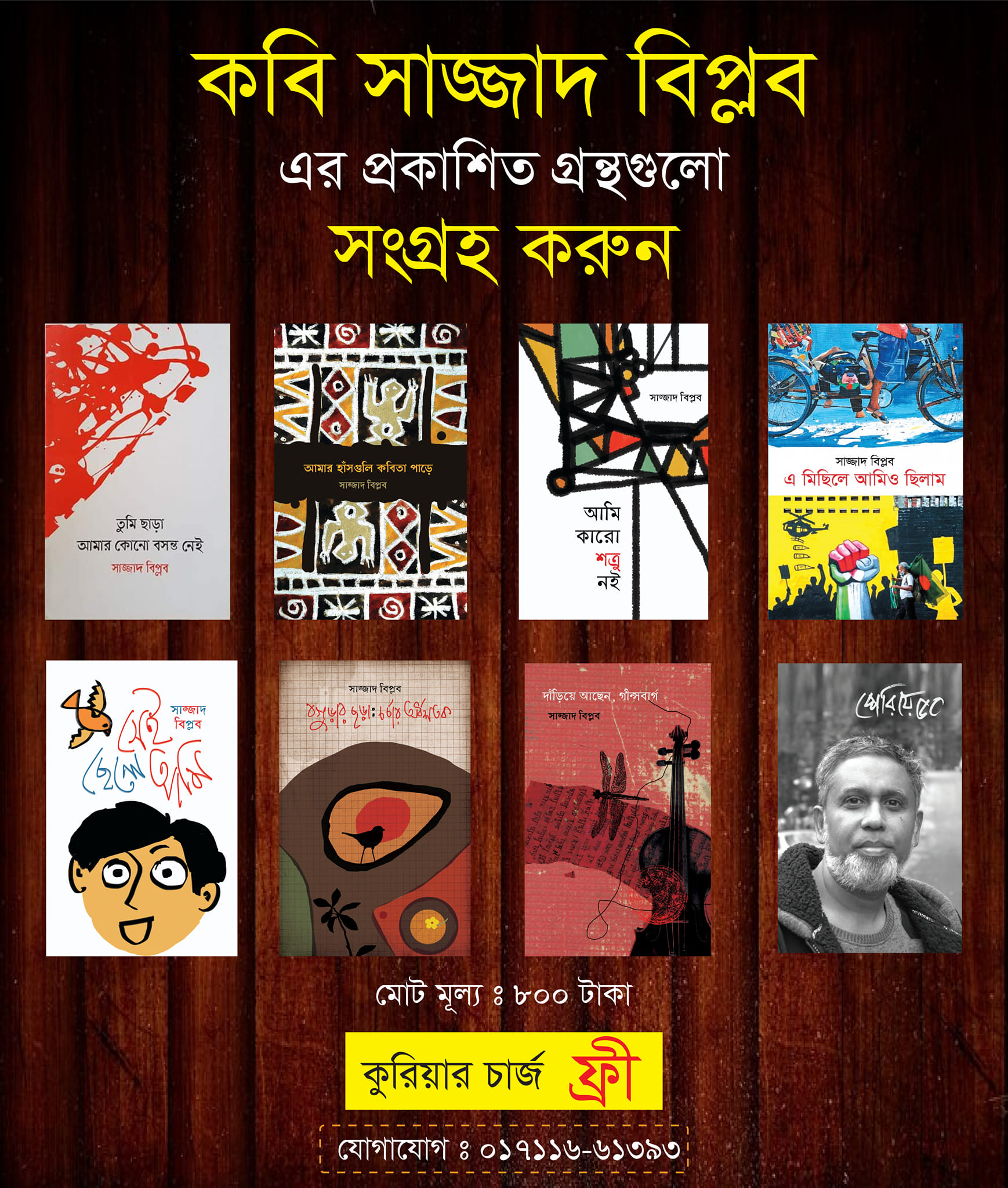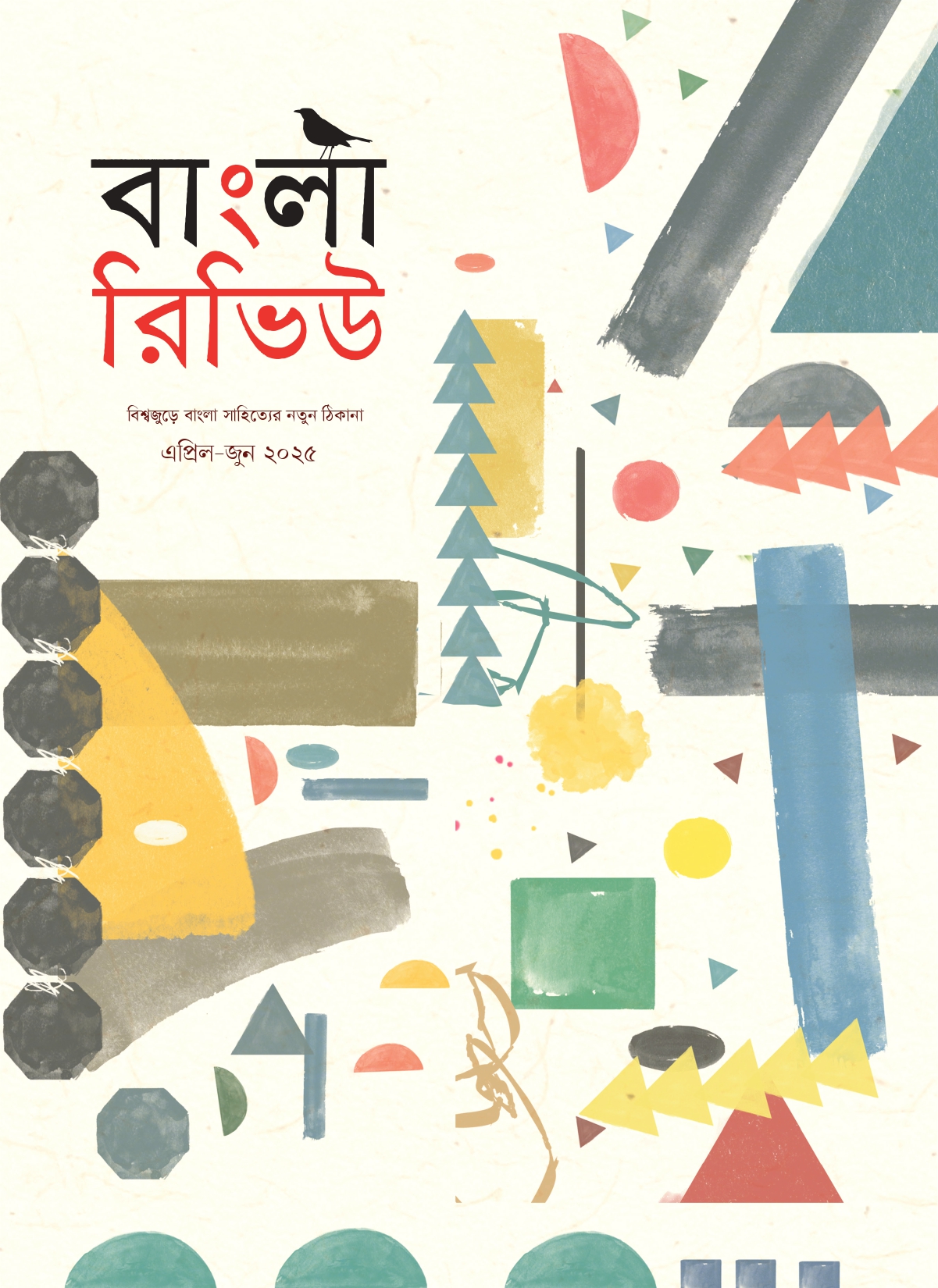তৈমুর খান
“হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো—
তখন পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল
সে-অন্ধকার মাটিতে আনলো কেতকীর গন্ধ,
রাতের অলস স্বপ্ন
এঁকে দিল কারো চোখে,
সে-অন্ধকার জ্বেলে দিলো কামনার কম্পিত শিখা
কুমারীর কমনীয় দেহে।
কেতকীর গন্ধে দুরন্ত,
এই অন্ধকার আমাকে কী ক’রে ছোঁবে ?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।”
(মুক্তি)
বাংলা কাব্য-সাহিত্যে চিরদিনই নিজেকে নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর নিঃসঙ্গ করে রেখেছিলেন কবি সমর সেন। মেকি জীবনের মোহ কোনোকালেই কবির ছিল না। তাই নিজের অন্ধকারে নিজেরই মুক্তি উপলব্ধি করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও, বিদেশে বসবাস করেও ঐতিহ্যবর্জিত অতি আধুনিকতায় কখনো প্রগতিশীল হতে চাননি। যে মধ্যবিত্ত জীবনের বৃত্তে তিনি অবস্থান করেছিলেন, তা থেকে বেরিয়ে আসারও চেষ্টা করেননি। তাকে কেউ কবি বলুক এটাও তাঁর কাম্য ছিল না। কিন্তু আধুনিক জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয়, নাগরিক জীবনের ক্লান্ত ক্লেদাক্ত বিষাক্ত ছোবল তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সেইসব দীর্ঘশ্বাস, কষ্ট ও ধ্বংসকে কবিতায় লালন করেও ইতিহাসবোধের প্রেক্ষিত থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেননি। বাস্তবতার রুক্ষ শুষ্ক রূপকে উপেক্ষা করেও রোমান্টিক স্বপ্নাদর্শে উন্মুখ হতে চাননি। তথাকথিত প্রেমও কবির সৃষ্টিতে সহায়ক হয়নি। একই সময়ে বহু কবির ভিড়েও তাই সমর সেনকে আলাদা করে চেনা যায়।
১০ অক্টোবর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সমর সেনের জন্ম। আদি পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন তাঁর পিতামহ। পিতার নাম ছিল অরুণচন্দ্র সেন। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক। ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি-এ ও এম-এ (১৯৩৮) পাশ করেন। তিরিশের দশক থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করে পূর্ণ খ্যাতির সময় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎই কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর রচিত কবিতা গ্রন্থগুলি হল :’কয়েকটি কবিতা’ (১৯৩৭), ‘গ্রহণ’ (১৯৪০), ‘নানা কথা'(১৯৪২), ‘খােলা চিঠি'(১৯৪৩), ‘তিন পুরুষ’(১৯৪৪) এবং পরে সংকলিত ‘সমর সেনের কবিতা'(১৯৫৪)। ‘বাবুবৃত্তান্ত’ (১৯৭৮) তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। চাকরি জীবনের সূচনাতেই অল্প কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। নিউজ এডিটর হিসেবে কয়েক বছর ‘আকাশবাণীতে’ও ছিলেন। পরে স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাব এডিটর হয়েছিলেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে অনুবাদকের কাজ নিয়ে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এসে কয়েক মাস একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করেন। তারপর হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় যোগ দিন। মতের অমিল হওয়া সে চাকরিও ছেড়ে দেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন কবিরের আহ্বানে ইংরেজি ‘নাউ’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু এখানেও মতবিরোধ দেখা দিলে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ওই পত্রিকা ছেড়ে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ইংরেজি ‘ফ্রন্টিয়ার’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি নকশাল ঘেঁষা রূপে খ্যাত হয়েছিল। সেই সময় থেকে সমর সেনকে বলা হত বিপ্লবী সম্পাদক। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি বিপ্লবী আদর্শে নির্ভিকভাবে পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন। ২৩ শে আগস্ট ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ৭১ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।
সংখ্যায় খুব কম লিখলেও সমর সেনের কবিতা একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছে। নতুন কাব্যরীতির ধারায়, রোমান্টিকতা বর্জিত ভাষা প্রয়োগে তাঁর কবিতাগুলি আলাদা মাত্রা লাভ করেছে। সৌখিন মজদুরির বদলে তাঁর সাহিত্য অভিজ্ঞতা ও আবেগের অকপট প্রকাশে মনোযোগ দাবি করে। বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী বলেই নয়, জীবন ও যুগ-যন্ত্রণাকে তিনি নিরপেক্ষ ও নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছেন। হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ ও আর্তি তাঁর কবিতাকে আজও জীবন্ত করে রেখেছে। গদ্য ছন্দে সহজ সরল ও প্রত্যক্ষ ভাবের প্রকাশে নাগরিক জীবনবোধের ক্ষয়িষ্ণু চেতনা-ই তাঁর কবিতার মৌল আবেদন। অবশ্য মধ্যবিত্ত সমাজেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা ও বেদনার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। তাই খুব সহজেই তিনি সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গেছেন। প্রজ্ঞায় বিষ্ণু দের কাছাকাছি অবস্থান করেও বিষ্ণু দের দুরূহ দুর্বোধ্যতা থেকে তিনি বহু দূরে সরে এসেছিলেন। কুশ্রিতা-কদর্যতার দিকেই তিনি নজর দিয়েছিলেন বেশি। সাম্যবাদের আদর্শেই সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যাকে তিনি সমর্থন করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র। গড়ে উঠেছে ডায়লেকটিক্ দৃষ্টিভঙ্গি। ‘প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি’—এই একটি পঙক্তির ভেতর দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন আধুনিক মানুষের ক্লান্তি, সংশয়, হতাশা ও বেকারত্বকে। যে জীবন আশাভঙ্গের শিকার তার পরিণতি সিগারেটের মতোই। ঘুমহীনতার অবসাদ, আসলে প্রেমহীন মনুষ্যত্বহীন সমাজ পণ্যবস্তুর মতো হৃদয়হীন এক যন্ত্র-যুগের ফসল। তাই ‘বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমিতে’ বেকার প্রেমিক দিশেহারা। পঁয়ত্রিশ বছরের কেরানি জীর্ণ বৃদ্ধ।জিভে স্বাদ নেই। ‘ধূসর’ শব্দটির মধ্য দিয়ে জীবনবোধের সমূহ ক্লান্তি, অবসাদকে কবিতায় টেনে এনেছেন। প্রেমের বিকৃতি, ছদ্মতাকে খুব সহজেই প্রকাশ করেছেন একটি উপমায়—
“স্যাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম!”
শুধু প্রেমের মিথ্যাচার মুখোশই নয়, নাগরিক জীবনের ক্ষয়, ক্লেদ, গ্লানি ও নৈরাশ্যের সীমাহীন সাম্রাজ্যকে তিনি রূপ দিতে পেরেছেন—
“মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি”
শ্বাসরোধকারী সভ্যতার অন্ধকারকেই কবি নেমে আসতে দেখলেন। জীবনযাত্রা এখানে স্তব্ধ হতে বাধ্য। রোলারের শব্দে ঘোর ধরে আছে।বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল এবং তার চকিত ঝলক দেখা গেলেও গলানো পিচের গন্ধ তা ঢেকে দিয়েছে। কংক্রিটময় প্রাণস্পন্দনশূন্য এই জীবনের একঘেয়েমি থেকে কবি তো মুক্তিই চান। কারণ কবিতার পরের চরণেই তিনি লেখেন আরো ভয়ংকর ক্ষুধার্ত বিধ্বস্ত মানুষের ছবি—
“যতদূর চাই, ইটের অরণ্য,
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ”
এই কান্না তো সেই যুগের কান্নাই, ইটের অরণ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তবুও কি ক্ষীণ আশার পদধ্বনি নেই তা বলে? অবশ্যই আছে। মাঝে মাঝেই শোনা গেছে—
“ঘুন ধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণি ত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার।”
সমর সেন রোমান্টিকবিরোধী হলেও তিনি রোমান্টিকতার হাতছানি ভুলতে পারেননি। মাঝে মাঝেই বিশ্রাম চেয়েছেন। মাঝে মাঝেই রোমান্টিক স্পর্শে নিজের ক্লান্তিকে একটু জুড়িয়ে নিতে চেয়েছেন—
“অনেক,অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দু’ধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।”
মহুয়ার দেশের রোমান্টিক হাতছানি কবিকে আকর্ষণ করে।দেবদারুর দীর্ঘ রহস্যের সঙ্গে সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস যেমন সব নির্জন-নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে, তেমনি মহুয়া ফুলের গন্ধও নেমে আসে ক্লান্তিকে দূর করার জন্য। কবি ব্যঙ্গের কশাঘাতে যেমন নিজেকেও মুক্তি দেন না, তেমনি রবীন্দ্র কবিতার চরণ ভেঙে অথবা উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়ে দেন ভঙ্গুর বাস্তবের কদর্য রূপ কতখানি মারাত্মক—
“কেটেছে বিশ বছর
রাত কত হল
এ প্রশ্নের মেলেনি উত্তর।
অনেকের দেহ মেদোচ্ছল,
অনেকের মনে পড়েছে কড়া।
ভারা ভারা ধান কাটা হয়নি সারা।”
এই প্রসঙ্গে ‘আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা’ গ্রন্থে ড.বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন , “এসকল উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করা কবির উদ্দেশ্য নয়, রবীন্দ্রনাথের সুন্দর ও সুস্থ কাব্যজগতের পটভূমিকায় পঙ্গু জীবনের ছবি এঁকে বর্তমানের অসম্পূর্ণতাকে প্রকট করে দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য।” আমরা জানি বিষাদ আর ধ্বংসময়তার মধ্যেও সমর সেন উত্তরণ চেয়েছেন। অন্ধকার কেটে কেটে আনতে চেয়েছেন দিন। তাঁরই উপসংহারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন নবযুগের যাত্রা। সমর সেনের ধ্বংসের কাকেরা গান গেয়েছে। নারীরা প্রেমে সুখ পায়নি।সন্তান ধারণেও সুখ হয়নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এসে সেখানেই বলেছেন ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত’।