আবু তাহের সরফরাজ
প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে দাসদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করা। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত রাখতে এসব দাস সর্বাত্মক মেধা ও শ্রম বিসর্জন দেবে। আর, এর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান দাসদেরকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেবে। মানে, প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক সবসময়ই দেয়া ও নেয়ার ভেতর দিয়েই চালু থাকে। এর কোনো-রকম এদিক-সেদিক হলে সম্পর্ক আর থাকে না। এই সত্য উপলব্ধি করেই আশির দশকের কবিরা ছোটকাগজ কেন্দ্রিক কবিতাচর্চায় রীতিমতো আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বেশ কয়েকটি ছোটকাগজকে কেন্দ্র করে আশির কবিরা গোষ্ঠিবদ্ধ হতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, দৈনিক খবরের কাগজের সাহিত্যপাতা সাহিত্যের নামে পাঠকদের কাছে যা পরিবেশন করে তা আসলে ভূষিমাল। ভূষি গরু-ছাগলের খাদ্য, মানুষের নয়। এই অনুপ্রেরণায় তাদের কাব্যযাত্রা বন্যার স্রোতের মতোই বেগবান হয়ে ওঠে। গোষ্ঠিভিত্তিক ছোকাগজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: গাণ্ডীব, পেঁচা, একবিংশ, অনিন্দ্য, পূর্ণদৈর্ঘ্য, প্রসূন, লিরিক, ছাঁট কাগজের মলাট ও নিসর্গ। এসব ছোটকাগজে ওই দশকের কবিরা দৈনিক পত্রিকার প্রভাব ডিঙিয়ে নিজেদের রুচি শিল্পমেধাকে প্রকাশ ঘটাতে থাকেন। ফলে, আগের দশকের কবিতার নির্মাণশৈলী ও বিষয়-চিন্তা রহিত হয়ে যায়। ছোটকাগজ চর্চা ছড়িয়ে পড়ে বৃহৎ পরিমণ্ডলে। এই চর্চা এতটাই গতিশীল হয়ে ওঠে যে, প্রতিষ্ঠানের সিলমারা সাহিত্য-বলয় থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে ছোটকাগজ-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা বেশ একটা আন্দোলনের রূপ পায়। এই ধারা আশির কবিদের শিল্পভিত্তি তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এই যজ্ঞে কবিতার বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাঠকের চোখে পড়ে। প্রথমত, প্রথা ভাঙার প্রবণতা। এই দশকের কবিরা আগের দশকের বিবৃতি কিংবা স্লোগানধর্মী কবিতার ঘেরাটোপ ভেঙে নতুন একটি ধারা সৃষ্টির চেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টার অগ্রগণ্য সারথি সৈয়দ তারিক। কেননা, তার কবিতা তার সময়ের আরসব কবির কবিতা থেকে কেবল রূপ-বৈচিত্র্যেই আলাদা নয়, ভাষাশৈলীতেও স্বতন্ত্র।
কাব্যযাত্রার প্রারম্ভিক যাত্রাপথেই তিনি নানা প্রকরণে নীরিক্ষার ভেতর দিয়ে কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কবিতার বিষয়কে নানা রূপে বিচিত্র অনুষঙ্গে তিনি ভাষিক ইশারায় সৃষ্টি করেছেন। এই যাত্রায় তিনি স্বকীয় কাব্যশৈলী নির্মাণ করে নিয়েছেন। কেবল শৈলী নয়, কবিতার বিষয় হিসেবে তার নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য পাঠকের চোখ এড়ায় না। সুফি-দর্শনকে তিনি কবিতার ভেতর দিয়ে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেন। বিষয়ভিত্তিক এই কাব্যযাত্রা আশির আরকোনো কবির কবিতায় আমাদের চোখে পড়ে না। সেই অর্থে সৈয়দ তারিক আশির কবিতা-ভূমে একক বৈশিষ্ট্য নির্মাণের রূপকার। ফলে, তার কবিতা পাঠে সহজেই তার স্বাতন্ত্রতা চিহ্নিত করা সম্ভব। আশির দশক ছাড়িয়ে পরবর্তী দশকের কবিতাতেও তার মতো সুফি-দর্শনকে জীবনের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে আশ্লেষ করার প্রবণতা আমাদের চোখে পড়ে না। সৈয়দ তারিকের সমসাময়িক কবিদের কবিতায় নানা নীরিক্ষা ও রূপ-বৈচিত্র্য আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু তারিক যে ভিত্তির ওপর কবিতাকে শৈল্পিক রূপ দেন সেই রূপ আর কারো কবিতায় আমরা দেখি না। সতীর্থ কবিদের কাব্যযাত্রায় সহযাত্রী থেকেও তারিক বাংলা কবিতায় পৃথক একটি সরণি ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। তার আগের দশকের কবিতায় ঐতিহ্য ও মিথের ব্যবহার খুবই কম এসেছে। কিন্তু আশির দশকের কবিরা আবারও সেই ধারা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। ভারতীয় ও ইউরোপীয়সহ কারো কারো কবিতায় ইসলামি মিথের ব্যবহারও ব্যাপক ভিত্তিকে চর্চা হতে থাকে। এই ধারাবাহিকতা তারিকের কবিতা ধারণ করলেও তিনি নিজস্ব একটি ঢঙ ও প্রকরণ তৈরি করে নেন কবিতার অবয়ব নির্মাণে। আর এজন্য তিনি সুফি-দর্শনকে কেন্দ্র করে জীবনের নানা গলি-উপ-গলিতে ঢুঁ মারতে শুরু করলেন। যা-যা দেখলেন সেসব চিত্রকরের মতো শব্দের রঙে চিত্রিত করতে লাগলেন কবিতায়। মূলত সুফি-দর্শন ও আধ্যাত্মিকতাই সৈয়দ তারিকের কবিতার প্রাণ-ভোমরা। বিষয়টি বিশেষভাবে চোখে পড়ে তার কবিতার বইগুলোর শিরোনাম দেখলে। ছুরি হাতে অশ্ব ছুটে যায়, মগ্ন তখন মোরাকাবায়, নাচে দরবেশ মাস্ত হালে, আমার ফকিরি, ঊনসন্ন্যাসী এবং আত্মায় ছিল তৃষ্ণা। প্রতিটি বইয়ের শিরোনামের আড়ালে রয়েছে সৈয়দ তারিকের সুফিবাদী চেতনার শৈল্পিক স্ফুরণ।
আমার মাবুদ তিনি, চেতনায় নিত্য যাঁর বাস;
নিটোল শরীর তাঁর, অপরূপ আলোর প্রতিমা;
গভীর মোরাকাবায় নম্র হয় যখন নিঃশ্বাস
উদ্ভাসিত হন তিনি, ছিন্ন হয় অসীমের সীমা।
বন্ধ চোখে দেখি তাঁকে, তাঁকেই তো দেখি চোখ খুলে,
সকল মানুষে তিনি কেন্দ্র হয়ে নীরবে থাকেন;
প্রাণী ও উদ্ভিদে গূঢ় প্রণোদনা দেন মর্মমূলে
জড়ের হৃদয়ে তিনি কোয়ার্কের নকশা আঁকেন।
ছড়ানো আকাশ তিনি, বয়ে যাওয়া তিনিই সময়,
প্রজ্ঞালোকে বাস তাঁর, অনন্য বিলাস তাঁর প্রেমে;
অবিদ্যা সেও তো তিনি: তিনি ছাড়া আর কেউ নয়,
নফসানিয়াতে তিনি নিজেই আসেন নিচে নেমে।
শুধু তাঁর নাম জপে, শুধু তাঁকে অপলক দেখে
আজ বলা যেতে পারে― সবিনয়ে― চিনেছি নিজেকে।
(আমার মাবুদ তিনি)
এই কবিতা পাঠে পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন, সুফিবাদী কবি হিসেবে সৈয়দ তারিকের অন্তর্বোধ। তারিক বিশ্বাস করেন, তার উপাস্য সবসময়ই তার চেতনায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তার শরীর নিটোল এবং তিনি মূর্তিমান আলোর অবয়ব। এখানে এসে কোরআনের সূরা নূর আমাদের মনে পড়ে। যেখানে লেখা, “আল্লাহর নূরের উপমা যেন একটি দীপাধার। যার ভেতর রয়েছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি কাচের একটি আলমারির ভেতর রাখা আছে। কাচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। বরকতময় জয়তুন গাছের তের দিয়ে এই প্রদীপ জ্বালানো হয়। যা কেবল পূর্ব দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত) নয়, আবার কেবল পশ্চি দিকেরও (সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত) নয়। সেই প্রদীপকে আগুন স্পর্শ না করলেও প্রদীপের তের যেন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। নূরের ওপর নূর!” এখানে আল্লাহর নূরের সত্তার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা মানুষকে উদাহরণ দিয়ে বোধগম্য করা হয়েছে। আল্লাহর প্রকৃত সত্তা বোঝার মতো ক্ষমতা ত্রিমাত্রিক জীব হিসেবে মানুষের নেই। তবে প্রদীপের উদাহরণ থেকে মোটামুটি এক ধরনের ধারণা আমরা পাই। সেই ধারণার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, পরম সত্তা নূরের শরীরী একজন অবয়ব। প্রতিদিনের যাপিত-বাস্তবতায় সেই নূরের ছটা আমরা অনুভব করতে পারি না। দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মার ভেতর ডুব দিয়ে গভীর মোরাকাবায় স্থিত হলে মানুষ বিনয়ী হয়ে ওঠে। পরমের উপলব্ধি ঘটলে মানুষ নিজের ক্ষুদ্রত্বও উপলব্ধি করতে পারে। যখন এই উপলব্ধি হয় তখনই কেবল পরম সত্তার নূর তার আত্মার আয়নায় উদ্ভাসিত হয়। এসময় মানুষের অবস্থা এমন হয় যে, চোখ বন্ধ করলেও পরম সত্তার নূর তার সামনে উদ্ভাসিত হয়। আবার, চোখ খুললেও সেই নূর। এই প্রক্রিয়াকে সুফি-দর্শনে বলা হয় ফানাফিল্লাহ। এই অবস্থায় স্থিত মানুষ প্রতিটি সৃষ্টির ভেতর পরমের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। প্রতিটি সৃষ্টির অন্তর্গহনে গূঢ় প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেন পরম স্রষ্টা। আপাতদৃষ্টিতে যাকে আমরা প্রাণহীন দেখছি তার ভেতরও প্রাণের স্ফুরণ তিনি নীরবে ঘটিয়ে চলেন। অতি-পারমাণবিক কণা কোয়ার্ক বিষয়ে যাদের ধারণা আছে তারা জানেন, পরমাণুর মৌলিক কণা এই কোয়ার্ক। লক্ষণীয় যে, কোয়ার্ক শব্দটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সৈয়দ তারিক সুফি-দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের চমৎকার যোগসূত্র নির্মাণ করেছেন। বস্তুত, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। যে বিরোধ আমরা শুনি তা মূলত ধর্ম-ব্যবসায়ী ও বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীদের ভেতরকার বিরোধ। সৈয়দ তারিক ধর্ম-ব্যবসায়ীও নন, বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীও নন। তিনি কবি। মোরাকাবায় স্থিত হয়ে ফানাফিল্লাহ স্তরে পৌঁছুতেই তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এর বাইরে কোনো ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি তার নেই। আর তাই তিনি প্রতিটি সৃষ্টির ভেতর অন্তর্লীন প্রবাহে বয়ে যাওয়া পরম সত্তার নূরকে দিব্যচোখে দেখতে পান। তারিক মনে করেন, পরম সত্ত কে মানুষ প্রজ্ঞা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। কারণ, প্রজ্ঞার ভেতর দিয়েই পৌঁছানো সম্ভব পরম সত্তার কাছে। তাঁর প্রেমে যে মানুষ লীন হয়ে যান তার অন্তর্করণ আনন্দের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। কোনো কিছুরই অভাব সে আর বোধ করে না। জীবনের এই পূর্ণতার চেয়ে পার্থিব বিলাস নিশ্চয়ই প্রধান নয়। শেষমেষ কবি বিনয়ের সঙ্গে পাঠককে জানাচ্ছেন, পরম সত্তাকে উপলব্ধি করেই তিনি নিজেকে চিনেছেন। যুগে-যুগে সকল সুফির সাধনা মূলত এটাই। নিজেকে চেনা। মনে পড়ছে লালনের সেই পঙক্তি, ‘একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা।’
সুফি-দর্শনকে কেন্দ্র করে সৈয়দ তারিক ছাড়া আর কোনো কবি কবিতায় এমন ব্যাপকতর ভাবসম্পদ গড়ে তুলতে পেরেছেন কিনা, তা গবেষণাযোগ্য। কারো কারো কবিতায় ছিটেফোটা সুফিতত্ত্ব আমরা পেয়েছি, কিন্তু তারিকের মতো সর্বস্ব আকুতি দিয়ে আর কোনো কবি সুফি-দর্শনকে কবিতায় প্রকাশ করতে পারেননি। বলতে কী, তারিকের জীবনযাপনও সুফিবাদী তরিকায় পরিচালিত হয়। আত্মদর্শন ও যাপিতজীবনকে তিনি আলাদা মেরুকরণে গড়ে তোলেন না। এখানেই পাঠকের কাছে তারিকের বিশেষ গ্রহণযোগ্য তৈরি হয়।
আত্মদর্শনকে কবিতার শারীরিক অবয়য়ে রূপ দিতে তারিক যেসব চিত্রকল্প নির্মাণ করেন সেসব চিত্রকল্প বাঙালি পাঠকের হৃদয়-সংলগ্ন। এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ মুসলমান। শৈশব থেকেই মুসলিম সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে তাদের বেড়ে ওঠা। ইসলামি মিথ ও ঐহিত্য বাঙালির চেতনায় গ্রোথিত। এদেশের ইসলামি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মূলত বিভিন্ন সময়ে বাংলায় আগত সুফিদের প্রচারণায়। ফলে, সুফিবাদী চেতনার এক ধরনের প্রবাহ বাংলার মুসলিম জনমানসে লক্ষ্য করা যায়। এই চেতনার সঙ্গে তারিকের কবিতার হৃদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই পাঠক তারিকের কবিতা পাঠ করেন আগ্রহ নিয়ে। তার কবিতায় যেসব চিত্রকল্প উঠে আসে সেসব চিত্রকল্পের সঙ্গে বাঙালি মুসলিম উত্তরাধিকার সূত্রেই পরিচিত।
ঝঞ্ঝামুখর সমুদ্র তুমি
আমার জাহাজে তুমি কম্পাস,
তোমাকেই দেখি― শুভ্র পদ্ম
দেখি ভেসে যাও সাদা রাজহাঁস।
জ্যোৎ¯œায় তুমি পূর্ণচন্দ্র
কৃষ্ণবিবরে তুমি আঁধার,
সবই যদি তুমি তাহলে আমি কে?
জবাব মেলে না এই ধাঁধার।
(ঝঞ্ঝামুখর সমুদ্র তুমি)
মরমী কণ্ঠশিল্পী আবদুল আলীমের গাওয়া ‘এই যে দুনিয়া’ গানটি বাংলার ঘরে ঘরে ব্যাপক জনপ্রিয়। গানের দুটি পঙক্তি হচ্ছে, তুমি ভেস্ত তুমি দোজখ তুমি ভালো-মন্দ/তুমি ফুল তুমি ফল তুমি তাতে গন্ধ।’ এই তত্ত¡ই আসলে সুফি-দর্শনের মরমী উপলব্ধি। এই উপলব্ধি ঐতিহ্যগতভাবে লালণ করে চলেছে বাংলার মুসলিম সমাজ। সৈয়দ তারিক এই উপলব্ধিজাত অন্তর্বোধ থেকে উচ্চারণ করছেন, পরম সত্তা ঝঞ্ঝামুখর সমুদ্র। সেই সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে চলেছেন কবি। অথচ সমুদ্রের জল ঝড়ে উথাল-পাথাল। জাহাজযাত্রীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। জাহাজি দিকভ্রান্ত। পাহাড় সমান ঢেউ ডিঙিয়ে জাহার যে কোথায় ভেসে যাচ্ছে, সকলেই শঙ্কিত। কিন্তু জাহাজে রয়েছে দিক-নির্দেশক কম্পাস। দিক-হারানোর কোনো সুযোগ তো নেই। কবি বলছেন, ঝড় হয়ে পরম সত্তা নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করছেন। আবার, কম্পাস হয়ে সেই তিনিই জাহাজিদের সঠিক দিকের নিশানা বাৎলে দিচ্ছেন। ঝঞ্ঝামুখর সমুদ্র ও কম্পাসের চিত্রকল্পে পরম সত্তার যে প্রকাশ সৈয়দ তারিক কবিতায় প্রকাশ করছেন তার শৈল্পিক কারুকাজ অনন্য। শুভ্র পদ্ম, রাজহাঁস, পূর্ণচন্দ্র, কৃষ্ণবিবরের অন্ধকার― সকল কিছুই পরম সত্তার ঐশ্বরিক প্রকাশ হিসেবে তারিক দেখতে পান। তার ভেতর প্রশ্ন জেগে ওঠে, সকল কিছুই যদি সেই পরম সত্তা তাহলে আমি কে? এই প্রশ্ন ধাঁধার মতো তাকে দ্বিধায় ফেলে দ্যায়। তিনি জবাব মেলাতে পারেন না। এই কবিতায় পরম সত্তার প্রকাশ হিসেবে যেসব চিত্রকল্প তারিক উপস্থাপন করেছেন সেসব চিত্রকল্প পাঠকের মননেও প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো চিত্রছাপ রেখে যায়। পাঠকও পড়ে যান গূঢ় ধাঁধায়।
যদিও বাতাসে খাচ্ছে পাক
আজ সবার নিন্দাবাদ
যেহেতু ধরেছি হাত তোমার
দিই স্লোগান: জিন্দাবাদ।
কেন থরো থরো প্রাণ আমার
যার বোঝার সেই বুঝুক
যেহেতু সকলে খাই না মদ
তৃষ্ণা যার সেই খুঁজুক।
(ব্রহ্মমূর্ধা)
ছন্দের কৃৎ-কৌশল সৈয়দ তারিকের মজ্জাগত। তবে প্রথাগত ছন্দে তিনি খুব বেশি কবিতা লেখেননি। কবিতার ভেতর তিনি ছন্দকে ভেঙেছেন, আবার নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলেছেন। এই বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ ‘ব্রহ্মমূর্ধা’ কবিতাটি। এটি মাত্রা বৃত্ত ছন্দের কবিতা। মাত্রাগুলো চিহ্নিত করা যাক।
যদিও বাতাসে (ছয় মাত্রা)/খাচ্ছে পাক (পাঁচ মাত্রা)/
আজ সবার (পাঁচ মাত্রা)/নিন্দাবাদ (পাঁচ মাত্রা)
যেহেতু ধরেছি (ছয় মাত্রা)/হাত তোমার (পাঁচ মাত্রা)/
দিই স্লোগান (পাঁচ মাত্রা):/জিন্দাবাদ। (পাঁচ মাত্রা)/
কেন থরো থরো (ছয় মাত্রা)/প্রাণ আমার (পাঁচ মাত্রা)/
যার বোঝার (পাঁচ মাত্রা)/সেই বুঝুক (পাঁচ মাত্রা)/
যেহেতু সকলে (ছয় মাত্রা)/খাই না মদ (পাঁচ মাত্রা)/
তৃষ্ণা যার (পাঁচ মাত্রা)/সেই খুঁজুক (পাঁচ মাত্রা)।
দেখা যাচ্ছে, প্রথম পঙক্তি শুরু হয়েছে ছয় মাত্রা দিয়ে। এর পরের পর্বগুলো পাঁচ মাত্রার। আমার দ্বিতীয় পঙক্তি শুরু হয়েছে ছয় মাত্রা দিয়ে। এর পরের পর্বগুলো পাঁচ মাত্রার। একইভাবে তৃতীয় পঙক্তি শুরু হয়েছে ছয় মাত্রা দিয়ে। এর পরের পর্বগুলো পাঁচ মাত্রার। চতুর্থ পঙক্তিও শুরু হয়েছে ছয় মাত্রা দিয়ে। এর পরের পর্বগুলো পাঁচ মাত্রার। ছন্দের কুশলী এই প্রয়োগ সৈয়দ তারিকের কবিসত্তার শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। প্রথাগত ছন্দেও তিনি কবিতা লিখেছেন। এরই পাশাপাশি কবিতায় ছন্দের নীরিক্ষাও তিনি চালিয়েছেন। এসব কবিতা পাঠে পাঠককে স্বীকার করতেই হবে, ছন্দের নীরিক্ষায় তারিক সার্থক। নীরিক্ষার প্রবণতা তারিকের কাব্যযাত্রার প্রারম্ভিক সূচনাপর্ব থেকেই আমাদের চোখে পড়ে। নানা বৈচিত্র্যে রাঙানো তার কবিতার স্বর ও ছন্দের প্রকরণ। তারিকের ভাষ্য, ছন্দের কুশলী প্রয়োগে কবিতার বিষয় ও উপস্থাপনে যে বৈচিত্র্যের অভিঘাত তৈরি হয় সেটি ছন্দছাড়া কবিতার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আর এ কারণেই আমরা দেখি, প্রথাগত ছন্দের নিগড়ে কবিতার শব্দগুলো সজ্জিত না হলেও বাক্যের বুননে প্রতিটি শব্দ ছন্দের এক ধরনের ঢেউ তুলে যাচ্ছে। হতে পারে এটি ধ্বনির ব্যঞ্জনা। কিন্তু এই ব্যঞ্জনা সুরের যে মূর্ছনা ছড়িয়ে দ্যায় তা পাঠকের শ্রুতিকে আরাম দ্যায়। বাক্যগুলো পড়তে পাঠক আনন্দবোধ করে। এরই পাশাপাশি তার কবিতার বিষয় হিসেবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে অন্তর্বোধের মরমী উপলব্ধি। যে উপলব্ধি মূলত সুফি-দর্শনের সারাৎসার।



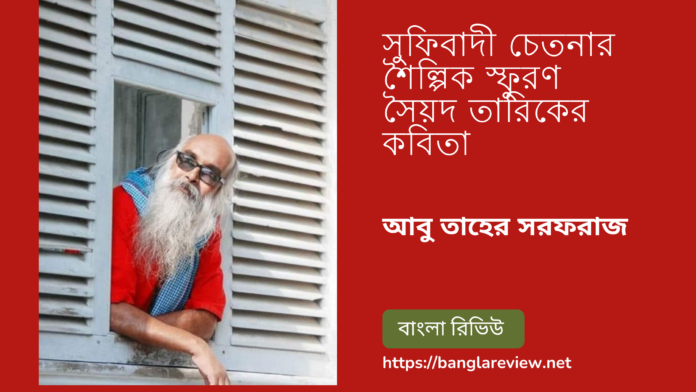
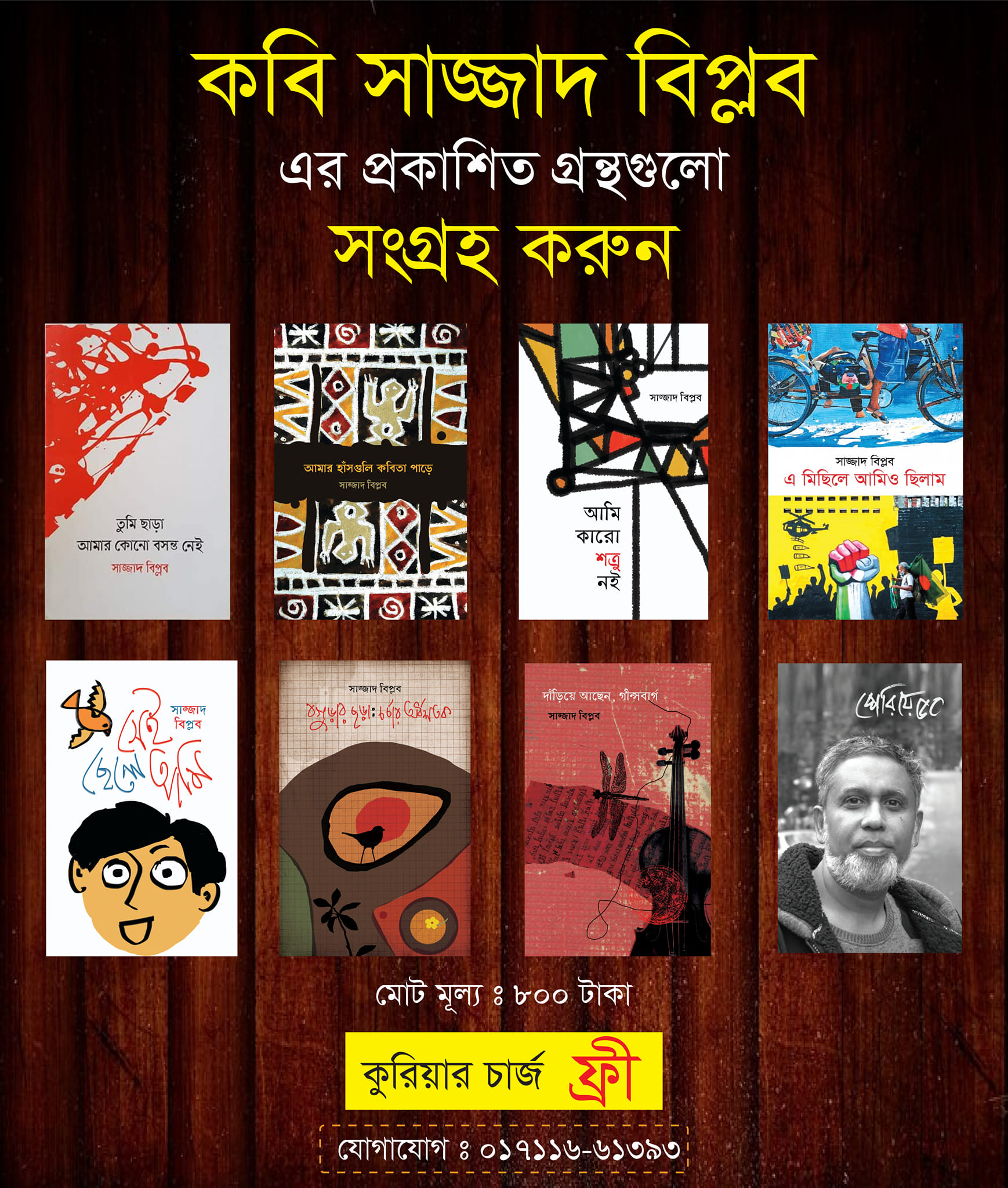
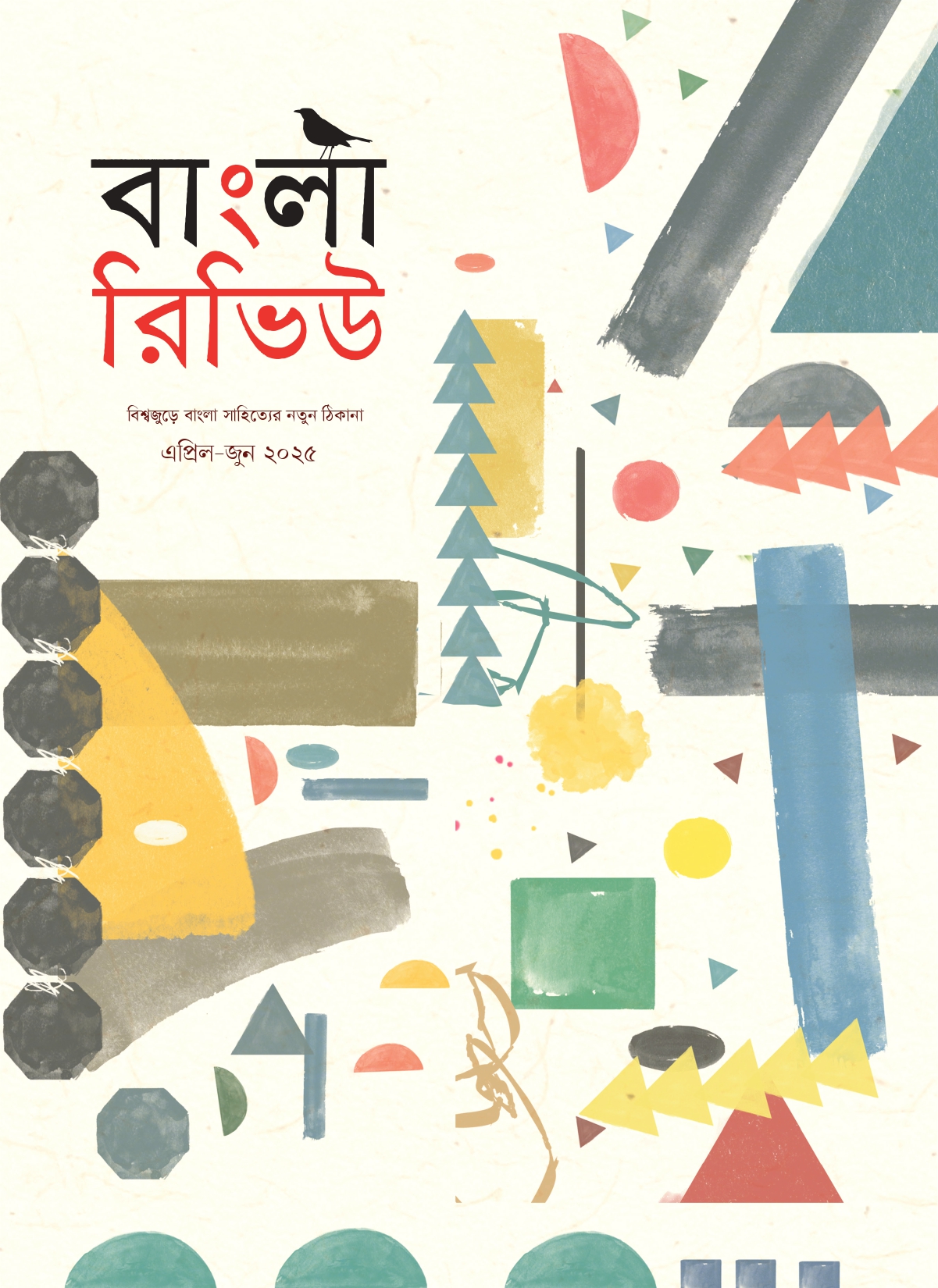


খুব ভালো লাগলো।