আবু তাহের সরফরাজ
কবিতার ভাষা শুধু অর্থের ভার বহন করে নিজেকে নিঃশেষ করে না। গদ্যের ভাষা বাজারের মিন্তি-বালকের মতো। ঝাঁকা বোঝাই অর্থের সওদা পাঠকের দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে প্রাপ্য মজুরি নিয়ে সে চলে যায়। কিন্তু কবিতার ভাষা বেড়াতে আসা মেহমানের মতো। হাতের বয়ে আনা অর্থের মিষ্টির বাকসো কেবল তার শুভেচ্ছার প্রতীক। তার আসল মূল্য ওইটুকুতে সীমাবদ্ধ নয়, এবং তাকে গদ্যের মতো পত্রপাঠ বিদায় দেওয়াও চলে না। তাকে মুখোমুখি নিয়ে বসতে হয়। শুনতে হয় তার না-বলা বাণীটুকু। যে কবিতার অর্থ তার বাচ্যার্থের সমান-সমান সেটি কবিতা হিসেবে অপকৃষ্ট। সে ঠং করে বাজা একটা আওয়াজ মাত্র, যার কোনো অনুরণ নেই। ভালো কবিতা বাজবে চেতনায় কিংবা হৃদয়ের তন্ত্রীতে, কাসর ঘণ্টার মতো অনেকক্ষণ ধরে। যে সুর কবির উদ্দিষ্ট ছিল না, বেজে উঠবে সেই সুরও, বলয়িত মন্দ্রিত হতে থাকবে গিরিকন্দরে উচ্চারিত ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেমন। কবিতা কোথাও না কোথাও আবেগের না হোক মননের কোনো না- কোনো প্রান্তকে স্পর্শ করবে, জ্বলে উঠবে কোথাও আলো, ধসে পড়বে কোথাও পাথরের চাঁই। একটি কবিতা পড়লাম আর আমার মানসে চেতনায় কোথাও সামান্যতম কিছু ঘটলো না, তাহলে বুঝবো সেটি কবিতা নয়, স্বর্ণখণ্ড নয়, ভূষিমাল, হয়তো রঙচঙে তামা কিংবা রাং।
(কবিতা অন্তর্যামী/খোন্দকার আশরাফ হোসেন)
তো, কবিতা কী ও কেন সে বিষয়ে পষ্ট একটি ধারণা পাঠক হিসেবে আমরা পেয়ে গেলাম। কবিতা যে নানা রকম সেই হিসাব তো আমরা জানিই। কিন্তু নানা রকমের ভেতরও এক রকম বোঝাপড়া থাকে। একটি রকমের সাথে আরেকটি রকমের যোগসূত্র থাকে। সেসব সূত্র মিলিয়ে কবিতা হয়ে ওঠার একটি সাধারণ ও সহজ পাঠ খোন্দকার আশরাফ হোসেন আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা তার দেয়া পাঠের ওপর আস্থা রাখতে পারি। কেননা, তিনি মনস্বী ও মননশীল একজন সাহিত্যিক। ইংরেজি সাহিত্য পড়িয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতার পাশাপাশি লিখেছেন সাহিত্য-আলোচনা ও নানা রূপী প্রবন্ধ। বিদেশি ভাষা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। মানে, তার সৃজনশীলতা ও প্রজ্ঞা এতটাই স্থিত যে তার শিল্পবোধ শিল্পের প্রকৃত স্বরূপকেই আমাদের সামনে উন্মোচিত করে। সত্যি যে, শিল্পের সংজ্ঞায়নে কবিতার সংজ্ঞা অমীমাংসিত। অনেকটা রমণীর অন্তর্জগতের মতো। রমণীর অন্তর্মহলে কখন যে কী রঙ রাঙিয়ে যায়, মোহান্ধ পুরুষ কখনোই তার হদিস জানতে পারে না। কেবল বাইরের রূপ দেখেই সুন্দরের জ্ঞান তাদের হয়। কোনো কোনো পুরুষ একটু এগিয়ে রমণীর রুচি ও সংস্কৃতির খোঁজও কিছুটা করেন। তবে কোনোভাবেই জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না, সঙ্গমরত রমণী সঙ্গী পুরুষের জায়গায় আরেক পুরষকে কল্পনা করছে কিনা। সেটা জানাও সম্ভব নয়। সুন্দরী রমণীর যেমন সৌন্দর্যের এক রকম ধরণ আছে, একইভাবে কবিতার মীমাংসিত শিল্প-সংজ্ঞা চিহ্নিত করতে না পারলেও কাব্য-সৌন্দর্যের এক রকম ধরণ আছে। খোন্দকার আশরাফ হোসেন আমাদেরকে সেই ধরণ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। কেবল জানিয়েই দেননি, নিজের বোঝাপড়ার মানদণ্ডে লিখেছেন কবিতা। ‘জীবনের সমান চুমুক’ আশির দশকের শেষদিকে প্রকাশিত কবিতার বই। বইয়ের শিরোনামটি লক্ষ্যণীয়। কেননা, কবিতা তার কাছে ছিল জীবনের সমান চুমুকের মতো। জীবনের সমান মানে জন্ম থেকে মৃত্যুর আগপর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যাপন করা গোটা একটা জীবন। আর, চুমুক মানে মানব-জীবনকে রসিয়ে রসিয়ে একটু একটু করে পান করা। সক্রেটিস হেমলক বিষ পান করেছিলেন। আমরা প্রতিদিন চা পান করি। শরবত পান করি। হেমলক ও চা কিংবা শরবতের ভেতর কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর মতো চূড়ান্ত তফাৎ রয়েছে। কিন্তু উভয়ই মানুষ পান করেছে ও করছে। জীবনের বাইরের দিকটা দেখতে বেশ ফুরফুরে। যেন বসন্ত বাতাসে বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি বয়ে আনে। কিন্তু জীবনের ভেতর আরেকটা যে জীবন মানুষ সবসময় বয়ে নিয়ে চলেছে সেই জীবন আসলে কোনো মানুষই বইতে চায় না। এরপরও তাকে বয়ে যেতে হয়। খোন্দকার আশরাফ হোসেন সেই জীবনকেও বেশ রসিয়ে রসিয়ে পান করেন। না-করে অবশ্য উপায়ও নেই। ‘প্রার্থনায় নম্র হও পাবে’ কবিতায় তিনি লিখছেন:
আমাকে পাবে না প্রেমে, প্রার্থনায় নম্র হও পাবে
কামে-ঘামে আমি নেই, পিপাসায় তপ্ত হও পাবে।
পাখিরা প্রমত্ত হলে সঙ্গিনীকে ডেকে নেয় দেহের ছায়ায়
ছায়া নয়, রৌদ্রতাপ জ্বালাবার শক্তি ধরো, কেবল আমাকে
তপ্তজলে দগ্ধ করো, রুদ্ধ ক্রোধে দীপ্ত করো, পাবে।
পৃথিবীর সর্বশেষ কবি আমি অহঙ্কার আমার কবিতা
বিষাদে বিশ্বাসে পূর্ণ হৃদয়ের জলাধার ধরো।
কবিতায় উল্লিখিত ‘আমি’ আসলে জীবন। অথবা জীবনরূপী কবি স্বয়ং। প্রেম এক ধরনের শুশ্রæষা। অন্তর্দহনের শুশ্রূষা। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম শেষে রাত্রে ঘরে ফিরে নারীর নাভিমূলে নাক ডুবিয়ে আমরা কস্তুরি সৌরভ পাই। শ্রান্তি নেমে আসে আমাদের বুকের ভেতর। ভালো লাগার ঝিরঝির হাওয়া বইতে থাকে। অথচ জীবন কিন্তু সেখানে নেই। কেননা, এই নারী সুযোগ পেলে আরেক পুরুষকে তার সৌরভ বিলিয়ে দেবে। জনে-জনে যে সৌরভ বিকোয় সেই সৌরভ বাজারি, ব্যক্তিগত নয়। কত যে সংসার এই চক্রে পড়ে ভেঙে যাচ্ছে, কে তার হিসাব রাখে! কাম-উত্তপ্ত নারী-পুরুষ সঙ্গমরত অবস্থা ঘেমে ওঠে। সেই ঘামে একজনের শরীর আরেকজনের শরীরের সাথে লেপ্টে যায়। আর তাদের শীর্ষসুখ আরও বেড়ে ওঠে। কিন্তু জীবনের শীর্ষ-সৌন্দর্য তারা কেউ-ই খুঁজে পায় না। কারণ, কামে ও ঘামে প্রেম নেই। মানুষের তৃষ্ণার গন্তব্য কাম নয়, সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যের কাছে পৌঁছুতে হলে নারীরিক সৌন্দর্যের কাছে প্রার্থনায় বিনয়ী হয়ে যেতে হয়। কামে নয়, পিপাসায় তপ্ত হয়ে উঠতে হয়। তবেই সম্ভব জীবনকে ছুঁয়ে দ্যাখা। কামোত্তেজক হলে পাখিরা তার সঙ্গিনীকে ডানার নিচে ছায়ার ডেকে নেয়। কবি বলছেন, সেই রকম ছায়া-স্নিগ্ধতার ভেতর দিয়ে জীবনকে পাওয়া যাবে না। জীবনকে পেতে হলে সূর্যের উত্তাপের মতো শক্তি নিজের ভেতর ধারণ করতে হবে। তবেই পাওয়া যেতে পারে জীবনকে। এরপর কবি ঘোষণা দিচ্ছেন, পৃথিবীর শেষ কবি তিনি। এটাই তার অহঙ্কার। শেষ কবি বলতে সত্যি সত্যিই তিনি যে শেষ কবি তা কিন্তু নয়। তিনি সেটা বলতেও চাননি। তার বলার কথা হচ্ছে, জীবনকে কোথায় কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় সেই জায়গাগুলো তিনি চিহ্নিত করে নিতে পেরেছেন। যেটা সকল কবিরই এক ধরনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। মানে, জীবনকে বুঝে নেওয়া। তার অহংকার এখানেই যে, তিনি জীবনকে উপলব্ধি করেই তার কবিতার আয়োজনে মেতে ওঠেন মানুষ হিসেবে নিজের সত্তাকে আবিষ্কার করতে। জীবনে গভীর বিষাদ থাকলেও জীবনের প্রতি খোন্দকার আশরাফ হোসেন প্রগাঢ়ভাবেই বিশ্বাসী।
‘সুদূরের পাখি’ কবিতায় তিনি লিখছেন, ‘কী খুঁটছো সারাদিন অনন্তের পাখি/খুঁটছি যবের দানা, শস্যবীজ, খুঁটছি জীবন।’ অনন্ত মানে মহাকাল। মহাকালকে কবি পাখি হিসেবে কল্পনা করছেন। দেখছেন যে, সেই পাখি তার খাবার খাচ্ছে। একইসঙ্গে খাচ্ছে জীবন। শস্যবীজের মতো জীবনও অনন্তের পাখির খাবার। বিষয়টি প্রতীকী হলেও নিগূঢ় অর্থে পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবনের প্রতিই কবি ইঙ্গিত করছেন। মহাকাল ওই পাখির মতোই আমাদের জীবনকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। আর আমরা সেই ঠোকর খেয়ে আর্তচিৎকার করছি। যদিও সেই চিৎকারও প্রতীকী, এরপরও চিৎকার তো চিৎকারই। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের বেশির ভাগ কবিতার অন্তর্বয়ানে এই চিৎকার ধ্বনিত হয়েছে। খুব সংবেদনশীল পাঠক ছাড়া সেই চিৎকার সাধারণ পাঠকের কর্ণকুহরে পৌঁছবে না।
বলা দরকার, ‘জীবনের সমান চুমুক’ বইয়ের কবিতাগুলো যখন তিনি লিখছেন তখনো পর্যন্ত তার কবিতার ভাষাশৈলী ও রূপ-প্রকরণ সত্তরের দশকের কবিতার কৃৎকৌশল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। দেখা যায়, এই বইয়ের পরের বইগুলোতে তার কবিতার ভাষাশৈলী ও বিষয়-প্রকরণ আশির দশকীয় প্রবণতা ধারণ করেই নির্মিত হতে থাকে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয় তার প্রথম কবিতার বই ‘তিন রমণীর ক্বাসিদা’। এই বইয়ের কবিতাগুলোতে পূর্বজ অনেক কবির কবিতার ভাষাশৈলী ও আঙ্গিকের প্রভাব চোখে পড়ার মতো। এরপর প্রকাশিত হয় ‘পার্থ তোমার তীব্র বিষ’। এই বইতে এসে দেখা যায়, তিনি স্বকীয় কাব্যশৈলী তৈরি করে নিতে পেরেছেন। শব্দের বিন্যাসে শৈল্পিক যে কারুকাজ তিনি বুনেছেন তা তার নিজস্ব শিল্প-পারঙ্গমতা। এই কুশলতা যত দিন গেছে তত বেশি শৈল্পিক সৌন্দর্যে রাঙিয়ে তুলেছে তার কবিতার জগৎ। কবিতার ধরণ ও চরিত্র কী রকম হতে পারে সে বিষয়ে তিনি নিজস্ব বুঝ তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। ফলে, তার চিন্তার সাথে শব্দ-বুনন ও বিষয়-বৈচিত্যের মেলবন্ধন স্থাপনের যোগসূত্র তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, কবিতার বিষয়-প্রকরণ ও আঙ্গিকগত অঙ্গসৌষ্ঠবে তিনি আগের দশকগুলো থেকে তার দশক হয়ে পরের দশকগুলোতে সংযোগ তৈরি করেন। সেই সময় উত্তর-আধুনিকতার ঢেউ আছড়ে পড়ে বঙ্গের কবিসমাজের ওপর। সেই ঢেউয়ের বাইরে থাকেননি খোন্দকার আশরাফ হোসেন। কবিতার রূপবৈচিত্র্যে নতুন নতুন অভিনবত্ব নিয়ে আসতে তিনি ছিলেন উদার। ফলে উত্তর-আধুনিকতার ডামাডোলে তিনি তার কবিতার শরীরকে প্রচল-আঙ্গিক থেকে একটু ভিন্ন মাত্রিকে নির্মাণ করতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে ভাষাশৈলীকে তিনি বিশেষ প্রাধান্য দেন। তারকাব্যযাত্রা শুরু হয় ১৯৮৪ সাল থেকে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি নানা রকম পরীক্ষা-নীরিক্ষার ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার কবিতাকে। ইউরোপীয় মিথকে বাংলা কবিতার পাঠকের হৃদয়-ঘেঁষা প্রতিবেশী করে তুলতে আশির দশকে তার মতো সফল প্রচেষ্টা আর কোনো কবির কবিতায় আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা দেখেছি, সত্তরের দশকের গনগনে জ্বলন্ত স্লোগানমুখর কাব্যভাষার সময়টিতে যাপিত বাস্তবতার টানাপড়েন যতটা উঠে এসেছে, মিথের ব্যবহার ঠিক ততটাই হয়েছে উপেক্ষিত। এমনটি হতে পারে এ কারণে যে, সত্তরের উত্তুঙ্গ সময়ে কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষার চেয়ে সময়ের দাবি মেটাতেই হয়তো কবিদের তাড়না ছিল। আর সেই সময়ে কবিতার পাঠকও ছিল বাস্তবতার প্রতি ক্ষুব্ধ ও দ্রোহী। ফলে, প্রাত্যহিক শব্দের প্রতিবাদী পঙক্তিগুচ্ছ পাঠক সহজেই গ্রহণ করতো। আশির দশকে এসে রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা যে স্বাভাবিক হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। এরপরও এই দশকের কবিরা কবিতাকে আগের দশক থেকে নতুন কাঠামোয় নতুন বৈচিত্র্যে রূপ দিতে নিরন্তর পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালান। সকল কবিই যে এই দলে ছিলেন, তা কিন্তু নয়। যারা ছিলেন, পরবর্তী দশকগুলোতে এসে কবিতার পাঠক আগ্রহ নিয়েই তাদের কবিতা পাঠ করেন। আশির দশকের গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে তাদেরকে স্বীকৃতি দেন। খোন্দকার আশরাফ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়াতেন। ফলে, ইউরোপীয় মিথ খুব ভালো রকম তার আত্মস্থ ছিল। সেই মিথকে তিনি বাংলার জনসংস্কৃতির আবহে তার কবিতায় পুনর্জীবিত করেন। কেবল তা-ই নয়, তৎসম ও দেশি শব্দের পাশাপাশি আরবি-ফারসি ও ইংরেজি শব্দের মিথষ্ক্রিয়ায় তার কবিতা আশির দশকের আরসব কবি থেকে তাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। এসবের মধ্যদিয়েই তিনি তৈরি করে নেন তার কবিতার শিল্পভাষ্য রূপ। বাক্য-বিন্যাসেও তার স্বকীয়তার স্বাক্ষর পষ্ট। ‘হোরেশিওর প্রতি হ্যামলেট’ কবিতায় তিনি লিখছেন:
বিদায় বন্ধু। মৃত্যুর তীর থেকে জীবনের সুস্থির প্রতিভূ
তোমাকে বিদায়। তরঙ্গসঙ্কুল অই সমুদ্রের নীল ঊর্মিমালা
ডাকছে আমাকে। তার শীলত আঁচল দ্যাখো প্রসারিত হয়
জননীর স্নেহাকুল বাহুর মতোন। ওফেলিয়া
দিগন্তের চৌকাঠে সাজিয়েছে ফুলতোলা বিবাহ বাসর!
আমি যাই। তুমি থাকো; জীবনের দুর্বিষহ ভার
বাষ্পাকুল পৃথিবীর শ্বাসরোধী চন্দ্রাতপ-তলে
বয়ে যাও আরও কিছু দিন।
দার্শনিকতা উৎসারিত জীবনোপলব্ধি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতাকে বিশেষভাকে পাঠযোগ্য করেছে। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য তার প্রথমদিককার কবিতায় যতটা চোখে পড়ে, পরের দিককার কবিতায় তেমনভাবে আসেনি। পরের দিকে তার কবিতা সামাজিক রীতিরনীতির প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। এছাড়া বাংলার এতিহ্য অনুসন্ধানে তার মেধাবী দৃষ্টি পড়ে কবিতার বিষয় হিসেবে। সামাজিক কাঠামোয় সম্মিলিত মানুষের বসবাস হলেও প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র অন্তর্জগতের বাসিন্দা। সেই অর্থে সকল মানুষের ভেতরই কমবেশি দার্শনিক উপলব্ধি রয়েছে। খোন্দকার আশরাফ এই সত্য শিল্পের স্মারকে উৎকীর্ণ সত্য হিসেবেই জানতেন। অনেক শিল্পবোধা বলেন যে, কবি মাত্রেই দার্শনিক। কেননা, শৈল্পিক সুষমা ধারণ করার পাশাপাশি শিল্পোৎত্তীর্ণ কবিতায় থাকে কবির অন্তর্বোধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপলব্ধি। কবি হলেও সে তো আসলে মানুষই। মানুষের ভেতরই তার জীবনযাপন। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অভিঘাত এসে আরসব মানুষের মতো কবিকেও উদ্বেলিত করে। ভাবনার নানা ভাঁজ তুলে তার জীবন অভিজ্ঞতাকে ঋদ্ধ করে। ফলে, কবিতার ভেতর অনিবার্যভাবেই আছড়ে পড়ে সেসব অভিজ্ঞতার তরঙ্গ। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের অনেক কবিতায় আমরা দেখি, সমাজের কদর্য রূপ। মানুষের প্রকৃত মুক্তির রক্তরাঙা সূর্যকে তিনি বারবার আহ্বান করেছেন নানা উপমায় ও রূপকের ঘেরাটোপে। কবি লিখছেন:
জীবনের প্রান্ত ঘিরে বেড়ে ওঠা পুঁই-ডালিমের লতার মতো
সোমত্ত নদীর মতো নারীদের মতো কথকতা
তপ্ত ললাট ঘিরে শুশ্রূষার হাত ছেড়ে আমাদের মাতা ও ভগ্নিরা
সব দলবেঁধে বাণিজ্যমেলায় যাচ্ছে যাচ্ছে সব বাণিজ্যমেলায় যাচ্ছে।
(ট্রেড ফেয়ার)
বাণিজ্যের সওদায় হেঁটে চলা মোহমুগ্ধ এইসব সুগন্ধী মা ও বোনের দল আসলে পুঁজির দাস। বৃহত্তর গণমানুষের জীবনপ্রবাহের সাথে তাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। চকচকে মেকাপে তাদের বাইরের খোলস ধবধবে উজ্জ্বল। অথচ ভেতরটা স্বার্থান্ধ। বস্তুত, তাদের জীবনধারাও কৃত্রিম, মেকি। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের ভেতর মানবতার শাশ্বত রূপ চিত্রিত ছিল বলেই তিনি এসব নারীদের প্রতি তীব্র শ্লেষ ছুড়ে দিয়েছেন।
এই পাশাপাশি আমরা দেখি যে, তার কবিতার অনুষঙ্গ হিসেবে সবুজ-শ্যামল গ্রাম, ফুল ও ফসলের প্রাচুর্য সত্যিকারের বাংলার রূপকে ধারণ করে। আশির দশকের অনেক কবির কবিতাতে বাংলার রূপকে সেইভাবে আমরা পাই না। কিন্তু খোন্দকার আশরাফ বাংলা কবিতার ঐতিহ্য ধারণ করেই কবিসত্তাকে উপলব্ধি করেন। যদিও তিনি ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের পণ্ডিত, এরপরও তিনি যে জসীম উদদীন ও বন্দে আলী মিঞার কাব্য-উত্তরসূরী সেই সত্য এতটুকু ভোলেননি। ঐতিহ্য সংরক্তি ও গৌরবের সাথে তার আত্মিক সংযোগ ছিল প্রগাঢ়। নিরীক্ষার আতিশয্যে তিনি কবিতাকে গিনিপিগ করে তোলেননি। বরং নীরিক্ষার ভেতর দিয়ে কবিতাকে শিল্পের নানা মাত্রিকে অভিনবত্ব দিয়েছেন। তাই তার কবিতা নিরীক্ষার অভিনবত্বে হয়ে ওঠে শাশ্বত বাংলার চিত্রকল্প।



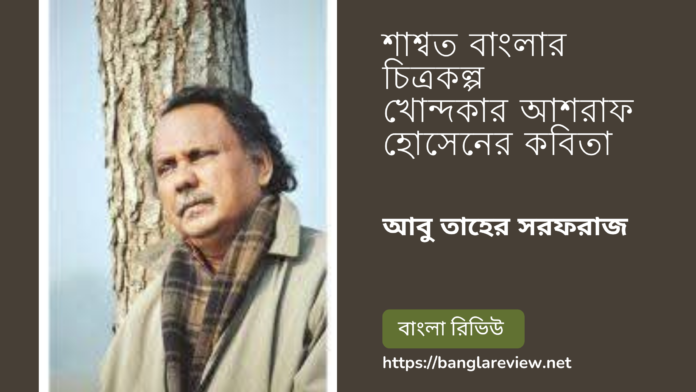
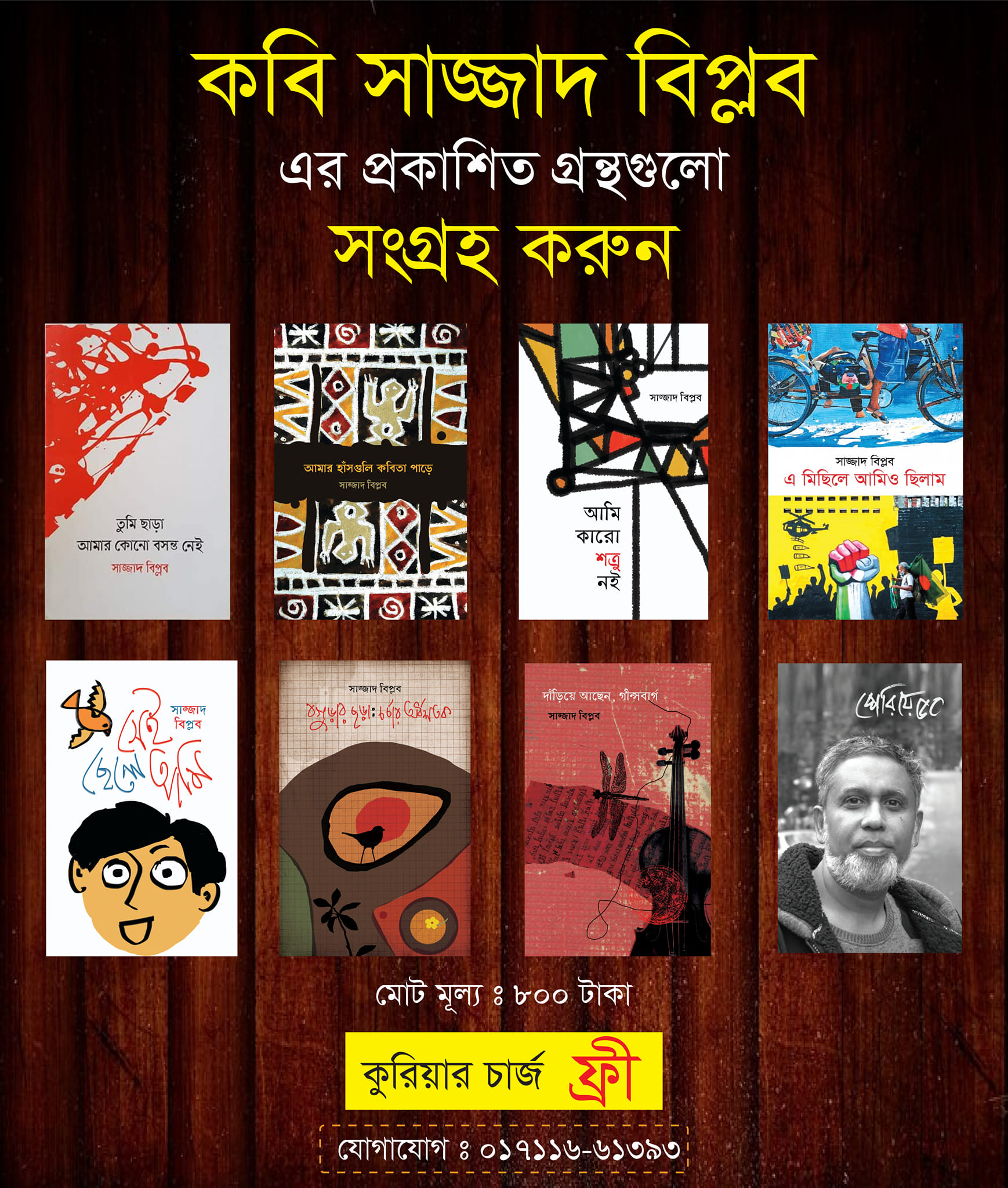
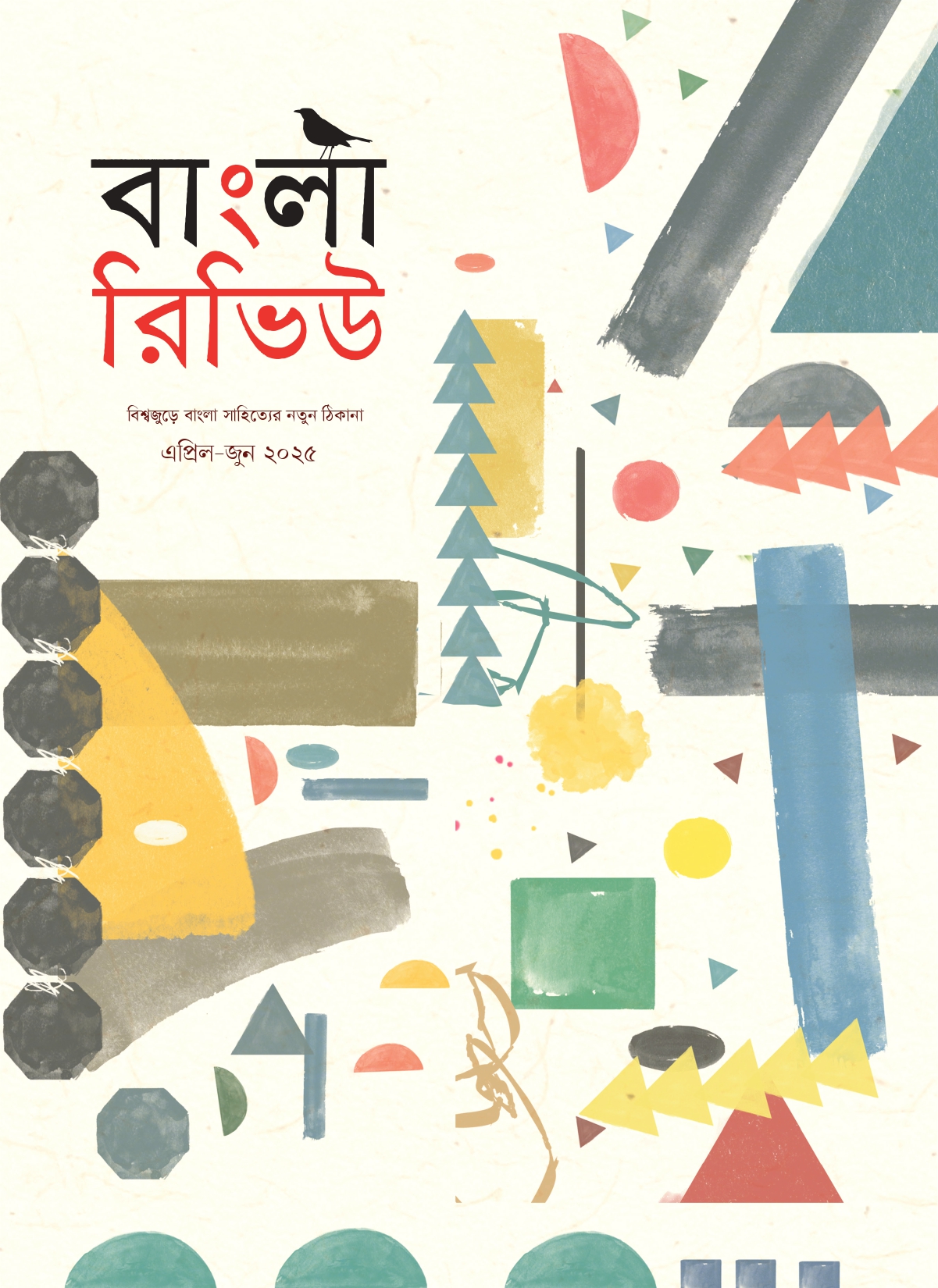


সুন্দর আলোচনা।