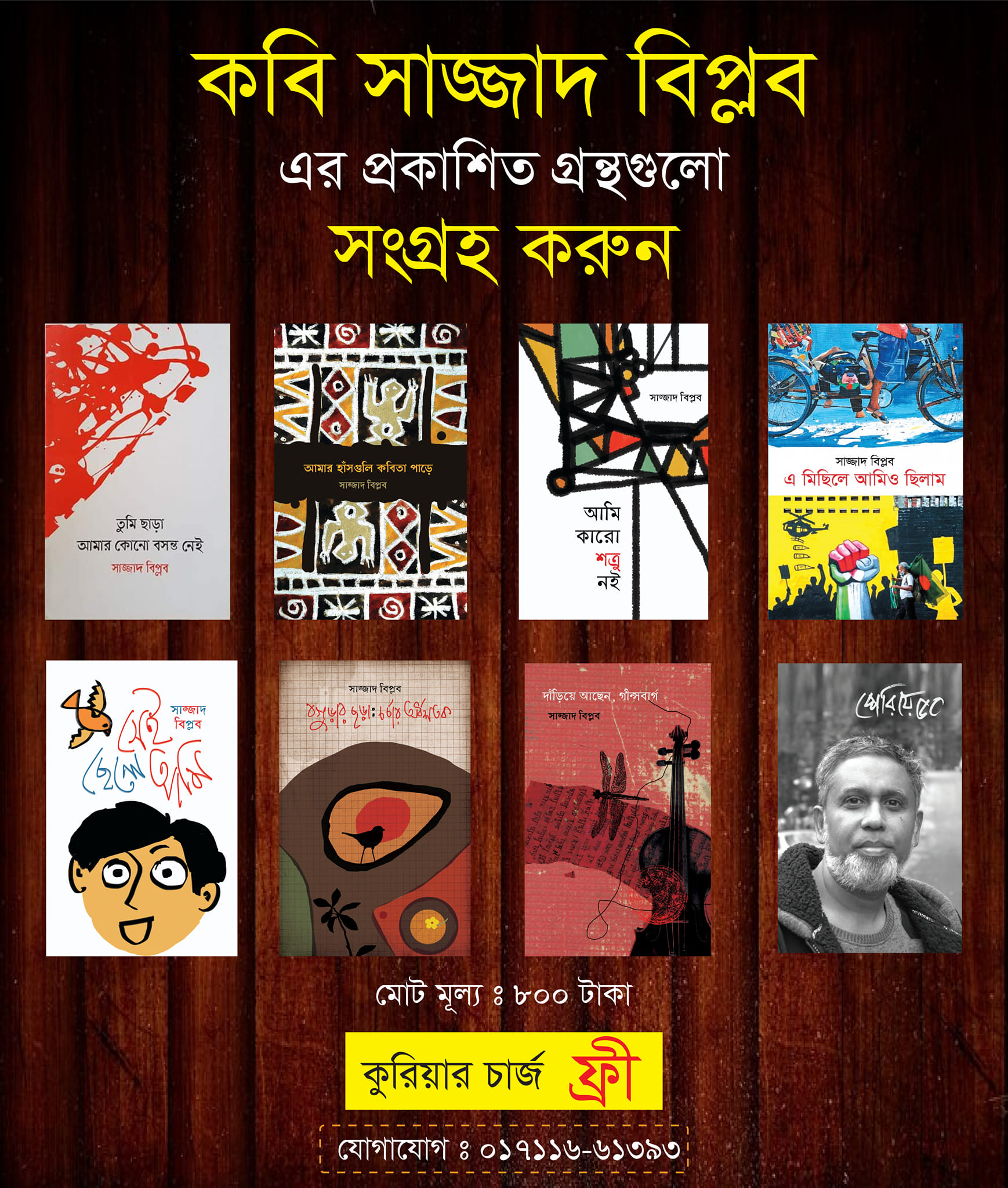কাজী জহিরুল ইসলাম
দুই সপ্তাহ আগে বর্ষিয়ান সঙ্গীতজ্ঞ মুত্তালিব বিশ্বাস আমাকে ফোন করেন। মুত্তালিব ভাই ফোন দিলেই আমি এর কারণ বুঝে যাই। তিনি ৮৩ অতিক্রম করেছেন, কাছাকাছি বয়সের শিল্প সাহিত্যাঙ্গনের কারো কথা মনে পড়লেই আমাকে ফোন দেন, তাঁদের শারীরীক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। আমি অবশ্য ফোন ধরেই বলি, মুত্তালিব ভাই কেমন আছেন? তিনি এর উত্তরে হেসে দেন। হেসে দিয়েই বলেন, আমি তো ভালোই আছি, ওমর সাহেব কেমন আছেন সেটা জানতেই ফোন করলাম। ওমর সাহেব মানে মহিউদ্দিন ওমর, এক সময় অভিনয় করতেন, এখন নিউ ইয়র্কে থাকেন। তিনিও আশি ছুঁই ছুঁই, প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুত্তালিব ভাই ৮৩ বছরের এক তুর্কি তরুণ। এখনও মঞ্চে দাঁড়িয়ে চার ঘণ্টা গান করতে পারেন। শুধু এক দেড় ঘণ্টা পরে তাঁর একটি সিগারেট ব্রেক লাগে, ব্যাস, আবার গাইতে শুরু করেন। শুধু যে গান করেন তা-ই না, প্রতিটি গানের ইতিহাস নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন। কোন গান কে লিখেছেন, কবে এটি প্রথম গাওয়া হয়, কোন স্টুডিওতে রেকর্ড করা হয় ইত্যাদি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি তাঁর সঙ্গীত বয়ান। অনেকেই হয়ত জানেন না এই মুত্তালিব বিশ্বাসই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপিটি তৈরী করেন। সেদিন ফোন করে জানতে চাইছিলেন ড. আশরাফ সিদ্দিকীর কথা। আজকাল তাঁর কোনো খোঁজ খবর পাই না। কেউ তাঁকে নিয়ে কিছু লেখেনও না, আপনি কিছু জানেন? আমি জানি তিনি কি জানতে চাইছেন। আমি বলি, যত দূর জানি তিনি বেঁচে আছেন। তবে কতটা সুস্থ আছেন এই খবর জানি না। খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাবো।
এক সময় আশরাফ সিদ্দিকীর সাথে আমার নিবিড় সখ্য ছিল। মুত্তালিব ভাই ফোন করার পর আমি কবি মাহবুব হাসানকে ফোন করি। গত রোববারের (৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৮) ঘরোয়া রেস্টুরেন্টের আড্ডায় মাহবুব ভাইকে আবারও জিজ্ঞেস করি, এবং এই প্রসঙ্গে আশরাফ সিদ্দিকীর কর্মকান্ড নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আলাপও করি। ১৯২৭ সালের ১ মার্চ টাঙ্গাইলে তাঁর জন্ম, মাহবুব ভাইয়ের বাড়িও টাঙ্গাইল, সেই সূত্রে লক্ষ করলাম কিছুটা বাড়তি টান রয়েছে তাঁর আশরাফ সিদ্দিকীর প্রতি। কিছুটা আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে, তাও জানালেন।
দেশ বিভাগের পর এক দরিদ্র শিক্ষক তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে আত্মহত্যা করেন। ঘটনাটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখন। এতে আশরাফ সিদ্দিকী খুবই মর্মাহত হন এবং সেই বৃদ্ধ শিক্ষককে নিয়ে লিখে ফেলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘তালেব মাস্টার’। ১৯৫০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বের হয় ‘তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা’। এর পরে যদিও তাঁর আরো বেশ কিছু কবিতার বই বের হয়েছে কিন্তু মানুষের হৃদয়ে আশরাফ সিদ্দিকী তালেব মাস্টার হয়েই বেঁচে আছেন। তালেব মাস্টার থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দিই।
যুদ্ধ থেমে গেছে । আমরা তো এখন স্বাধীন ।
কিন্তু তালেব মাস্টারের তবু ফিরল না তো দিন !
স্ত্রী ছয় মাস অসুস্থা
আমারও সময় হয়ে এসেছে : এই তো শরীরের অবস্থা !
পাঁচ মাস হয়ে গেছে : শিক্ষা বোর্ডের বিল নাই ।
হয়ত এ-বারের টাকা আসতে আসতে শেষ হবে আয়ু তাই
শতচ্ছিন্ন জামাটা কাঁধে ফেলে এখনো পাঠশালায় যাই
ক্ষীণ কন্ঠে পড়াই:
‘হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে…’
মনে মনে বলি :
যদি ফোটে একদিন আমার এইসব সূর্যমুখীর কলি!
ইতিহাস সবই লিখে রেখেছে । রাখবে —
কিন্তু এই তালেব মাস্টারের কথা কি লেখা থাকবে?
আমি যেন সেই হতভাগ্য বাতিওয়ালা
আলো দিয়ে বেড়াই পথে পথে কিন্তু
নিজের জীবনই অন্ধকারমালা ।মানিকবাবু! অনেক বই পড়েছি আপনার
পদ্মানদীর মাঝির ব্যথায় আমিও কেঁদেছি বহুবার
খোদার কাছে মুনাজাত করি : তিনি আপনাকে
দীর্ঘজীবী করুনআমার অনুরোধ: আপনি আরও একটা বই লিখুন
আপনার সমস্ত দরদ দিয়ে তাকে তুলে ধরুন
আর আমাকেই তার নায়ক করুণ !
কোথাও রোমান্স নেই! খাঁটি করুণ বাস্তবতা –
এবং এই বাংলাদেশের কথা।
আশির দশকের শেষের দিকে এবং নব্বুয়ের দশকের গোড়ার দিকে ঢাকা শহরে আমি এবং আমার খালাত ভাই কাজী কনক প্রচুর অনুষ্ঠান করতাম। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ছিল আমাদের নিয়মিত মঞ্চ। প্রায় সব অনুষ্ঠানেই আমাদের অবধারিত অতিথি থাকতেন আশরাফ সিদ্দিকী। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমাদের একটি নিবিড় সখ্য গড়ে ওঠে। তিনি মঞ্চে উঠে বেশ হাস্যরস তৈরী করতেন, দর্শকদের হাসাতেন। তাঁর এই গুণটি আমার খুব ভালো লাগত। একদিন তাঁর সঙ্গে মঞ্চে লেখিকা রাবেয়া খাতুনও আছেন। তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছেন রাবেয়া খাতুনের দিকে। রাবেয়া খাতুন কি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন? আশরাফ সিদ্দিকী দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো করে বলে উঠলেন, ‘রাবেয়া, হায় রাবেয়া’। এই বলার মধ্যে কিছুটা ব্যর্থ প্রেমের আহাজারি ছিল বলেই হয়ত দর্শক নড়ে-চড়ে বসলেন, কেউ কেউ হেসেও উঠলেন। তিনি মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলেন, ‘কিছু হলে হতেও পারত। যৌবনে রাবেয়া বেশ সুন্দরী ছিলেন।’রাবেয়া খাতুন তখন নিজের অস্বস্তি কাটাতেই একটি হাসির আভাস তোলেন মুখশ্রীতে। এরপর শুরু করেন ঢাকাইয়া জোকস। এক লোক জুতো কিনতে এসেছে। জুতোর দাম বারো টাকা, ক্রেতা দামাদামি করছে, ছয় টাকায় দেবেন? বিক্রেতা বলে, হ, দিমু। ক্রেতা বাড়িতে গিয়ে প্যাকেট খুলে দেখে বাক্সের ভেতরে এক পাটি জুতো। সে দোকানে ফিরে আসে। দোকানি বলে, দুইটার দাম তো বারো টেকা, ছয় টেকায় তো একটাই পাইবেন। পাশের দোকান থেকে আরেক ঢাকাইয়া দোকানদার বলে, হালায় বহুত বদ। কিছু মনে কৈরেন না ভাইজান। এক কাম করেন, হুগনা গু চিবায়া ওর মুখে থুক দেন।
আশরাফ সিদ্দিকী মুলত লোকবিজ্ঞানী। লোকজ সাহিত্য নিয়ে তিনি প্রচুর কাজ করেছেন। তিনি কবি জসীম উদদীনের ছাত্র ছিলেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সাথেও ছিল তাঁর সুসম্পর্ক, সেই সুবাদে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে কিছু কাজও তিনি করেন। তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সংগ্রহ করেছেন লোকজ সাহিত্য। আমাদের পল্লী সঙ্গীতের যে শতাধিক উপশাখা আছে এটা আশরাফ সিদ্দিকীই খুঁজে খুঁজে বের করেন। প্রায় সাড়ে তিনশর মত কবিতা লিখলেও ‘তালেব মাস্টার’ ছাড়া তাঁর অন্য কোনো কবিতা তেমন তরঙ্গ তুলতে পারেনি। বরং তাঁর গল্প ‘গলির ধারের ছেলেটি’ অবলম্বনে নির্মিত সুভাস দত্তের চলচ্চিত্র ‘ডুমুরের ফুল’ তাঁকে অনেক বেশি পরিচিতি এনে দেয়। ছবিটি অনেকগুলো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।
বাড্ডায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর নাম আবদুল বাকী। আবদুল বাকীর বাড়ি শেরপুরের ভায়াডাঙ্গায়। তাঁর খুব ইচ্ছে আমরা তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাই, ভায়াডাঙ্গা স্কুলের মাঠে কবিতা পড়ি। তিনি সব আয়োজন করে ফেলেছেন। দুটি মাইক্রোবাস ভাড়া করেছেন। ১৯ নভেম্বর ১৯৯৯, শুক্রবার ভোরে আমরা যাত্রা করলাম ভায়াডাঙ্গার উদ্দেশে। যেহেতু লোকজ সাহিত্যের প্রতিই ড. আশরাফ সিদ্দিকীর আগ্রহ বেশি ছিল। ঢাকার বাইরে যাবার কোনো নিমন্ত্রণ হাতছাড়া করতেন না। সেই সফরে তিনি সানন্দে আমাদের সঙ্গী হন। একসঙ্গে ভ্রমণ এবং রাত্রিযাপন তাঁকে আরো নিবিড়ভাবে চিনতে সাহায্য করে। এই সময়েই তিনি আমাকে নাতি ডাকতে শুরু করেন। আমিও তাঁকে নানা ডাকতে লাগলাম। এর আগে অবশ্য তাঁকে আমি স্যার বলতাম। যেতে যেতে গাড়িতে তিনি একটার পর একটা জোকস বলে আমাদের হাসিয়েছেন। ভায়াডাঙ্গার অনুষ্ঠানে তিনিই প্রধান অতিথি। বয়সে তরুণ হলেও আমিও ছিলাম একজন বিশেষ অতিথি। নানা-নাতির নানান ঠাট্টা মশকরা গাড়ির ভেতরে চলছিল। আশরাফ সিদ্দিকী জোকস শুরু করেন, নাতি শোনো, এক লোক ঢাকাইয়া আমওয়ালার কাছে গেছে আম কিনতে। টুকরিতে সাজানো আমগুলো সে কিছুক্ষণ নেড়ে-চেড়ে দামে পোষায়নি বলে না কিনেই চলে যাচ্ছিল। বিক্রেতা তাঁকে ডেকে বলেন, ভাই কিনবেন না টিপেন কেলা, ঘরের বিবি পাইছেন নিহি? আমরা হো হো হো হো করে হাসি।
ভায়াডাঙা পৌঁছানোর পরে প্রায় কুড়িজনের দলটিকে কয়েকটি ছোটো দলে ভাগ করে বিভিন্ন বাড়ির অতিথি করা হলো। কিন্তু আশরাফ সিদ্দিকী কাউকেই কোথাও যেতে দিচ্ছেন না। রাতের খাবার সবাই একসাথে খেলাম। খেয়ে-দেয়ে শুরু হলো ম্যারাথন আড্ডা। সেই আড্ডা প্রায় ভোররাত অবধি চললো মূলত তাঁরই উৎসাহে এবং নেতৃত্বে। ভায়াডাঙ্গায় আমরা খুব সফল এবং আনন্দদায়ক একটি কবিতাভ্রমণ করি। শত বছরের পুরনো ভায়াডাঙ্গা স্কুলের মাঠে সেই রোদেলা দুপুরে দশ হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে কবিতা শুনেছে। এক তরুণ মাস দুয়েক আগে জনকণ্ঠে ছাপা হওয়া আমার একটি কবিতার পেপার কাটিং নিয়ে এসে অনুরোধ করছে এই কবিতাটি পড়ে শোনাতে। আনন্দে আমি কাঁদতে শুরু করি। আশরাফ সিদ্দিকী আমাকে কাছে টানেন, বলেন, কাইন্দো না কাইন্দো না নাতি, এইটাই হল কবিতার শক্তি।
একবার কবি জসীম উদদীন পরিষদ ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে জসীম উদদীন পুরষ্কারের জন্য মনোনীত করে। নির্বাচক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন ড. আশরাফ সিদ্দিকী। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করা হয় ড. আবুল কাশেম ফজলুল হককে। অনুষ্ঠান হবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমরা গল্প করছিলাম। তখন জানতে পারি আশরাফ সিদ্দিকীর ছাত্র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আর মনিরুজ্জামানের ছাত্র আবুল কাশেম ফজলুল হক। আবুল কাশেম ফজলুল হক কিন্তু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান। আমি কম বয়স থেকেই মানুষকে খোঁচাতাম। পরিষদের বর্ষীয়ান মহাসচিব ড. জিয়াউদ্দিনকে খোঁচা দিয়ে বলি, এতো ছোটো মানুষকে প্রধান অতিথি করলেন? কথাটা আশরাফ সিদ্দিকী শুনে ফেলেছেন। আমি তো ভয়ে মূর্ছা যাই। তিনি না আবার রাগারাগি শুরু করেন, তাহলে ড. কাশেম শুনে ফেলবেন, আমাকে বেয়াদব ভাববেন। না, তিনি রাগারাগি তো করলেনই না, জিয়াউদ্দিন সাহেবের প্রশংসা করে বললেন, বয়স দিয়ে নয়, গুণ দিয়েই মানুষকে মূল্যায়ন করতে হয়। আপনারা ঠিক কাজই করেছেন।
তাঁকে দিয়ে আমরা সেই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করিয়েছিলাম।
জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষকতা করলেও ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক পদে যোগ দেন এবং ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। এই সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি কবিতা লিখে তা বাংলা একাডেমীর মঞ্চে পাঠ করেন নির্মলেন্দু গুণ। এই অপরাধে গুণ দা’কে মহাপরিচালকের কক্ষে, মানে আশরাফ সিদ্দিকীর কক্ষে, ডেকে আনা হয়। কয়েকজন আন্ডার কভার সেনা কর্মকর্তা গুণ দা’কে জেরা করেন। তাঁর কাছে কবিতাটির কপি চান। তিনি বলেন, আমার কাছে কপি নেই। এই গল্প অন্য এক আড্ডায় গুণ দা’র কাছে শুনেছি। গুণ দা’কে নিয়ে যেদিন আড্ডার গল্প লিখবো তখন আরো বিস্তারিত বলবো।
১৯৮৯ সালে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের জীবদ্দশায় তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেছি আমরা। আশরাফ সিদ্দিকীর বয়স এখন ৯১ বছর। আমি প্রার্থনা করি তিনি যেন কমপক্ষে আর ৯টি বছর বেঁচে থাকেন। আমরা অন্তত একজন প্রকৃত লেখকের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করি।
হলিসউড, নিউ ইয়র্ক। ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৮