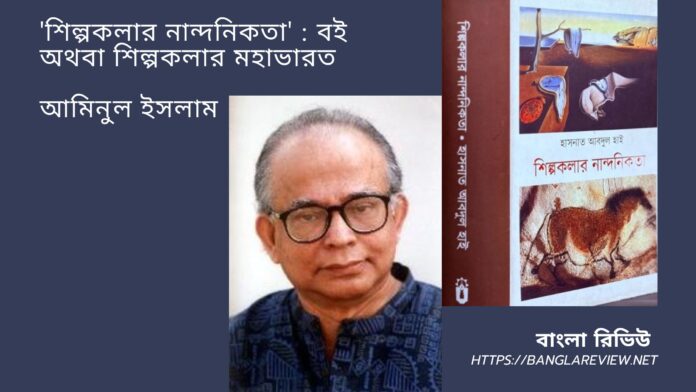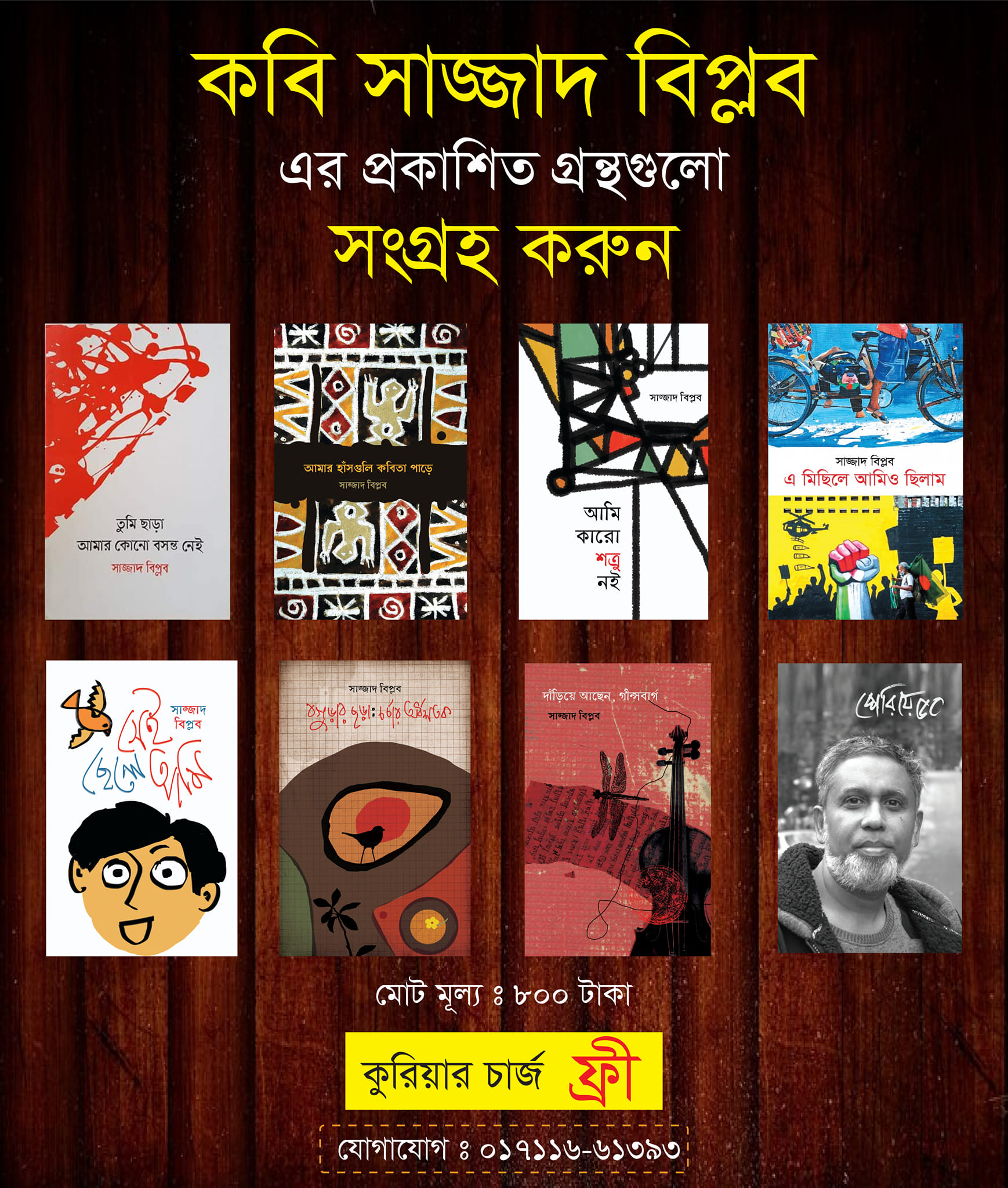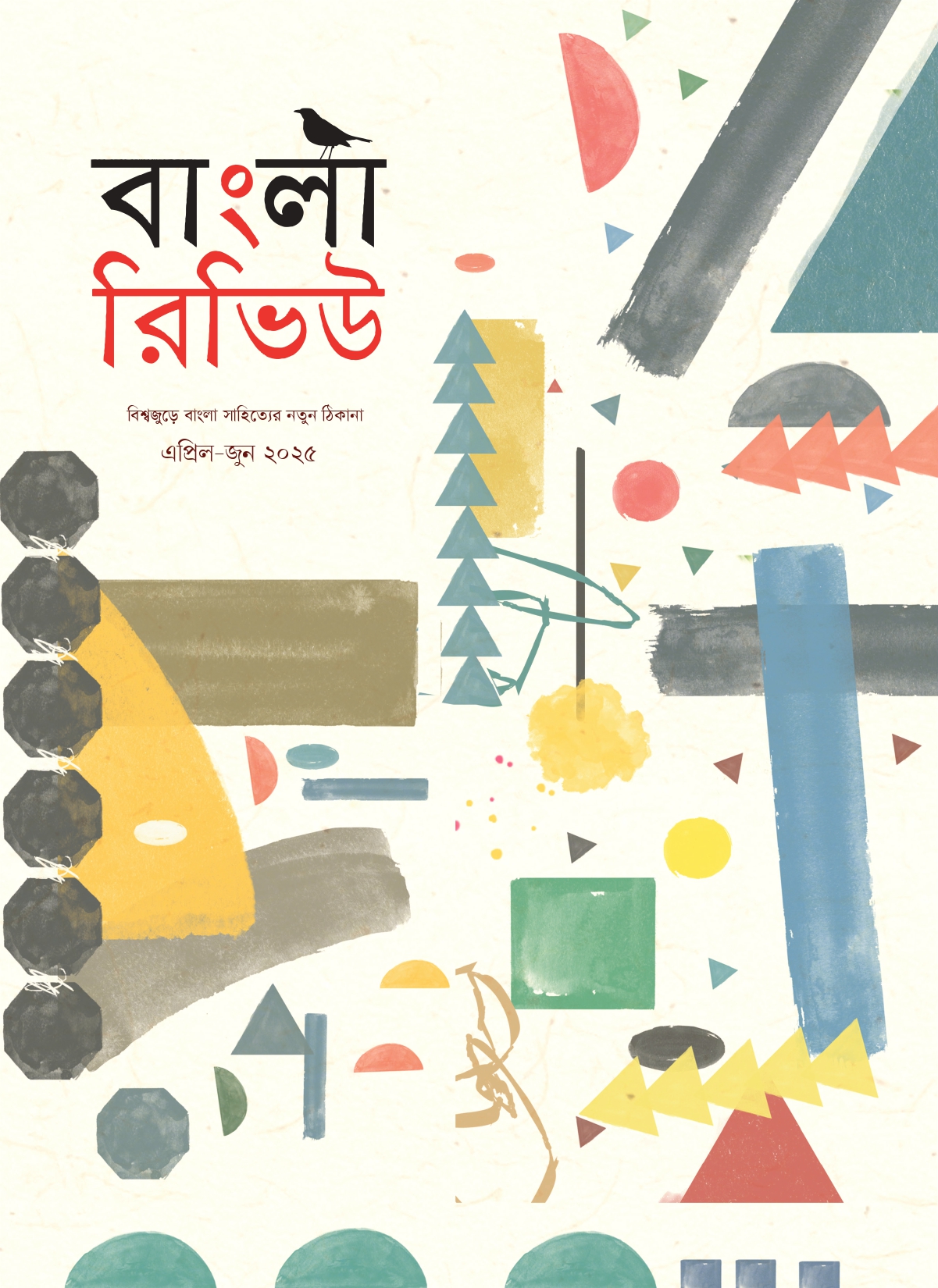আমিনুল ইসলাম
‘জানি, কবিতার চেয়ে তুমি সুন্দরতম ওগো মোর ভাবনার নায়িকা,
তুমি ইলোরা অজন্তার কারুকার্য, কোনো শিল্পীমনের তুমি চিত্রলেখা।’
গাজী মাজহারুল আনোয়ার রচিত গানের উপরে বর্ণিত বাণী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার তাঁর সুরেলা ভরাট কণ্ঠে সর্বোচ্চ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলেন; যখনই শুনি, মনপ্রাণ ভরে ওঠে অনির্বচনীয় অনিঃশেষ ভালো লাগায় কিন্তু নারীর সৌন্দর্য, ইলোরা-অজন্তার কারুকাজ এবং শিল্পীর আঁকা চিত্রের মাঝে শৈল্পিক যোগসূত্র কিংবা শিল্পের ব্যাকরণগত সাদৃশ্য কি, তা বুঝে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ ভালো লাগে। তার মানে ষোল আনা না বুঝেও অথবা বুঝা আর না বুঝার মাঝামাঝি অবস্থানে থেকেও কবিতা-ভাস্কর্য-চিত্রশিল্পের সৌন্দর্য কিংবা শিল্পরস উপভোগ করা যায়। পুরোপুরি না হলেও অন্তত কিছুটা। তবে গানের বাণীর সবচেয়ে রহস্যাবৃত অংশটি হচ্ছে ‘ কোনো শিল্পীমনের তুমি চিত্রলেখা’ চিত্রকল্পটি। শিল্পী ছবি আঁকেন রঙতুলি আর ক্যানভাস নিয়ে; ভাস্করের সঙ্গে থাকে হাতুড়ি নেহাই, পাথরখণ্ড । কিন্তু সেসবের আড়ালে থেকে পরিচালকের ভূমিকা পালন করে ‘শিল্পীর মন’। আল মাহমুদের চিরবিখ্যাত ‘সোনালি কাবিন’ কবিতাটি পড়তে পড়তে বারবার চোখ আটকে গেছে নিচে উল্লেখিত দুটি লাইনে:
‘এদেশের কলাকেন্দ্রে এদেশের সর্বকারুকাজে,
অস্তিবাদী জিরাফেরা উঠিয়েছে ব্যক্তিগত গলা।’
(সোনালি কাবিন/ আল মাহমুদ)
মন্ত্রমুগ্ধতা নিয়ে বারবার পড়েছি সোনালি কাবিন কিন্তু তার অনেককিছুই বুঝিনি ভালোমতো। শিল্পকলার প্রসঙ্গটি তো নয়ই। কারণ আর্ট বা শিল্পকলা ছিল আমার শিক্ষার ও চর্চার বাইরের জিনিস। এখনও আর্ট নিয়ে আমার কিছু করার সাধ্য নেই। কিন্তু সাহিত্য চর্চা করি; বিশেষত কবিতা। কেউ কেউ বলেন , কবিতা হচ্ছে সর্বোচ্চ আর্ট। আর কবিতা পড়তে গিয়ে, লিখতে গিয়ে জেনেছি– রোমান্টিকতা, আধুনিকতা, উত্তরাধুনিকতা, ডাডাইজম, পরাবাস্তববাদ, বিমূর্তবাদ, প্রতীকবাদ, রিয়েলিজম প্রভৃতি তত্ত্ব ও তথ্যের কথা। এগুলো এত জটিল এবং একটার সঙ্গে আরেকটা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে কোনোটাকেই শতভাগ আলাদা করে পরিস্কারভাবে বুঝে উঠতে পারিনি যেভাবে নদী বলতে নদীকেই বুঝি সহজ সরলতায় অথবা বন বলতে বনকেই বুঝি সবখানি। আবার এসব নিয়ে প্রচুর মতভেদও বিদ্যমান। শিল্পসমালোচক ও সাহিত্যসমালোচকগণ নিজেরাই যেখানে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেন না, সেখানে আমার মতোন একজন নগণ্য মানুষ সেসব বুঝবে কীভাবে? কিন্তু কিছু কিছু কবিতা পড়ে, কিছু কিছু আঁকা ছবি দেখে ভালো লাগে, একধরনের মুগ্ধতা বা বিস্ময় জন্মায় । জয়নুলের গুন টানা নৌকার ছবি অথবা সুলতানের পেশীবহুল কিষাণি-কিষাণীদের দেখলে সেসবের ব্যাকরণ না বুঝেও ভালো লাগে, একধরনের আনন্দ পাই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নির্মিত ভাস্কর্য দেখে এক অনির্বচনীয় আনন্দ পাই । কিন্তু সেসব কেন ভালো লাগে, তার শৈল্পিক ব্যাখ্যা চাইলে আমি তা দিতে পারবো না । সমুদ্র দেখে, আকাশ দেখে, বনভূমি দেখে, তালগাছে ঝুলে থাকা বাবুই পাখির বাসা দেখে, এমনকি মাঠে রাখালের গোরু-ছাগলের পাল দেখে ভালো লাগে আমার। খুব ভালো লাগে। কিন্তু কেন ভালো লাগে, তার একাডেমিক ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার।
প্রখ্যাত কথাশিল্পী-শিল্পবোদ্ধা হাসনাত আবদুল হাইয়ের ‘শিল্পকলার নান্দনিকতা’ নামক ভয়াবহভাবে বিশাল আকৃতির বইখানা ‘পাঠক সমাবেশ’-এ চোখে পড়ার খেয়ালবশত কিনেছিলাম। একদিন ভয়ার্ত মন নিয়ে পড়া শুরু করি। কিন্তু এগুতে পারি না। এত তথ্য, এত তত্ত্ব, এত ইতিহাস, ঘটনার এত ঘনঘটা! নবাবের হাজার দুয়ারী ঘরের মতো! পড়া শেষ হয় না। বুঝা শেষ হয় না। একটার সাথে আরেকটা এমনভাবে জড়িয়ে যে আলাদা করা যায় না। অনভ্যস্ত চোখের কাছে হাজার দুয়ারীর প্রতিটি দুয়ার একই রকম; শিল্পীদের প্রতিটি শিল্পকর্ম অ-শিল্পীর চোখে সমানভাবে ব্যাখ্যার অযোগ্য সাদৃশ্যে মোড়ানো। এমন আনাড়ি চোখ, এমন বাইরের মন নিয়েই ‘শিল্পকলার নান্দনিকতা’ বইটি পড়া শুরু করেছিরাম এবং কোনো কোনো অংশ বারবার পড়েছি।
শিল্পকলার নান্দনিকতা বইটি সুনির্দিষ্ট শিরোনামে মোট ১১টি অধ্যায়ে সাজানো। তার সাথে আছে গ্রন্থপঞ্জি এবং নির্ঘণ্ট। অধ্যায়গুলোর অধিকাংশই অনেকগুলো উপ-শিরোনামে বিভক্ত। বইটি না পড়েও কেউ যদি বইটির সূচিপত্রটি একবার দেখেন, তিনি পরিস্কার ধারণ লাভ করবেন যে এটি শিল্পকলা বিষয়ে তার অতীত ও বর্তমান, আদি অবস্থা ও বিবর্তন ইত্যাদিসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতির মহাগ্রন্থ। শিল্পকলার প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর অথবা উত্তরের নির্দেশনা রয়েছে বইটিতে। যারা বইটি পড়েননি বা দেখেননি অথবা যাদের পড়া হবে না ,তাদের জন্য এখানে সূচিপত্রটি তুলে ধরছি।
প্রথম অধ্যায়: শিল্পকলার নান্দনিকতা;
দ্বিতীয় অধ্যায়: শিল্পকলা :
প্রাগৈতিহাসিক যুগ;
তৃতীয় অধ্যায় : শিল্পকলা :
প্রাচীন সভ্যতা; প্রাচীন মিশর, মেসোপোটেমিয়া, সিন্ধুনদ উপত্যকা সভ্যতা, প্রাচীন চীন সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা এবং রোমক সভ্যতা;
চতুর্থ অধ্যায় : মধ্যযুগ
রোমানেস্ক শিল্প, গথিক;
পঞ্চম অধ্যায়: শিল্পকলা : রেনেসাঁ
ইতালির উত্তরাঞ্চলের দেশে রেনেসাঁ, ইতালির হাই রেনেসাঁ শিল্প, ভেনিসের রেনেসাঁ শিল্পিরা, উত্তর ইতালির রেনেসাঁ, উত্তর ইউরোপের হাই রেনেসাঁ, ইতালিয়ান ম্যানারিজম, ইতালির বাইরে ম্যানারিজম , হাই রেনেসাঁ ভাস্কর্য ও ম্যানারিজম ;
ষষ্ঠ অধ্যায় : ব্যারোক, রোকোকো ও নিউ ক্লাসিসিজম:
ব্যারোক, ইতালির ব্যারোক শিল্প, ফ্লেমিশ এবং স্প্যানিশ ব্যারোক, স্পেনের ব্যারোক ,নেদারল্যান্ডসের ব্যারোক শিল্প, ফরাসি ব্যারোক, রোকেকো, ফরাসি রোকোকো, ফ্রান্সের বাইরে রোকোকো, নিও-ক্লাসিসিজম;
সপ্তম অধ্যায়: শিল্পকলা: রোমান্টিসিজম:
প্রি-রাফেলাইট
অষ্টম অধ্যায়: শিল্পকলা: মডার্নিজম:
রিয়েলিজম , ইমপ্রেসনিজম, সিম্বলিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ফভিজম, কিউবিজম, অর্ফিক কিউবিজম, ফিউচারিজম, বিমূর্তশিল্প, ডাডাইজম, বাউহাউস, আর্ট ডেকো, স্যুররিয়ালিজম, বিমূর্ত প্রকাশবাদ, কংক্রিট আর্ট, অর্গানিক অ্যাবস্ট্রাকশন, এক্সজিসটেনশিয়াল আর্ট, আর্ট ইনফর্মাল, কোবরা, নিও-ডাডা, সাম্প্রতিক বিমূত শিল্প;
নবম অধ্যায়: শিল্পকলা: পোস্ট-মডার্নিজম
পপ আর্ট, অপ আর্ট, পারফর্মেন্স আর্ট, ফাঙ্ক আর্ট, বিট আর্ট, কাইনেটিক আর্ট, নুভোঁ রিয়েলিজম, ফ্লাক্সাস, মিনিমালিস্ট আর্ট, কনসেপচুয়াল আর্ট, ইনস্টলেশন আর্ট, আর্ট প্রভেরা, ফটোরিয়ালিজম/সুপার রিয়েলিজম, নিউ ফিগারেটিভ, ভিডিও আর্ট, ফটোগ্রাফি এবং আর্ট, আর্থ আর্ট, সাইট ওয়ার্কস, নিও-পপ, নিও-এক্সপ্রেশনিজম;
দশম অধ্যায়: শিল্পকলা: পোস্ট-মর্ডানিজম
ডিজিটাল আর্ট, প্রযুক্তিভিত্তিক আর্টের ইতিহাস, ডিজিটাল আর্টের সৃষ্টি, সরবরাহ এবং সংরক্ষণ, উপায় বা পন্থা হিসাবে ডিজিটাল মাধ্যম, ডিজিটাল ইমেজিং: ফটোগ্রাফ এবং প্রিন্ট, ভাস্কর্য, মিডিয়াম হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি, ইনস্টলেশন, ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক আর্ট, সফটওয়্যার আর্ট, ভার্চুয়াল নিয়েলিটি (রিয়েলিটি) আর্ট;
একাদশ অধ্যায়: শেষের কথা;
গ্রন্থসূচি;
নির্ঘণ্ট;
আমার মতো সাধারণ শিক্ষিতদের কাছে শিল্পকলা একটি জটিল, নীরস এবং বোধগম্যতার প্রায় বাইরের একটি বিষয়। এমন কঠিন, আনকমন এবং পাঠকবিহীন বিষয নিয়ে এমন বৃহৎ কলেবরের বই লেখার পেছনে উদ্দেশ্য কি? প্রয়োজন কোথায়? এই বই কবি-সাহিত্যিক-শিল্পজনদের কী উপকারে আসবে? আমি নিজেও একজন শিল্প-নিরক্ষর ব্যক্তি। কিন্তু বইটি পড়ার পর এখন আর নিজেকে পুরোপুরি শিল্প-নিরক্ষর মনে হয় না। বইটিতে লেখক শিল্পকলার শুরু থেকে বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেছেন সবিস্তারে। ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অন্যদের ব্যাখ্যা ও মতামত তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত শিল্পীদের তাদের সৃষ্টিসহ উপস্থাপন করেছেন। তাদের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ রঙিন ছবি সংযুক্ত করেছেন। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে আমার কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, লেখক হাসনাত আবদুল হাইয়ের নিজস্ব শিল্পভাবনা, ব্যাখ্যা ও অভিমত। তিনি বইয়ের ভূমিকায়, প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সংযুক্ত ‘সারসংক্ষেপ’-এ এবং পরিশেষের ‘শেষের কথা’ অধ্যায়ে আপন শিল্পভাবনা ও অভিমত উপস্থাপন করেছেন। লেখকের সকল অভিমতের সঙ্গে শিল্পকলার পণ্ডিতগণ সহমত হবেন এমনটা লেখক নিজেও মনে করেন না। তবে নিজস্ব অভিমতসমূহের মাঝে লেখক হাসনাত আবদুল হাইয়ের শিল্পপ্রীতি, শিল্পবোধ ও শিল্পজ্ঞানের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে , সেসবের প্রতি বিস্ময়মাখা শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হওয়ার কথা। তিনি শিল্পকলার ছাত্র ছিলেন না, শিল্পকলার অধ্যাপকও নন। তিনি মূলত সাহিত্যিক, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে কথাসাহিত্যিক। কিন্তু কলেজ জীবনের থেকে শুরু তাঁর শিল্পপ্রীতি তাঁকে একজন স্বশিক্ষিত সুশিক্ষিত শিল্পবোদ্ধায় পরিণত করেছে। তিনি বিবরণের ভাঁজে ভাঁজে নিজের অভিমতের হীরক টুকরো গুঁজে দিয়েছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে একটি করে ‘সারসংক্ষেপ’ সংযোজন করেছেন যা মহামূল্যবান। হাজারো তথ্যে ও ইজমের উদাহরণে ভরা এক একটি বিশালাকৃতির অধ্যায় পড়তে পড়তে যখন পাঠকের জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ এর সেই “হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা “-সমান অবস্থা হবে,, তখনই সংযোজিত সারসংক্ষেপ ” সবুজ দ্বীপ ” হয়ে পতাকা ওড়াবে । এটি চৌকস শিল্পবোদ্ধা হাসনাত আবদুল হাইয়ের লেখক হিসেবে অনুপম দূরদর্শিতার সোনালি স্বাক্ষর। তিনি বিভিন্ন অধায়ের অভ্যন্তরেও প্রয়োজন মাফিক বর্ণনা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ শিল্পকলার ভুবনে মডার্নিজম এবং পোস্ট মডার্নিজম নিয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন তার অংশবিশেষ পাঠকের জন্য উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করছে:
(১) ” শিল্প-সাহিত্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মডার্নিজম শব্দটির ব্যবহার বেশ পুরনো হলেও এর অর্থ নিয়ে মাঝে-মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এর কারণ মডার্নিজমের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সংস্কৃতির এই সব কর্মকান্ডে (শিল্প ও সাহিত্য) এক নয় এবং যেসব পরিবর্তন ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মডার্নিজমকে বিশেষ সময়কালে (শুরু ও শেষ) চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি এক ও অভিন্ন নয়। সাহিত্যে মডার্নিজম চিহ্নিত হয়েছে ১৯০০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত। কেউ কেউ এর শেষ সময়সীমা ১৯৫০ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। মোটামুটি ঐকমত্য দেখা যায় সংগীতের ক্ষেত্রে যেখানে এর সূচনা হয়েছে আর্নল্ড শোয়েনবার্গ এবং অ্যালবান বার্গের স্বরবৈচিত্র্যহীনতার সংগীত (এটোনাল) ও ইগর স্ট্রাভিনিস্কির সামঞ্জস্যহীন সংগীত কাঠামো প্রচলনের পর থেকে। স্থাপত্যে মডার্নিজমের যাত্রা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, স্থপতি ল্যু কুর্বশিয়ের, মিয়েস ভ্যান ডার রোহে এবং ওয়াল্টার গ্রোপ্রিয়াসের ফাংশনাল স্থাপত্যের প্রচলন থেকে। অনেকেই মনে করেন, শিল্পকলায় মডার্নিজমের যাত্রা শুরু হয় ইমপ্রেসনিস্টদের আন্দোলনের সময় থেকে, ১৮৬৪ সালে তাঁদের ছবির প্রথম প্রদর্শনীর মাধ্যমে। শিল্পকলায় মডার্নিজমের শুরু নিয়ে এই লেখায় ভিন্নমত পোষণ করা হয়েছে।
হার্বাট রিড শৈলীর ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনকেই মডার্নিজমের সংজ্ঞায় কেন্দ্রীয় স্থান দিয়েছেন। পল ক্লির মতো তিনিও বলেছেন, মডার্ন আর্টের উদ্দেশ্য যা বাস্তবে দৃশ্যমান তার হুবহু প্রতিফলন নয়, বরং দৃশ্যমানকে দৃশ্যমান করা (মেক ভিজিবল ভিজিবল)। শেষোক্ত মন্তব্যে শিল্প স্বায়ত্তশাসিত (অটোনোমাস), প্রথমটি অনুযায়ী শিল্প বাস্তবের দৃশ্যের ওপর নির্ভরশীল। এর পর রিড বলেছেন, ‘শিল্পের ইতিহাস হলো দৃশ্য সম্বন্ধে শিল্পীর ধারণার বিবর্তন। তিনি আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, ‘শিল্পে আধুনিক আন্দোলন বলতে যা বুঝি তার সূত্রপাত হয়েছে একজন ফরাসি শিল্পী বাহ্যিক বাস্তবকে বস্তুগতভাবে কীভাবে দেখেছেন সেই একাগ্র সংকল্প থেকে। এ নিয়ে কোনো রহস্যময়তা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশের অবকাশ নেই।” (পৃষ্ঠা নং ২৫৬-২৫৭)
(২) “ষাটের দশক থেকে ‘পোস্ট-মর্ডানিজম’ কথাটির ওপর বেশ কয়েকটি পরতের অর্থ সংযোজিত হয়েছে যার জন্য কেউ কেউ এই পর্বকে সুদৃঢ় সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ করার বিপক্ষে মত রেখেছেন। যেমন, আন্দ্রিয়াস হুইসেন তাঁর ‘আফটার দ্য গ্রেট ডিভাইড’ (১৯৮৬) বইতে জোর দিয়ে বলেছেন, শিল্পের ক্ষেত্রে পোস্ট-মর্ডানিজমের সূচনা হয়েছে পপ আর্ট থেকে। পপ আর্টের জনপ্রিয়তার পেছনে তিনি শনাক্ত করেছেন ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা, প্রগতিশীল রাজনীতির পক্ষে জনমত সৃষ্টি, শিল্পকর্ম তৈরির জন্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন (যেমন, সিল্কস্ক্রিনে ছবি ছাপানো), ক্ষুদ্র আকারের গ্যালারিতে ছবি প্রদর্শনের সুযোগ, শিল্পকে একই সঙ্গে সমকালীন ভোক্তাকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রকাশ এবং তার সমালোচনা হিসেবে দেখা, গজদন্ত মিনার থেকে শিল্পকে উদ্ধার করে সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপন, ফ্যান্টাসি এবং স্বতঃস্ফূর্ততার স্বীকৃতি, উজ্জ্বল রঙের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গ হওয়া, বস্তু এবং ইমেজের প্রতিফলনের মাধ্যমে বাস্তবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, বুর্জোয়া সমাজের হাই আর্টকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসা, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ততা, এসথেটিক এবং নন-এসথেটিকের মধ্যবর্তী পার্থক্য ঘুচিয়ে বাস্তব ও শিল্পকে অভিন্ন করে তোলা, অসুন্দরসহ সুন্দরের সহাবস্থানে আস্থাজ্ঞাপন, এই সব ঘটনা বা কারণকে। এই সব প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং রীতি-পদ্ধতি পোস্ট মর্ডানের সজ্ঞা পরে।” (পৃষ্ঠা নং-৪৩৩)
দা ভিঞ্চি, বতেচিল্লি, পাবলো পিকাসো, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, কারাভাজ্জিও, উইলিয়াম ব্লেক, ভ্যান গঁগ, মার্ক শাগাল, পল সেজাঁ, পল গগাঁ, ভাসিলি কান্দিনিস্কি, সালভাদর দালি,কিলমেন্ট গ্রিনবার্গ, জ্যাকসন পোলক, রামকিঙ্কর, জয়নুল আবেদীন, এসএম সুলতান, মকবুল ফিদা হুসেন — আমার কাছে শুকতারা, সন্ধ্যাতারা, স্বাতি, জোহরা, তিনতারা, আদমসুরুত, অরুন্ধতী প্রভৃতির মতো অধরা চিরবিস্ময়মাখা নাম। আমি এদের বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলো বিভিন্ন বইয়ে এবং কিছু চিত্রগ্যালারিতে দেখেছি নানাসময়ে। কিন্তু এসবকে শিল্পের ব্যাকরণ মিলিয়ে দেখার ও বুঝার মতো যোগ্যতা আমার ছিল না। এখনও নেই। কিন্তু হাসনাত আবুদল হাইয়ের ‘শিল্পকলার নান্দনিকতা’’ বইটি পড়ে অন্তত এটুক বুঝতে পেরেছি, কেন তাঁরা এত এত খ্যাতিমান। নিঃসন্দেহে এই বইটি শিল্পকলার ছাত্র-শিক্ষকদের উপযোগী করে উচ্চমার্গীয় বৈশিষ্ট্যে ও ব্যঞ্জনায় রচিত। কিন্তু আমার মতো অবোধ শিল্পপ্রেমিকদেরও শিল্পপ্রেম বৃদ্ধিতে বইটির পাঠ সহায়ক হবে বলে মনে হয়েছে। বইটিতে বিখ্যাত শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবন ও শিল্পজীবন নিয়েও ছোটখাট আলোকপাত করা হয়েছে। সেগুলো খুব সংক্সিফ্ত হলেও শিল্পীকে বুঝার জন্য সফলভাবে সহায়ক।
তিনি ভ্যান গঁগের শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর যাপিত জীবনের ওপরও আলোকপাত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, মাত্র ৩৭ বছর জীবন যাপনকারী ভ্যান গঁগ তাঁর ৭ বছরের আঁকাআঁকির জীবনে কীভাবে শিল্পকর্মে নিজস্ব চিন্তা, শাররিক অসুস্থতা, উত্তেজিত ভাবনা ও চঞ্চল মানসিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ফলে তাঁর শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে ‘শিল্পীমনের চিত্রলেখা’। আরেক বিখ্যাত আধুনিক শিল্পীর নাম পল গগাঁ। পল গগাঁর শিল্পভাবনা, শিল্পসাধনা ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর ইতিহাস অনন্যতায় সমৃদ্ধ। সেসব যেমন আকর্ষণীয় তেমনি ভাবনা উদ্রেককারী। পল গগাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে হাসনাত আবদুল হাই লিখেছেন, ”…এক বছর পর গঁগা তাহিতি থেকে ছবিসহ প্যারিসে এসে সেসব দেখানোর পর বন্ধুসহ অনেকে হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়ে। ছবিগুলি অতিশয় বর্বরোচিত এবং আদিম বলে মনে হয়েছে তাদের কাছে । এতে গঁগা অবাক হননি, তিনি তা-ই চেয়েছিলেন। সেই জন্য তাঁকে ‘বর্বর শিল্পী’ বলায় তিনি খুশিই হন। তাহিতির নর-নারী যাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, সেই সব মানুষের প্রকৃতি সংলগ্ন সরল ও নিষ্পাপ জীবন প্রতিফলনের জন্য রং এবং ডিজাইনও হতে হবে আদিম শিল্পের সমতুল্য, তিনি একথার ওপর জোর দিয়েছেন। ‘ডে ড্রিমিং’ শীর্ষক ছবি দেখে অবশ্য এখন কেউ বর্বরোচিত বলবে না, কেননা এ ধরনের, বরং এর চেয়েও উদ্ভট ছবি দেখে দর্শকরা অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। গমব্রিখের ভাষায়, আমরা এখন আরো বেশি উদ্ভট শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং সেসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।’ এই তাৎক্ষণিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও শিল্পবোদ্ধাদের কেউ কেউ উপলব্ধি করেন যে, গঁগা নতুন কিছু সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু যে তাঁর ছবির বিষয় নতুন ও অদ্ভুত তাই না, তিনি আদিম সমাজের মানুষেরা যেভাবে পরিপার্শ্বকে দেখে তার অনুসরণে দেখার জন্য তাদের চেতনা ও বোধ আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। তিনি আদিম সমাজের কারুশিল্পীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং প্রায় ছবিতেই কারুশিল্পের উপাদান ব্যবহার করেছেন। পোর্ট্রেট আঁকতে গিয়ে তিনি নিজের শৈলীকে নেটিভদের শিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যময় করতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে ফর্মের আউটলাইন সহজ ও সরল হয়েছে এবং উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ততা। সেজাঁর মতো তিনি ছবিতে ফ্ল্যাট হওয়ার আশঙ্কায় সরলীকৃত ফর্ম ও রঙের অভিন্ন মাত্রা ব্যবহারে ইতস্তত করেননি। তিনি হয়তো সব ছবিতেই প্রিমিটিভ আর্টের প্রত্যক্ষতা ও সরলতা প্রকাশে সফল হননি, কিন্তু এর জন্য তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়াসের তীব্রতা সেজাঁর তুলনায় কম ছিল না। তাঁর আদর্শের জন্য তিনি তাঁর জীবন নিবেদিত করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অসহায় ও করুণ অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত দিয়েছেন । ইউরোপে প্রত্যাশিত স্বীকৃতি না পেয়ে গঁগা আবার তাহিতি ফিরে যান এবং সেখানেই নির্জন একাকিত্বে মৃত্যুবরণ করেন। গঁগার প্রথম পর্বের একটি ছবি ‘দ্য ভিশন অব দ্য সারমন জেকভ রেসলিং উইথ দি অ্যাঞ্জেল’ শীর্ষক ছবিতে ব্রেটন অঞ্চলের কৃষকদের দৃষ্টিতে দেখা অপ্রচলিত রং এবং লীলায়িত রেখা ইমপ্রেসনিস্ট ধারার দৃষ্টিভিত্তিক ন্যাচারালিজমের সঙ্গে যে পার্থক্য সূচিত করেছিল তাহিতিতে আঁকা ছবিগুলো তারই চরম পরিণতি বলে ধরা যায়। দৃশ্যমান পৃথিবীর প্রতি শিল্পীর বিশ্বস্ততা প্রত্যাখ্যান করে গঁগা শিল্পে বাস্তবের প্রতিফলনের রীতি ত্যাগ করেন। তাঁর ছবিতে প্রথমে দেখা দেয় বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলন যেমন: প্রকৃতির দৃশ্য, শিল্পীর দেখা বাস্তব, বাস্তবের দর্শনে শিল্পীর মনের প্রতিক্রিয়া ও ‘স্বপ্ন’ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ফর্ম ও রঙের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন, তাহিতি পর্বে গিয়ে সেই সবের স্থানে ক্রমে দেখা দেয় আদিম শিল্পের সরলতা ও প্রাঞ্জলতা। মনে হয়, যে লক্ষ্যে তিনি পৌঁছাতে চেয়েছিলেন গঁগা শেষ পর্যন্ত তা অর্জন করতে পেরেছেন। তাহিতিতে আঁকা গঁগার ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘বেদিং তাহিতিয়ানস’, ‘গার্ল উইথ ফ্রুট ডিশ’, ‘লেজেন্ট’, ‘তাহেতিয়ান উইমেন’, ‘ডিলাইটফুল ডে’ এবং ‘হোয়ার ডু উই কাম ফ্রম’,‘ইয়ুথ বিটুইন টু গার্লস’ এবং ‘হোয়াট উই আর ডুইং’। শেষোক্ত ছবিতে গগাঁ তাহিতির আদিম সমাজের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্যে এঁকেছেন সংক্ষিপ্ত আকারে যা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি বলে বিবেচিত।’’
(পৃষ্ঠা নং ৩১৪-৩১৫ )
বইটির বিষয় শিল্পকলার বিভিন্ন মতবাদ বা ইজম সম্পর্কে নিবিড় আলোকপাত ও আলোচনা। প্রাচীন যুগের শিল্প, রোমান্টিক শিল্প, মডার্ন শিল্প, পোস্ট-মডার্ন শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বইটিতে উদাহরণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও অভিমত আছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন শিল্পীর কাজের তুলনা , পার্থক্য ও সাদৃশ্য এবং একধরনের শিল্পের মাঝে আরেক ধরনের শিল্পের অনুপ্রবেশ বা ওভারল্যাপিং ইত্যাদি বিষয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ আছে। কোথায় রোমান্টিসিজমের শেষ আর মর্ডানিজমের শুরু , দুই ইজমের মধ্যে পার্থক্য রেখা টানা যায় কীভাবে , মর্ডানিজম এবং পোস্ট-মর্ডানিজমের মধ্যে পার্থক্য, সাদৃশ্য, সম্পর্ক, শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মকে চিহ্নিতকরণ, শ্রেণিকরণ এবং সময়ের স্কেলে মেপে তাদের ব্যবধান ও ওভারল্যাপিংয়ের অবস্থা ও মাত্রা নির্ণয় ও নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় এত সুচারু রূপে ও এত বেশি সংখ্যক উদাহরণ সহযোগে সম্পন্ন করা হয়েছে যে সেসব পড়ে সেগুলোকে শিল্পকর্মের উচ্চতর শ্রেণির পাঠ্য-রচনা মনে হয়। বলা চলে, শিল্পকলার শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জন্য এই বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
‘ শিল্পকলার নান্দনিকতা’ মহাগ্রন্থটির আরেকটি খুবই গরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে রোমান্টিজম, মডার্নিজম, পোস্ট-মডার্নিজম প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মতবাদ যেমন কিউবিজম, স্যুররিয়ালিজম, এক্সপ্রেসনিজম, বিমূর্ত শিল্প, ডাডাইজম, মতবাদ ইত্যাদির সাথে শিল্পকর্মের পাশাপাশি সাহিত্যের বিবর্তনের সম্পর্ক বিষয়ে প্রয়োজন মাফিক আলোকপাত। বিশেষত কবিদের জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো মতবাদ কবিসাহিত্যিকদের হাতে সূচিত হয়ে শিল্পকলার ভুবনে প্রবেশ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি কবিতা ও শিল্পকর্ম উভয় ভুবনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। যেমন উইলয়াম ব্লেক, শার্ল বোদলেয়ার । আমরা জেনে নতুন করে মুগ্ধ হই যে, শার্ল বোদলেয়ার কবিতা এবং আর্ট উভয় ক্ষেত্রেই মডার্নিজমের অন্যতম পুরোধা প্রতিভা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। রোমান্টিসিজমের ক্ষেত্রে উইলয়াম ব্লেকের অবদান প্রায় অনুরূপ। স্যুররিয়ালিজম, বিমূর্ত চিত্র, প্রতীকবাদ, পোস্ট-মডার্নিজম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পকলার জগতে যে ছবি দেখা যায়, সাহিত্য বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে সেসবের অনুসরণ ও প্রয়োগকে মিলিয়ে নেয়া যেতে পারে। সেসব থেকে আহরিত জ্ঞান কবিতা রচনাকালেও কাজে লাগানো যায়।
শিল্পকলার মতো প্রায় অপঠিত এবং পাঠক-বিরল বিষয়ে ডাইনোসোর আকৃতির এমন একটি গ্রন্থ রচনার পেছনে হাসনাত আবদুল হাইয়ের মতো মহাভিজ্ঞ সাহিত্যিক-শিল্পবোদ্ধার উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি নিজেই একজন সৃজনশীল সাহিত্যিক। সৃজনশীলতার সময় কাটছাঁট করে তিনি কেন এত বড় একটি কাজ হাতে নিয়েছিলেন? বইটির প্রথম অধ্যায়েই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেসব অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো চিরকালীন মূল ধারা আছে কি না, তার উত্তর খোঁজার ভাবনা থেকে বইটি রচিত হয়েছে। হাসনাত আবদুল বলেছেন, ‘‘ শিল্প-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ও সময়কালে বাস্তবের প্রতিফলন অথবা আবেগ ও আইডিয়ার প্রকাশ শিল্পকর্মে কতটুকু হয়েছে, কেমন করে হয়েছে, সেই বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণই এই বইটি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। এর অর্থ হলো শিল্পের ইতিহাসকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে, ইতিহাসের নিছক পালাবদল হিসেবে নয় অথবা ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে বিবেচনা করেও নয়। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প-ইতিহাসকে এর আগে কেউ দেখেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। এমন প্রশ্ন নিয়ে শিল্প-ইতিহাসকে দেখার মধ্যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে বলেই আমার ধারণা, কেননা এর মাধ্যমে শিল্পের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা ও সেই প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করা সম্ভব। যেমন, শিল্পে মূল ধারা বলে কিছু আছে কি না, থাকা উচিৎ কি না এবং তা কি হতে পারে বা, হওয়া উচিৎ— এই সব প্রশ্নের অবতারণা ও তার উত্তর খোঁজা। ‘’( পৃষ্ঠা নং ২১)
হাসনাত আবদুল হাই তাঁর প্রশ্নে জাগা উল্লিখিত প্রশ্নে উত্তর খুঁজেছেন বইটির মধ্যে এবং একটা সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। বইটির ” শেষের কথা ” শিরোনামের উপসংহারমূলক অধ্যায়ে সেই অনুসন্ধানলব্ধ অভিজ্ঞানের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগ থেকে আজতক শিল্পকলার ব্যাপক বিবর্তন ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিনি ইতিহাস ঘেটে তথ্য প্রমাণকসহ দেখিয়েছেন যে, বাস্তবের প্রতিফলনই হচ্ছে শিল্পকলার আদি ও মূল ধারা। শতভাগ বিমূর্ত শিল্প ছাড়া অবশিষ্ট সকল শিল্পকর্মই বাস্তবের প্রতিফলন — কোথাও বেশি, কোথাও কম; কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও বা পরোক্ষ বা প্রতীকী। মানুষ বাস্তবে বাঁচে। বাস্তবকে অস্বীকার করলে মানুষ হয়ে ওঠে উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ। এ ধরনের মানুষের সংখ্যা খুবই কম— বলা যায় বিরলপ্রায় এবং তাদের আয়ু স্বল্প। শিল্পসাহিত্যে আদিকালে একভাবে বাস্তবের প্রতিফলন হতো; রোমান্টিক কালে আরেকভাবে; এবং মডার্নিজম কালে আরেকটু পরিবর্তন ঘটেছিল। পোস্ট-মডার্ন বা পপ আর্টে ভিন্নতা এসেছে আরেকভাবে। কিন্তু যে শিল্পে বাস্তবতার স্পর্শ নেই, তা বেশিদিন টিকেনি; ভবিষ্যতেও টিকবে না। লেখক শিল্পকলার সাম্প্রতিকতম ধারাকে চিহ্নিত করেছেন যে ধারাটির নাম তার কথায় ” মিশ্র প্রকাশবাদী”। এই ধারার বিমূর্ততার সঙ্গে বাস্তবতার মোটিফ মিশে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। লেখকের মতে, এই ধারায় পেইন্টিং থেকে শুরু করে ভাস্কর্য, ইন্সটলেশন, মিক্সমিডিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পকর্ম ন্যাচারালিজমের স্থানে অর্ধবিমৃত এবং প্রকাশবাদের শ্রেণিতে মিশ্র প্রকাশবাদী হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি এই গ্রন্থে শিল্পকলার উদ্দেশ্য ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক দিকগুলোও উপস্থাপন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন সমান গুরুত্ব দিয়ে। লেখকের বই থেকে আবারও উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। “মূলধারা নিয়ে আলোচনা নান্দনিকতার বিচারে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, উপসংহারে এই কথা বলতেই হয়। নান্দনিকতার বিচারে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শিল্পকলার চর্চায় তার উদ্দেশ্য ও ভূমিকা মনে রাখা হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে প্রধান দুটির মধ্যে কোনটি ( বাস্তবের প্রতিফলন অথবা আবেগ/অনুভূতির প্রকাশ) । উদ্দেশ্য ও ভূমিকা শনাক্ত করার পর প্রশ্ন করা হবে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও ভূমিকা কেন এবং কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে? এই দুটি প্রশ্নই শিল্পকলার নান্দনিকতার বিচারে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ। ” (পৃষ্ঠা নং ৫২৩)
আসলে এই দুটি প্রশ্ন দ্বারা শুধু শিল্পকলাই নয়, সাহিত্যের যেকোনো (কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক) কাজের নান্দনিক বা শৈল্পিক মান নির্ণয় ও নির্ধারণ করা যায় এবং হয়। রুমির ‘মসনবী’, খৈয়ামের ‘রুবাইয়াত’, শেক্সপিয়রের ‘হ্যামলেট’, বোদলেয়ারের ‘ফ্লর দ্য মল’, কাজী নজরুল ইসলামের ‘ বিদ্রোহী ‘, টিএস এলিয়টের ‘দি ওয়েস্ট ল্যান্ড’, জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ‘ পদ্মানদীর মাঝি ‘ কিংবা হাসনাত আবদুল হাইয়ের ‘ সুলতান ‘ কিংবা আল মাহমুদের ‘সোনালি কাবিন’ এর বিচার বিশ্লেষণ এই সূত্র অনুসরণপূর্বক করা হয়েছে। এখন সাহিত্য ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে কথাবার্তা শোনা যায় যে কবিতার বা ছোটগল্পের কোনো বিষয় থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আসলে এটা একটি হ্রস্বদৃষ্টিজনিত ভ্রম। অর্থহীন কবিতার বা ছোটগল্পের আয়ু হুজুগ ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায়। আমরা যদি প্রতিবছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের বিষয়ে নোবেল কমিটির মতামত দেখি, সেখানেও তারা সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের বিষয়ভাবনার গুরুত্ব ও প্রকাশশৈলীর বিষয়গুলো একইসঙ্গে গভীর বিচেনায় নিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বিষয় ও আঙ্গিকের মণিকাঞ্চন যোগই একটি সাহিত্যকর্মকে সোনালি ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করে। শিল্পকলায় সেটাই হচ্ছে বাস্তরের প্রতিফলন এবং নির্মাণ কৌশল।
শিল্পকলার নান্দনিকতা বিষয়ে রচিত একটি মহাগ্রন্থের ওপর কিছু লেখা আমার মতো অ-শিল্পজনের জন্য ভয়ংকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। বহুমুখী হীনমন্যতা, ঈর্ষাকাতরতা, পরশ্রীকাতরতা কবলিত বঙ্গদেশে দুটি মারাত্মক প্রকৃতির প্রবাদবাক্য আছে : (১) ‘মোগল পাঠান হদ্দ হলো ফার্সি পড়ে তাঁতি।’ এবং (২) ‘অল্পবিদ্যা ভয়ংকর’। সেই ঝুঁকি নিয়ে আমি বইটি পড়েছি কয়েকবার এবং এটার বিষয়ে আমার পাঠপ্রতিক্রিয়া লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আসলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র থেকে আজকের পপ আর্ট বা ডিজিটাল আর্ট সবই আলোচ্য বিষয় হয়েছে বইটিতে। তেমনি আছে সব যুগের এবং সব মতবাদের বিখ্যাত শিল্পীদের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোকপাত এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সচিত্র উদাহরণ সন্নিবেশিতকরণ। তথ্য ও তত্ত্বের ঘনঘটা এবং বিভিন্ন ইজমের আলোচনা ও পারস্পারিক তুলনা বইটিকে বেড়াহীন বিস্তার এবং মহাসাগরীয় গভীরতা দিয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি উপ-অধ্যায়, প্রতিটি অনুচ্ছেদ বিস্ময়কর তথ্য-উপাত্ত-ইজম-উদাহরণে বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ। এই বই থেকে কবি নিতে পারেন অসংখ্য মিথ, চিত্রকল্প, তুলনা, প্রতিতুলনা এবং পথের দিশা; উপন্যাসিক নিতে পারেন কাহিনির ঐতিহাসিক প্লট ; নবীন চিত্রকর্মীরা নিতে পারেন অনুসরণযোগ্য অজস্র উদাহরণ। বইটি বারবার পাঠেও নিঃশেষে পাঠ-সমাপ্তিযোগ্য নয়। আমার কাছে মনে হয়েছে, ‘শিল্পকলার নান্দনিকতা’ বইটি কথাসাহিত্যিক শিল্পসমালোচক হাসনাত আবদুল হাইয়ের হাতে রচিত শিল্পকলার মহাভারত । হাসনাত আবদুল হাই শিল্পকলার কোনো “প্রাতিষ্ঠানিক পুরোহিত’’নন; অথচ তাঁর হাতেই প্রথম রচিত হলো শিল্পকলার এই মহাভারত। অবশ্য এই মহাভারতে কিছু বানান বিভ্রাট ঘটেছে; বিশেষত ‘ণ’ এর স্থানে ‘ন’ হয়েছে। এবং তা অনেক স্থানে– অনেকবার। দু’একটি তথ্যবিভ্রাটও ঘটেছে। যেমন ৪৮৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ” কোরিয়ান শিল্পী নাম জুন ১৮৬৩ সালে তার তৈরী ‘ র্যানডম অ্যাকসেস’ শীর্ষক ইনস্টলেশনে এমন সম্ভাবনা কথা বলেছেন।’’ সঠিক তথ্য হচ্ছে, সালটি হবে ১৯৬৩। এগুলো মুদ্রণপ্রমাদ, আমি নিশ্চিত। আরেকটি বিষয়। এই মহাভারত লেখক ওল্ড টেস্টামেন্টের বাইবেলের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছেন। কোনো অনুষঙ্গই বাদ দেননি। কিন্তু আলোচনার বিভিন্ন স্তরে জাপানী ফটোশিল্পীদের প্রভাব, সিন্ধুনদ সভ্যতা, প্রাচীন চীন সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। কিন্তু রোমান্টিক-আধুনিক কোনো পর্বের আলোচনাতেই রামকিঙ্কর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়নুল আবেদীন, এসএম সুলতান, মকবুল ফিদা হুসেন প্রমুখদের শিল্পকর্মের প্রসঙ্গ আলোচনায় আনেননি কেন, তা বোধগম্য হয়নি আমার । সেসবের কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না কি? আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি ‘সুলতান’, ‘নভেরা’ ইত্যাদি উপন্যাস হাসনাত আবদুল হাইয়ের শিল্পাভিজ্ঞ হাতে রচিত এবং উপমহাদেশীয় শিল্পকলা বিষয়ে তিনি সমানভাবে ওয়াকিফহাল ও পারদর্শী।
বইয়ের শেষে সংযোজিত নির্ঘণ্ট দেখে বুঝা যায়, শিল্পকলার চর্চায় যেমন ইউরোপের অতুলনীয় প্রাধান্য রয়েছে, শিল্পকলা রচিত বইগুলোও প্রায়সবই ইউরোপীয় শিল্পবোদ্ধাদের হাতে রচিত। অল্প কিছু আছেন আমেরিকান লেখক। ভারতীয় উপমহাদেশীয় লেখকের সংখ্যা দুই বা তিন। কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপমহাদেশে পিছিয়ে নেই; কিন্তু শিল্পকলার চর্চায় ও তা নিয়ে লেখালেখিতে কেন এত পিছিয়ে?
ওসমান গণির আগামী প্রকাশনী ‘শিল্পকলার নান্দনিকতা’ নামক শিল্পকলার এই মহাগ্রন্থটি প্রকাশ করে একটি মহত কাজ করেছেন। আর এই মহাগ্রন্থ রচয়িতা হাসনাত আবদুল হাইয়ের জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট হবে না ।
—————–০০০——————
১ মার্চ ২০২২
আমিনুল ইসলাম
কবি ও প্রাবন্ধিক