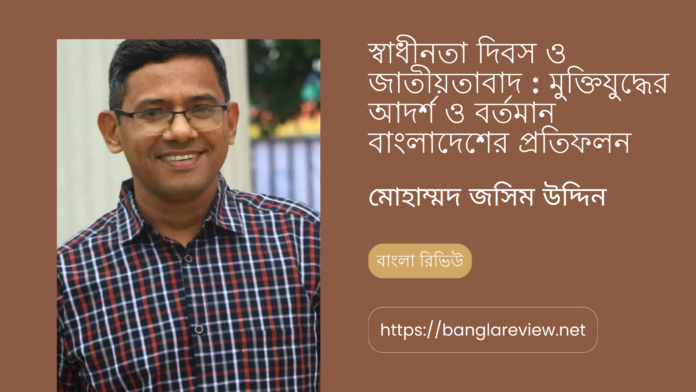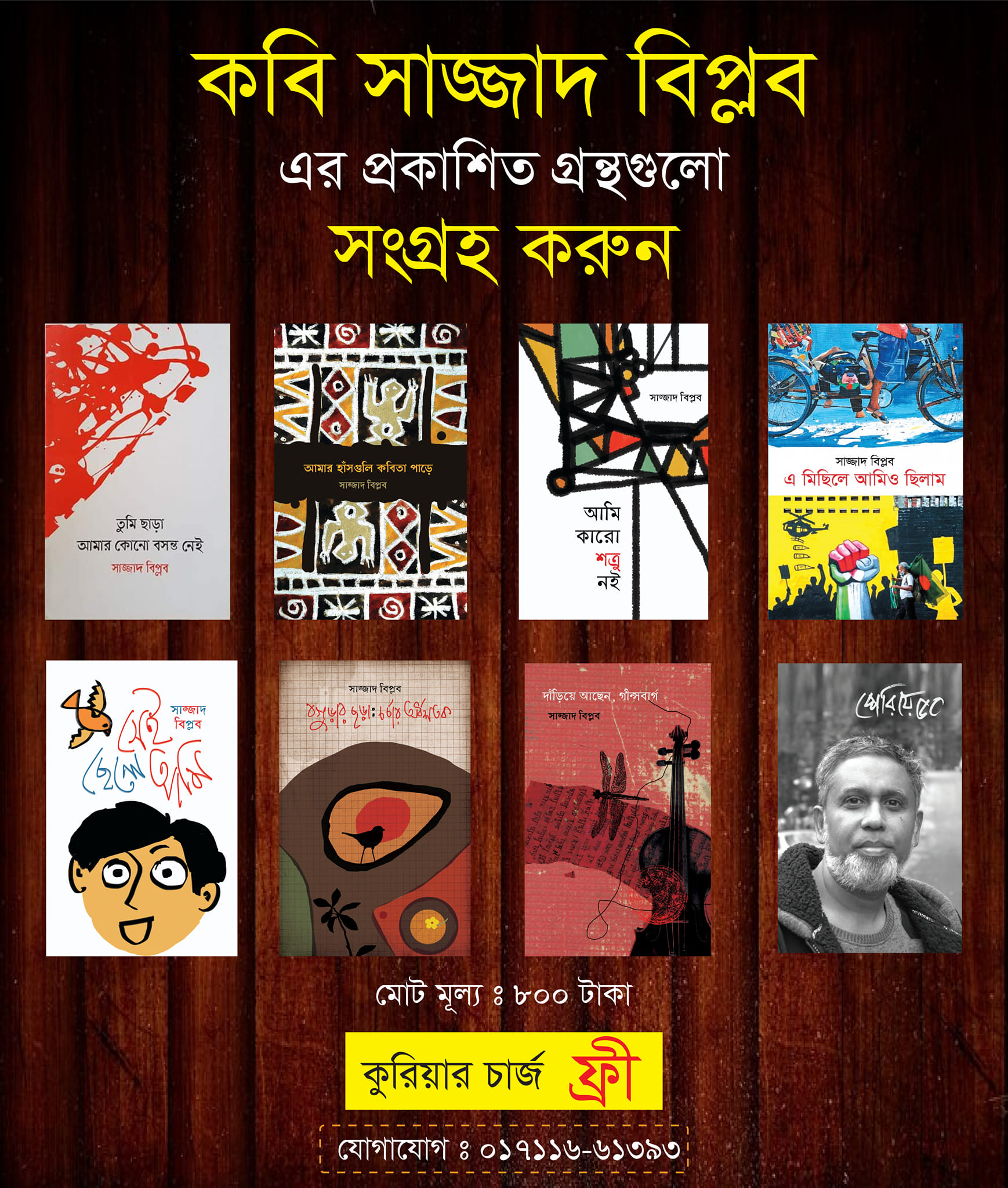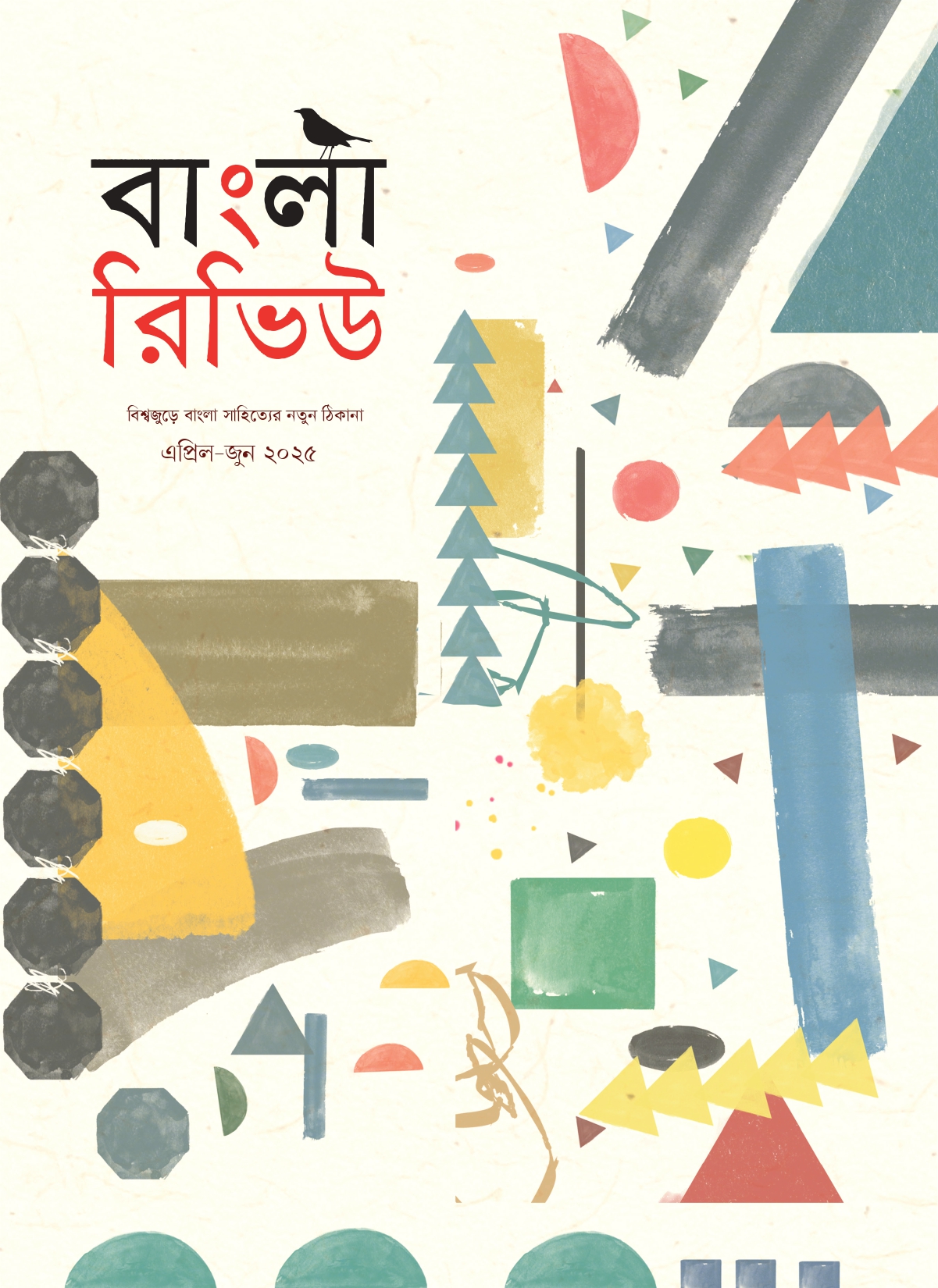মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিবস (২৬ মার্চ) শুধু একটি তারিখ নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক, একটি সংগ্রামের বিজয়গাঁথা। জাতীয়তাবাদ এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে এই আদর্শ কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োজন।
১৯৫৪ সালের মার্চের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নির্বাচন ছিল। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল, ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ আসন লাভ করে পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে ধর্মীয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে কিছু আসন সংরক্ষিত ছিল। ফলে এটি একটি স্বাধীন জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্তু ১৯৭০ সালের পূর্বে সাতচল্লিশে স্বাধীন হওয়ার পাকিস্তান রাষ্ট্রে কোনো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন হয়নি। কেননা প্রাপ্তবয়ষ্ক এবং জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনটি নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলসমূহ নিজের আদর্শিক মতপার্থক্য ভুলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে পরাভূত করে এবং এককভাবে ক্ষমতার দাবীদার হয়েছিল। পুর্ব পাকিস্তানিরা মূলত ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ’৬৬-র ছয় দফার ভিত্তিতে। অন্যদিকে, পিপলস পার্টির মূল এজেন্ড ছিল ‘শক্তিশালী কেন্দ্র, ইসলামী সমাজতন্ত্র, এবং অভ্যাহত ভারত বিরোধী’। এসবের সাথে এদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দ্বিমত না থাকলেও সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ধারাবাহিক প্রতারণা, কথা না রাখার প্রবণতা, শ্রেণি বৈষম্য তৈরি করে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রান্তিক করে রাখা, সাংস্কৃতিক, ভাষিক ও অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রভু শ্রেণিতে পারিণত করা এবং এদেশের মানুষকে আজ্ঞাবহ করে রাখায় তাদের সকল কিছু প্রত্যাখ্যান করেছে এ নির্বাচনে। এ নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে পাকাপোক্ত করে এবং বর্তা দিতে সক্ষম হয় তারা আর পশ্চিম পাকিস্তানের গোলামী করবে না।
এ বিজয়ের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং স্বাভাবিক নিয়মে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে প্রস্তুতি নিতে আহ্বান করেন। কিন্তু ১ মার্চ ১৯৭১, তিনি তা অজানা কারণে স্থগিত করেন এবং এদেশের মানুষ বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পুর্ব পাকিস্তানিদের হাতে দেশের দায়িত্ব দিতে রাজী নয়। তাই পুর্ব পাকিস্তনিরা অধিকার আদায়ে তাৎক্ষণিক নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেন।
২ মার্চ ১৯৭১ সালে আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন, যা সরাসরি পাকিস্তানি শাসন ও স্বার্ববৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের আহ্বান করে। এ পতাকা উত্তোলনে আওয়ামী লিগের প্রধান শেখ মুজিবের সায় ছিল কিনা এ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। কেননা আ স ম আব্দুর রব, শাহজান শিরাজ, সিরাজুল আলম খানসহ কোনো জাতীয় ছাত্র নেতা যারা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব দিতেন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন করার ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশ গঠনে নানা ভূমিকা রেখেছেন, কেউ এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন নি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শোনা যায় তিনি এ বিষয়টির সেদিন বিরোধীতা করেছিলেন।
উল্লেখ্য, ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ পুরো প্রদেশে শেখ মুজিব হরতাল ডেকেছিল, যেন পাকিস্তানি জান্তা সরকার এদেশের মানুষের ভাষা বুঝে। অর্থাৎ নির্বাচিত দলের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেয়।১ এটি পরিস্কার যে, শেখ মুজিবুর রহমান কোনভাবেই স্বাধীনতার পথে হাটেন নি। আর ছাত্ররা স্বাধীনতার জন্যই পতাকা উড়িয়েছেন একথাও পুরো জোর দিয়ে বলা যায় না। ছাত্ররা মূলত শেখ মুজিবকে চাপে রাখার কৌশল হিসেবেই এসব কাজ করেছেন এবং মনে কোণায় লুকিয়ে থাকা ইচ্ছাগুলোকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করছিলেন।
৩ মার্চ পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে শাহজান সিরাজ আবার পতাকা উত্তোলন করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক প্রত্যক্ষভাবে দেন। এখানেও সেই বির্তক রয়ে যায় শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত থাকার পরও কেন তিনি নিজ হাতে পতাকাটি উত্তোলন করলেন না! শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে ২৩ মার্চ ১৯৭১ সালে তার ধানমন্ডির বাসায় পতাকা উত্তোলন করেন। যদিও এক্ষেত্রে অনেক ছাত্র নেতার লেখায় পাওয়া যায় তিনি স্বইচ্ছায় নয়, বরং তাদের চাপে পড়েই এ কাজটি করেছেন। এর স্বপক্ষে একটি দলিল উপস্থান করা যায় এভাবে-৭ মার্চ ১৯৭১ সালে রেইসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটিকে ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে গণ্য করা হয়, যেখানে দশ লক্ষের উপর মানুষ এসেছিল একটি সুস্পষ্ট ঘোষণার জন্য। কিন্তু সে সভার কোথাও বাংলাদেশের পতাকা দেখা যায় নি। বরং সে ভাষণে কিছু উদ্ধৃতি নিয়ে সিরাজুল আলম খানের বক্তব্য বেশ বিতকের সৃষ্টি করেছে। ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ও এর পিছনের ইতিহাসও একটু দেখা প্রয়োজন।
ইতিহাস বিকৃতি ঘটেছে নানা সময়ে নানা হাতে। আওয়ামী লীগের হাতে ইতিহাস নির্মভাবে বিকৃত হয়েছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল। বিশেষ করে গত দুই যুগে ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাকে এমনভাবে বিকৃত করেছে এ যেন ফ্যব্রিকেটেড বা এআই দিয়ে কৃত্রিম এক ইতিহাস জাতির সামনে হারিজ করা হয়। আওয়ামী লীগের একটি বড় অংশ দাবী করছেন ৭ মার্চ ভাষণের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।
বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সিরাজুল আলম খান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম রূপকার এবং সশস্ত্র যুদ্ধের প্রধান সংগঠক।২ আওয়ামী বয়ানটি হলো, স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৭ মার্চের ভাষণটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। তবে একথা অনস্বীকার্য, এ ভাষণের সাবলীল ভাষাভঙ্গি ও মানবিক কাঠামো ছিলো অতিমাত্রায় হৃদয়স্পর্শী।৩ ফলে এ ভাষণ মানুষকে তার মর্মমূল থেকে গভীরভাবে আবেগকম্পিত, উদ্দীপিত এবং জাগ্রত করে তুলেছিলো। সে ভাষণের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহের বাণী মানুষকে সশ¯্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে তোলে। মুস্তাফা নূরুউল ইসলাম দাবী করেন, ‘৭ই মর্চকে অবলম্বন করে এসেছে মানুষের অধিকার, মুক্তি, স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দাবি ও সাধারণের স্বার্থে তাদের নিজেদের সরকার।’৪
এ ভাষণ সম্পর্কে বাংলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক প্রয়াত শামসুজ্জামান খান বলেন, ‘যে ভাষণ দিয়েছিলেন ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ এড্রেস বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিলের ভাষণসহ অন্য কোন ভাষণের সঙ্গে এ ভাষণের তুলনা চলে না। এদেশের মাটি মানুষের নিস্বর্গ প্রকৃতি এবং জীবনধারার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ ভাষণে মনে হয় যেন বঙ্গবন্ধু জীবনব্যাপী সাধনায় ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। এমনও মনে হয়, বাঙালির হাজার বছরের দুঃখ বেদনা, এবং বঞ্চনা, এবং ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে থাকার ইতিহাস। কৃষক, কৈবর্ত, উপজাতিদের বিদ্রোহ প্রভৃতির বারুদ ঠাসা উপাদানে তার সচেতন এবং অবচেতন মনে ভাষণটি তৈরি হয়ে প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়েছিল।’৫
৭ মার্চের ভাষণকে আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে দেখেন বা দাবী করেন। এটি ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার। এই ভাষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি সংক্ষিপ্ত তুলে ধরা হলো যেন ইতিহাস বিকৃতকারীদের ভবিষ্যতে রুখে দেওয়া যায়। ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে পুলিশ, বিডিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে ‘ডিফেকশন’র পরিকল্পনা করে ‘নিউক্লিয়াস’। ৭ মার্চের পর থেকে স্বাধীনতার প্রচার কর্মকাণ্ড শেখ মুজিবুর রহমানের নামেই করার পরিকল্পনা গৃহীত হলেও কোনো এক অজানা কারণে এ বিষয়ে মুজিব ছিলেন নিরব। ‘নিউক্লিয়াস’ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩ মার্চে ঘোষিত স্বাধীনতার ইশতেহারে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা আছে। ‘নিউক্লিয়াস’ (সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মনি এবং তোফায়েল আহমেদ) ও আওয়ামী লীগের হাই কমাণ্ড (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোস্তাক আহমদ এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী)-এর সঙ্গে আলোচনা করেই শেখ মুজিব ৭ মার্চের ভাষণের বিষয় চূড়ান্ত করেন। এ বিষয়টি সরলীকরণ নয়। বরং তাত্তি¡ক বিশ্লেষণ দাবী রাখে। কেননা আওয়ামী লীগ এতদিন যে দাবী করে আসছিল, শেখ মুজিব নিজেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং সভার আগে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব অভয় দিয়ে বলেছিলেন, আপনার যা মনে আসে সেটাই বলিয়েন। কিন্তু বিষয়টি হলো মুজিব অন্যদের প্রেসক্রিপশনে এ কাজটি করেছে। কেবল এখানেই শেষ নয়। এই ভাষণে তার মুখে উচ্চারিত ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ —এই অংশটি মুজিব কোনভাবেই বলতে চাননি নি। কিন্তু‘নিউক্লিয়াস’ তাকে অস্ত্র দেখিয়েছিল এবং বাধ্য করেছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যটি তারা বারবার চেপে রাখার চেষ্টা করলেও নানা বইয়ে এর প্রমাণ মেলে এবং সিরাজুল আলম খানের বইয়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেই লেখা হয়েছে।৬
আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। এ ভাষণে যদি মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন তবে তিনি ক. অবিলম্বে মার্শাল ল’ প্রত্যাহার; খ. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর; গ. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া; এবং ঘ. সেনাবাহিনীর গুলি বর্ষণ ও মানুষ হত্যার ঘটনাসমূহের তদন্ত অনুষ্ঠান৭ চাইতেন না। কারণ কারোও অভিষ্ঠ লক্ষ্য স্বাধীনতা হলে উল্লেখিত দাবীসমুহ করতে পারে না। সেসব দাবীর মধ্যে বিদ্যমান সরকারকে মেনে নিয়ে নতজানু হয়ে বিচার চাওয়ার শামিল। চব্বিশের গণ-অভ্যূত্থানে খুনি হাসিনা একের পর এক নির্বিচারে হত্যা করলে ছাত্র-জনতা খুনের বিচার তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকারের কাছে চায়নি। বরং তারা এক দফা তথা সরকারের পদত্যাগ চেয়েছিল এবং সরকার পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে সরকার হটানোর আন্দোলন করে এবং তাদের তাড়িয়ে বিচারের মুখোমুখি করেছে। অতএব, নানা বিবেচনায় ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়নি। বরং আপোষকামীতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিক সরকার, শেখ মুজিব ও ভুট্টো ধারাবাহিক বৈঠক করে যাচ্ছিল কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায় এবং ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রেখে অক্ষুণ্ণ পাকিস্তান টিকিয়ে রাখা যায়। ইতিহাস বলছে, ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টোর বৈঠক চলাকালেই ২৫ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবারো স্থগিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট ভবনের মুখপাত্রের ঘোষণায় বলা হয়, পাকিস্তানের দুই অংশের নেতাদের মধ্যে আলোচনা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতৈক্যের পরিবেশ সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য প্রেসিডেন্ট এ অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।৮ বৈঠক শেষে, বাসভবনে ফিরে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেন, বাঙালি আন্দোলনে আছে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে। তিনি জানান, ইয়াহিয়ার সঙ্গে কার নির্ধারিত বৈঠকে ভুট্টোও ছিলেন। তিনি আরও বলেন, প্রসিডেন্টের সঙ্গে পরের বৈঠক কবে হবে, তা তিনি জানেন না। তার পরের দিন বা তারও পরের দিন হতে পারে।৯ অর্থাৎ এখানেও মুজিব বৈঠকে সমাধান চেয়েছেন, যা একজন স্বাধীনতাকামী নেতার লক্ষ্য নয়।
২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিরা অর্তকিতভাবে নিরীহ বাংলাদেশিদের উপর গুলি বর্ষণ করে নির্বিচারে হত্যা করেছে। এ হত্যাকাণ্ডর কোনো সংবাদ এদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে ছিল না। ফলে প্রতিহতের প্রশ্নই আসেনি। আর এই বর্বোরোচিত আক্রমণ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের বিকৃত বয়ানটি হলো, মহান মুক্তিযুদ্ধেও সূচনা থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতি জেনে এসেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই ওয়্যারলেস এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে প্রচারিত হওয়ার পর সর্বস্তরের মানুষ প্রবল উৎসাহ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।১০
আওয়ামী লীগ দাবি করছে, শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বেই টেলিগ্রামে চট্টগামে তার ঘোষণাপত্রটি পাঠিয়ে দেন। আর সেই মোতাবেক জহুর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী ও এম আর সিদ্দিকসহ চট্টগাম শহরে যারা আছেন তারা বেতারে গিয়ে ঘোষণাটি সম্পন্ন করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এম এ হান্নান ও তার সহযোগীরা ২৬ মার্চ দুপুর ১২টায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে যান এবং সেখানে কাউকে খুঁজে পাননি। পরবর্তীতে তারা বেতারের আঞ্চলিক প্রৌকশলী মীর্জা নাসির উদ্দিনকে তার আগ্রাবাদ সরকারি কলোনি থেকে ডেকে নিয়ে যান কালুরঘাট বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রে। এরপর তিনি শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। এসব বয়ানে বেশ অসংলগ্নতা এবং মিথ্যাচারের গন্ধ পাওয়া যায়। প্রথম কথা হলো শেখ মুজিব কী গ্রেপ্তার হলেন না আগে থেকেই আত্মসর্মপনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বসেছিলেন, তা নিয়ে আছে বিপরীত তথ্য রয়েছে। কেননা, তার প্রস্তুতি ও পরিবকারের সুরক্ষার দায়িত পাকিস্তানিরা পালন করায় এ সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। পরের দিন বেতারে কেউ ছিল না, এ কথাটি ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা। এম আর আকতার মুকুল ও বেলাল মোহাম্মদের বয়ানে এটি উঠে এেেছ তারাসহ আরও অনেকেই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র সচল রেখে পাকিস্তানি আক্রমণের কথা প্রচার করে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় প্রশ্নটি আসে এম এ হান্নান যে বার্তাটি গ্রহণ হরেছিলেন মুজিবের কাছ থেকে তার কোন নমুনা আজও কেনো প্রদর্শন করা হলো না! তৃতীয় প্রশ্নটি হলো, হান্নান সাহেব যদি বেতারে ঘোষণাটি দিয়ে থাকে আ নিজ কানে শুনেছেন, এমন একজন স্বাক্ষীও কেনো পাওয়া যায়নি।
স্বাধীনতা যুদ্ধে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা অনেক। সে সময়ে মেজর জিয়া সাহসী ভূমিকা রেখেছেন পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা পাকিস্তানের পরিকল্পনা টের না পেলেও জিয়া সচেতন ছিলেন এবং প্রস্তুতি নিয়েছেন প্রতিরোধের। ২৫ মার্চ আক্রমণের পরের দিন এম আর আকতার মুকুল ও বেলার মোহাম্মদসহ আরও বেশ কয়েকজন বেতার কর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সারা বাংলাদেশের জনগণকে সচেতন করা প্রয়োজন। শেখ মুজিব যেহেতু নেই, তাই তারা কালুঘাট ব্রিজ পার হয়ে জিয়ার কাছে আহ্বান জানালে তিনি সানন্দে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে নিজের নামে এবং পরবর্তীতে বেতার কর্মীদের অনুরোধে শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার এই ঘোষণাটি হাজার হাজার মানুষ নিজ কানে শুনেছে এবং আজও তার স্বাক্ষী দিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুল আলম হানিফ একবার এক অনুষ্ঠানে দাবী করেছিলেন মেজর জিয়া আওয়ামী লীগের নেতাদের অনুরোধে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন।১১ এসব তথ্য বেশ কয়েকটি বার্তা দেয়। এক, জিয়া নিজেও স্ব-ইচ্ছায় ঘোষণাটি দেননি। দুই, বেতার কর্মীরাও কারও নির্দেশে নয়, বরং নিজ উদ্যোগেই দেশের মানুষের জন্য জিয়ার কাছে গিয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে যাননি। তিন, যে আওয়ামী লীগ সব সময় জিয়াকে পাকিস্তানের দোসর বলে আসছিল, তারাই স্বীকার করে নিল মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার ভূমিকা।
আওয়ামী লীগের নেতাদের দাবীর বিপরীতে এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা দাবি করেন, ‘বাংলাদেশের সর্বত্র পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষত বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সদস্যরা একযোগে বিদ্রোহ করেন; যদিও পরবর্তীতে এটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের আহ্বানে তারা বিদ্রোহ করে যুদ্ধে নেমেছেন এটা অসত্য। আসল ঘঘটনা হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের আক্রমণ করেছে, এবং আক্রান্ত হওয়ার পর তারা বিদ্রোহ করেছে।’১২ তারা আরও দাবি করেন, ‘প্রথমত, এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কোনো প্রকার রাজনৈতিক নির্দেশ ছাড়াই। এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন, যদি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে যুদ্ধ শুরু হতো, তাহলে এই যুদ্ধে আমরা অনেক বেশি ভালো করতে পারতাম। এর চেয়ে বড় সত্য উপলব্দি আর হতে পারে না।’১৩ তারা ছাত্র লীগের তৎকালীন এক নেতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ‘আওয়ামী লীগের কোনো প্রকার যুদ্ধপ্রস্তুতি নেই, এমনিতেই আন্দোলন চলছে।’১৪
স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধে নির্দেশনা নিয়ে শেখ মুজিবের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা হয় মঈদুল হাসান ও শেখ মুজিবের। কিন্তু মুজিব ছিলেন নির্লিপ্ত এবং কোনো ধরণের নির্দেশনা না দিয়ে মঈদুল হাসানকে পাঠিয়ে দিলেন তাজউদ্দীনের কাছে। তাজউদ্দীনের এক প্রশ্নের জবাবে মঈদুল হাসান বলনে, ‘[তাজউদ্দীন] অবশেসে জিজ্ঞাস করলেন, ‘রুজিব ভাইয়ের কথা শুনে আপনার কী মনে হলো? তিনি কেন আপনাকে [মঈদুর হাসান] আমার [তাজউদ্দীন] কাছে পাঠালেন? আমি বললাম, ‘তিনি হয়তো এ ব্যাপারে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান না। আবার খবরটা আগ্রহও করতে পারলেন না। তাই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। দায়দায়িত্ব এখন আপনার।’১৫
স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা দাবি করেন, ‘৭ মার্চের জনসভায় শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার শর্ত হিসেবে তিনটি দাবি তোলেনÑসান্ধ্য আইন তুলে নিতে হবে, সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যা ও নির্যাতনের ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। তিনি এও জানতেন যে, এদেশের মানুষ স্বাধীনতার ঘোষণা শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে জনসভায় এসেছেন।’১৬ কেবল তাই নয়, ‘পাকিস্তানি ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর শেখ মুজিবের কণ্ঠে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো স্বাধীনতার ঘোষণা না থাকায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরবর্তী পর্যায়ে [২৬ মার্চ পরবর্তী] ৭ মার্চের ঘোষণাকে প্রতিদিন কয়েকবার করে বাজানো হয়েছে।’১৭
অতএব, স্বাধীনতার ঘোষণার একক কোন ব্যক্তির কৃতিত্ব নাই। শেখ মুজিব কোনোভাবেই স্বাধীনতার ঘোষণার সাথে ছিলেন না এবং এম এ হান্নানের ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও আষাঢ়ে গল্প। জিয়াউর রহমান নিজ দায়িত্বে দিলেও নিজের পরিকল্পনায় দিয়েছেন এ কথা বলার সুযোগ খুব কম। তবে কালুরঘাট বেতার কর্মীদের ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে ভাসানী নানাভাবে স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেছেন, তবে সেটিও আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়নি। তবে প্রবাসী সরকার গঠনের মাধ্যমে বৈদ্যনাথ তলায় যে শপথ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা করেছে, তা অনস্বীকার্যভাবে বিশ্ব স্বীকৃতির পথে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ ছিল সাম্য, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে বাহাত্তরের সংবিধানে, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ অর্ন্তভূক্ত করা হয়। মজার বিষয় হলো সমাজতন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় আবহে বিশ্বাস করে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ স্বাধীনতার মূল ধারণা বা চেতানার পরিপন্থী। আর জাতীয়তাবাদের বিতর্কে দেশ একাত্তর পরবর্তী সময়ে এখনও বিভক্ত। প্রথমত, বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সাতচল্লিশে বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানের সাথে অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশিদের জাতীয়তাবাদকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে পরিণত করায় একাত্তর অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেটি ভারতীয়ত জাতীয়তাবাদের কাছে পরাভূত হয়ে দীর্ঘ তেপ্পান্ন বছর প্রান্তিক ছিল। এমনকি যারা বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন, তারাও পরিস্কার করে বলতে ব্যর্থ হয়েছেন এটি আসলে কী। কেননা তারা যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা অনেকটাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যরূপ। তবে যে জাতীয়তাবাদ আমাদের স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করেছে তার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল ১৭৫৭ সালের পর বাঁশের কেল্লা, তিতুমীরসহ নানা বীর যোদ্ধারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তা থেকে এবং এর পূর্ণতা পেয়েছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। সুতরাং যে আদর্শ ও মৌরিক নীতির কারণে বাংলা ভাগ হযেছিল ১৯০৫ সালে, তাই আমাদের জাতীয়কতাবাদের আসল রূপ।
আজকের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও জাতীয়তাবাদ কতটা সংরক্ষিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা জরুরি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গণতন্ত্রের চর্চা, ধর্মনিরপেক্ষতা, এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলে বোঝা যায়, আদর্শের অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্যুতি ঘটেছে।১৮ যদিও বাংলাদেশ ডিজিটাল অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, রাজনৈতিক বিভাজন ও দুর্নীতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ব্যাহত করছে।১৯ তাই এ বিভাজন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। মোকাবেলার জন্য করণীয়: এক. গণতান্ত্রিক চর্চার সম্প্রসারণ: মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করা।২০ দুই. শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযুক্ত করে তার দুর্বল দিক তুলে ধরার পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে ভারত কুক্ষিগত করেছে এবং যার অনিবার্য রূপ ছিল চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান তার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা।২১ তিন. সামাজিক সাম্য ও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা: সকল ধর্মের অধিকার সমুন্নত রাখা এবং বিদেশী প্ররোচনায় পা না দিয়ে ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।২২ দুর্নীতি ও বৈষম্য দমন এবং সুশাসন নিশ্চিত করা: জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠ বণ্ঠন করা।২৩
স্বাধীনতা দিবস কেবল একটি উৎসব নয়, এটি জাতীয়তাবাদের প্রতীক। একাত্তরের চেতনা জাতীয় সংহতির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে, যেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত ধারাবাহিকতা আন্দোলন জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি স্থাপন করে। সেই ধারাবাহিকার প্রকৃত রূপ ধারণ করে চব্বিশের অভ্যুত্থানে দ্বিতীয় স্বাধীনতার ডাকের মাধ্যমে। কেননা একাত্তরের স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ভুলে ভারতীয় আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের মধ্যে রেখে পরাধীন করে রেখেছিল। কিন্তু চব্বিশ সে আধিপত্যবাদকে র্নিমূলের কাজ করেছে।
তথ্যসূত্র:
১. রাও ফরমান আলী খান, বাংলাদেশের জন্ম, অনুবাদ ও ভূমিকা, মুনতাসির মামুন, ইউনিভার্সিটি প্রেস রিমিটে, ঢাকা:২০১৯:৫৮।
২. খন্দকার আতাউল হক সম্পাদিত, সিরাজুল আলম খান নির্বাচিত রাজনৈতিক রচনাবলী থেকে সংকলিত, খন্দকার আতাউল হক সম্পাদিত, সিরাজুল আলম খান নির্বাচিত রাজনৈতিক রচনাবলী থেকে সংকলিত,
৩. মুস্তাফা নূরুউল ইসলাম, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: রাজনীতির মহাকাব্য, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়, ২০১৭:২৮।
৪. শামসুজ্জামান খান, উদ্ধৃতি খন্দকার আতাউল হক সম্পাদিত, সিরাজুল আলম খান নির্বাচিত রাজনৈতিক রচনাবলী থেকে সংকলিত
৫. খন্দকার আতাউল হক সম্পাদিত, সিরাজুল আলম খান নির্বাচিত রাজনৈতিক রচনাবলী থেকে সংকলিত, যঃঃঢ়ং://িি.িংযড়শধষংযড়হফযধ.পড়স/নধহমধনড়হফযঁ-ফবপষধৎধঃরড়হ-ড়ভ-রহফবঢ়বহফবহপব-নু-রিৎবষবংং/
৬. রাও ফরমান আলী খান, বাংলাদেশের জন্ম, অনুবাদ ও ভূমিকা, মুনতাসির মামুন, ইউনিভার্সিটি প্রেস রিমিটে, ঢাকা:২০১৯:৭০।
৭. প্রথম আলো, ‘মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে ভুট্টো’, মুক্তিযুদ্ধে দিনলিপি, ২২ মার্চ ২০২১।
৮. প্রথম আলো, ‘মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে ভুট্টো’, মুক্তিযুদ্ধে দিনলিপি, ২২ মার্চ ২০২১।
৯. মুহাম্মদ শামসুল হক, ‘ওয়ারলেসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও চট্টগ্রামের সংগ্রামী ভ’মিকা’, ২৭ মার্চ ২০২৪। যঃঃঢ়ং://িি.িংযড়শধষংযড়হফযধ.পড়স/নধহমধনড়হফযঁ-ফবপষধৎধঃরড়হ-ড়ভ-রহফবঢ়বহফবহপব-নু-রিৎবষবংং/
১০. সমকাল, ‘আ’লীগ নেতাদের অনুরোধে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন: হানিফ’, ২৩ জুলাই ২০২২। এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, মুক্তিযুদ্ধে পূর্বাপর: কথোপকথন, প্রথমা প্রকশানা, ঢাকা, ২০১৩:১০।
১১. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, মুক্তিযুদ্ধে পূর্বাপর: কথোপকথন, প্রথমা প্রকশানা, ঢাকা, ২০১৩:১১।
১২. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, মুক্তিযুদ্ধে পূর্বাপর: কথোপকথন, প্রথমা প্রকশানা, ঢাকা, ২০১৩:১১।
১৩. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, মুক্তিযুদ্ধে পূর্বাপর: কথোপকথন, প্রথমা প্রকশানা, ঢাকা, ২০১৩:১৫।
১৪. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, মুক্তিযুদ্ধে পূর্বাপর: কথোপকথন, প্রথমা প্রকশানা, ঢাকা, ২০১৩:১৫।
১৫. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, মুক্তিযুদ্ধে পূর্বাপর: কথোপকথন, প্রথমা প্রকশানা, ঢাকা, ২০১৩:১৬।
১৬. মহিউদ্দিন হোসেন, ‘বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ: এক পর্যালোচনা’, সমকালীন গবেষণা জার্নাল, ২০১৯।
১৭. এম. রহমান, ‘অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত’, বাংলাদেশ স্টাডি রিপোর্ট, ২০২১।
১৮. সাইফুল করিম, গণতন্ত্র ও সুশাসন: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া, ঢাকা:ন্যাশনাল বুক সেন্টার, ২০১৫।
১৯. রফিকুল ইসলাম, ‘শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: বর্তমান অবস্থা ও করণীয়’, বাংলাদেশ শিক্ষা সমীক্ষা, ২০২০।
২০. মনসুর হাসান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক সাম্য, ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ২০১৭।
২১. আসিফ চৌধুরী, ‘দুর্নীতি ও সুশাসন: বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ’, গবেষণা জার্নাল অফ পলিটিক্স, ২০২২।
( লেখক সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।)