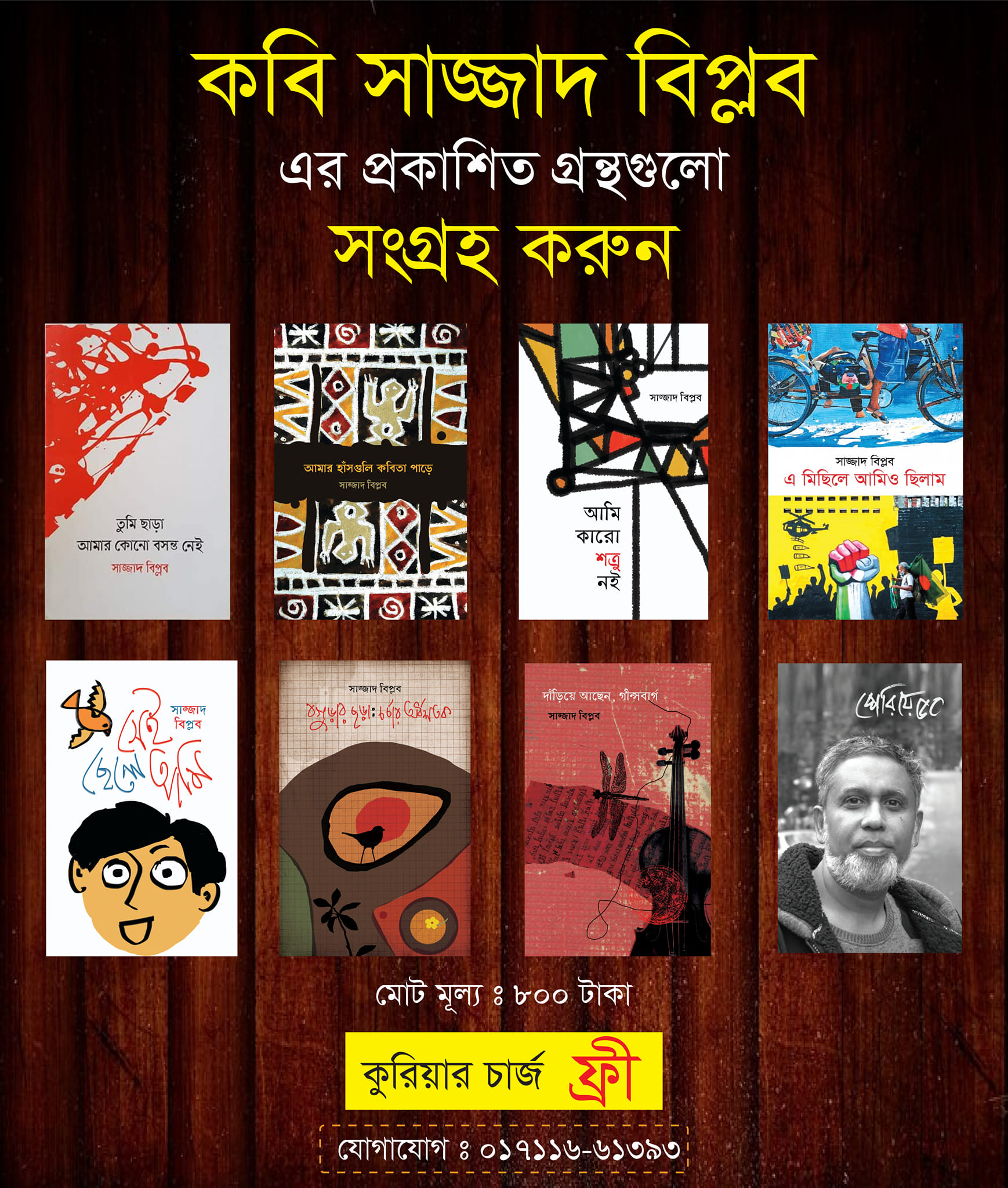আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
সাধারণভাবে ভারতের এবং ব্যাপকভাবে উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসবেত্তা এবং উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলোর নেতারা সব সময় নেতিবাচক, বিদ্বেষপ্রসূত ও উসকানিমূলক কথা বলেন। তারা সংবাদপত্রে এবং টেলিভিশন টকশোতে যে ভাষায়, যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন, তাতে মনে হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহখ্যাত উপমহাদেশের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রাম থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত মুসলিম নেতাদের মধ্যে ভারত বিভাজনের আন্দোলন একটি সাধারণ প্রবণতা ছিল। তারা বলতে চেষ্টা করেন, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাকাল থেকেই মুসলমানরা বিরোধিতা করেছে। তারা এমন কথাও বলেন যে, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, অর্থাৎ মুসলমানরা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতকে কখনো তাদের মাতৃভূমি হিসাবে গ্রহণ করেনি এবং নিজের দেশ হিসাবে ভালোবাসেনি।
উগ্র হিন্দুরা দোষারোপ করেন, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের জন্য মুসলমানদের এ প্রবণতাই শেষ পর্যন্ত দায়ী ছিল। তাদের মতে, বিচ্ছিন্নতাবাদের এ মনোভাব মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এমন তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দুরা তাদের যে ছাড় দিয়েছিল, তাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির করেছিল ভারতমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করার এবং মুসলমানদের পৃথক দেশ পাকিস্তান অর্জন না করা পর্যন্ত তারা সন্তুষ্ট হয়নি।
এসবেরই পরিণতি হিসাবে এসেছে ভারতজুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে ঢালাও অপপ্রচার। কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের বহু আগে থেকে ভারতের বহু মুসলিম শাসক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদতবরণ করেছেন, ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেছেন, বিনা বিচারে কারাগারে কাটিয়েছেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করে নিয়েছে এবং তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে শিক্ষা, চাকরি থেকে। এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখনো মুসলমানদের একটি বড় অংশ দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করে অখণ্ড ভারতের পক্ষে প্রবল ভূমিকা পালন করেছে। এটা সত্য, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক ধারায় ভারতকে বিভক্ত করার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিল; কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য, ভারতের সব মুসলমান মুসলিম লীগের দর্শনের সঙ্গে একমত পোষণ করেনি। ভারত বিভাগের প্রাক্কালে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতেই অবস্থান করতে চেয়েছে।
স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের রাজনীতিবিদের চেয়ে বরং একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করেন। তারা ভারতের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপনের ব্রিটিশ রাজের ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতিকেই আবারও বহাল করতে চেয়েছেন। বিজেপিশাসিত ভারতের বর্তমান রাজনীতি সে নীতিকেই কার্যকর করে ভারতীয় মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা গণমাধ্যম বা রাজনৈতিক ইতিহাসের গ্রন্থে যথাযথভাবে স্থান পায়নি। স্বাধীনতাসংগ্রামে মুসলমানদের অবদানকে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে অথবা পণ্ডিতরা বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবতাকে এড়িয়ে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার পরিবর্তে তারা ভারতের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস রচনা করেছেন। সে কারণেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম বিপ্লবী, সামরিক নেতা, কবি ও লেখকদের অবদান আজ আর তেমন জানা যায় না।
একইভাবে উত্তর প্রদেশের শাহজেহানপুরের মুহাম্মদ আশফাকউল্লাহ খানের অবদান সম্পর্কে ভারতবাসী এখন জানে না বললেই চলে, যিনি ব্রিটিশ প্রশাসনকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে তার বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে লখনৌর কাছে কাকোরিতে ট্রেনে হামলা চালিয়ে ট্রেনে বহনকারী ব্রিটিশ অর্থ লুট করেছিলেন। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন : ‘একটি ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো ইচ্ছা অবশিষ্ট নেই যে, কেউ আমার কাফনের ওপর মাতৃভূমির সামান্য মাটি ছড়িয়ে দেবে।’
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারত চরম নৈরাজ্যের শিকার হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা ও শূন্যতার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের ক্ষমতা বিস্তারের একটি স্থান করে নেয়, যা তারা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে রেখেছিল। বাংলার নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিপদ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার দূরদর্শিতা দেখিয়েছিলেন এবং তা যথাযথ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কোম্পানির শক্তিকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে কলকাতার দিকে অগ্রসর হন এবং ১৭৫৬ সালের ২০ জুন কোম্পানির শক্তিশালী ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেন। কিন্তু তার অবিশ্বস্ত সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায় তাকে প্রথমত কলকাতাকে অরক্ষিত রেখে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসতে হয় এবং ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সেনাপতি ও তহবিল সরবরাহকারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়।
দক্ষিণ ভারতে মহীশূরের শাসক সুলতান হায়দার আলী সহজে কোনো বিদেশি শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেননি। হায়দার আলী ইতিহাসে যে ছাপ রেখে গেছেন, তা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক মহান যোদ্ধার। টিপু সুলতান বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে তার পিতার চেয়েও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। এসব ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন অধিকাংশ ভারতীয় শাসক বিদেশি শাসকে জেঁকে বসার প্রচেষ্টার পরিণতি উপলব্ধি করতে অসমর্থ ছিলেন। টিপু সুলতান তার সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধকৌশলে পাশ্চাত্যের কৌশল অবলম্বন করেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিত্রের সন্ধানে তিনি ১৭৮৫-৮৫ সালে তুরস্কে, ১৭৮৭-৮৮ সালে ফ্রান্সে, ১৭৮৬ সালে আফগানিস্তানে তার দূত প্রেরণ করেছিলেন।
ফরাসি বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে টিপু সুলতান ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নের সমরবিজ্ঞান থেকে রণকৌশল ধার করেন। নবদীক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে গঠিত তার ‘আহমাদি’ বাহিনী আধুনিক ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর আদলে গড়ে তোলা হয়েছিল, যা অটোমান তুর্কিদের জানিসারিদের মতো ছিল।
সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়ে কোনো শাসকের পক্ষে একটি উন্নত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে থাকা সম্ভব নয়। টিপু সুলতানের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। তিনি যদি ব্রিটিশের আনুগত্য স্বীকার করে তার রাজ্যকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামন্ত রাজ্যে পরিণত করতে চাইতেন, তাহলে তিনি হয়তো তার রাজ্য রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তার বাহিনীর সীমিত সামর্থ্য দিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করে মাতৃভূমির রক্ষায় নিষ্ঠার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়েছেন। হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপমহাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন, ‘এই সময়ের সব ভারতীয় শাসকের মধ্যে হায়দার আলী ও তার পুত্র টিপু সুলতান ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক শক্তির বিকাশের সবচেয়ে আপসহীনবিরোধী। তারা অন্যদের চেয়ে আরও বেশি উপলব্ধি করেছিলেন, ব্রিটিশ শক্তির বিকাশের অর্থ ভারতের জন্য বিরাট বিপদ ও বিপর্যয়। মাতৃভূমির স্বাধীনতার প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং বিশেষ করে ব্রিটিশের সঙ্গে অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তির প্রস্তাবকে টিপু সুলতান যেভাবে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তা তাকে বিভিন্ন অঞ্চল শাসনকারী ভারতের সমসাময়িক রাজন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।’
ব্রিটিশরা কেবল শাসক ও রাজন্যদের প্রতিরোধের মুখে পড়েনি, তাদের বিরোধিতায় এমনকি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও ফকিররাও অবতীর্ণ হয়েছিল। ডক্টর তারা চাঁদ তার ‘দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘মুসলিম ফকিরদের আন্দোলন ব্রিটিশ শাসকদের জন্য নিয়মিত সমস্যায় পরিণত হয়েছিল।’ তাদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ, যিনি ১৭৭২ সালের প্রথমদিকে তার পুত্র চেরাগ আলী শাহের সঙ্গে প্রায় দুই হাজার অনুসারী নিয়ে বাংলায় আবির্ভূত হন।
স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে মজনু শাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সীমাহীন সম্ভাবনার একজন ব্যক্তি হিসাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং বহুবার তার হাতে জেনারেল ম্যাকেঞ্জিকে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে। মজনু শাহ তার সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং ১৭৮৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একটি বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান, যে যুদ্ধে মজনু শাহ আহত হয়ে কয়েক মাস পর মারা যান।
১৭৮৩ সালে বাংলার রংপুরে শক্তিশালী এক উত্থান ঘটেছিল। এটি সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহে রূপ নিয়েছিল, যে বিদ্রোহে হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল। এছাড়া ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) পরিচালিত ফারায়েজি আন্দোলন বাংলায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম ছিল, যখন তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করেন, ব্রিটিশের অধীনে তার মাতৃভূমি ‘দার-উল-হরব’ বা যুদ্ধের দেশে পরিণত হয়েছে। অতএব মাতৃভূমি রক্ষায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের উৎখাত করা মুসলমানদের জন্য ‘ফরজ’ বা অবশ্য কর্তব্য। তার পুত্র মৌলভী মুহাম্মদ মুসলেহউদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৫৯) পিতার চেয়ে অধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছিলেন এবং ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে কৌশলগত পদক্ষেপের অংশ হিসাবে বাংলাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে আন্দোলন জোরদার করেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গেও বারাসাতে মীর নিসার আলী ওরফে তীতুমীর ফারায়েজি আন্দোলনে লড়াকু বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন।
১৮৩১ সালের ১৮ নভেম্বর তিনি মেজর স্কট, মেজর সাদারল্যান্ড ও লেফটেন্যান্ট শেকসপিয়রের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে নিহত হন। তীতুমীরের পতনের পর দুদু মিয়া ১৮৪০-৪৭ সালের মধ্যে আশি হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গড়ে তোলেন এবং এ বাহিনী বারাসাত, জয়সুর, পাটনা, ঢাকা এবং মালদাসহ বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন এলাকায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তীতুমীর ও দুদু মিয়ার প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশের হাতে নিষ্পেষিত হাজার হাজার কৃষক নীল চাষিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ইতিহাসে এটি ‘বারাসত বিদ্রোহ’ নামে খ্যাত। শান্তিময় রায় তার ‘দ্য আর্মি ইন ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল ইন চ্যালেঞ্জ: অ্যা সাগা অফ ইন্ডিয়া’স স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘নিসার আলী (তীতু মিয়াঁ) ও মুহাম্মদ মুসলেহউদ্দীনের (দুদু মিয়াঁ) নেতৃত্বে যথাক্রমে বারাসাত ও ফরিদপুরের বিদ্রোহ ছিল ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সূচনা সংগীতের মতো।’
উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তাদের নেতৃত্বদানকারী প্রধান ব্যক্তিত্বদের অন্বেষণ করা হলে প্রমাণিত হবে যে, মুসলমানরা স্বাধীনতাসংগ্রামে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে কম অবদান রাখেনি। বিজেপির নেতৃত্বে ভারতে উগ্রপন্থি হিন্দুরা মুসলমানদের ত্যাগকে খর্ব করার চেষ্টা করলেও ইতিহাসের পাতা থেকে তাদের অবদানকে আড়ালে রাখা যাবে না।