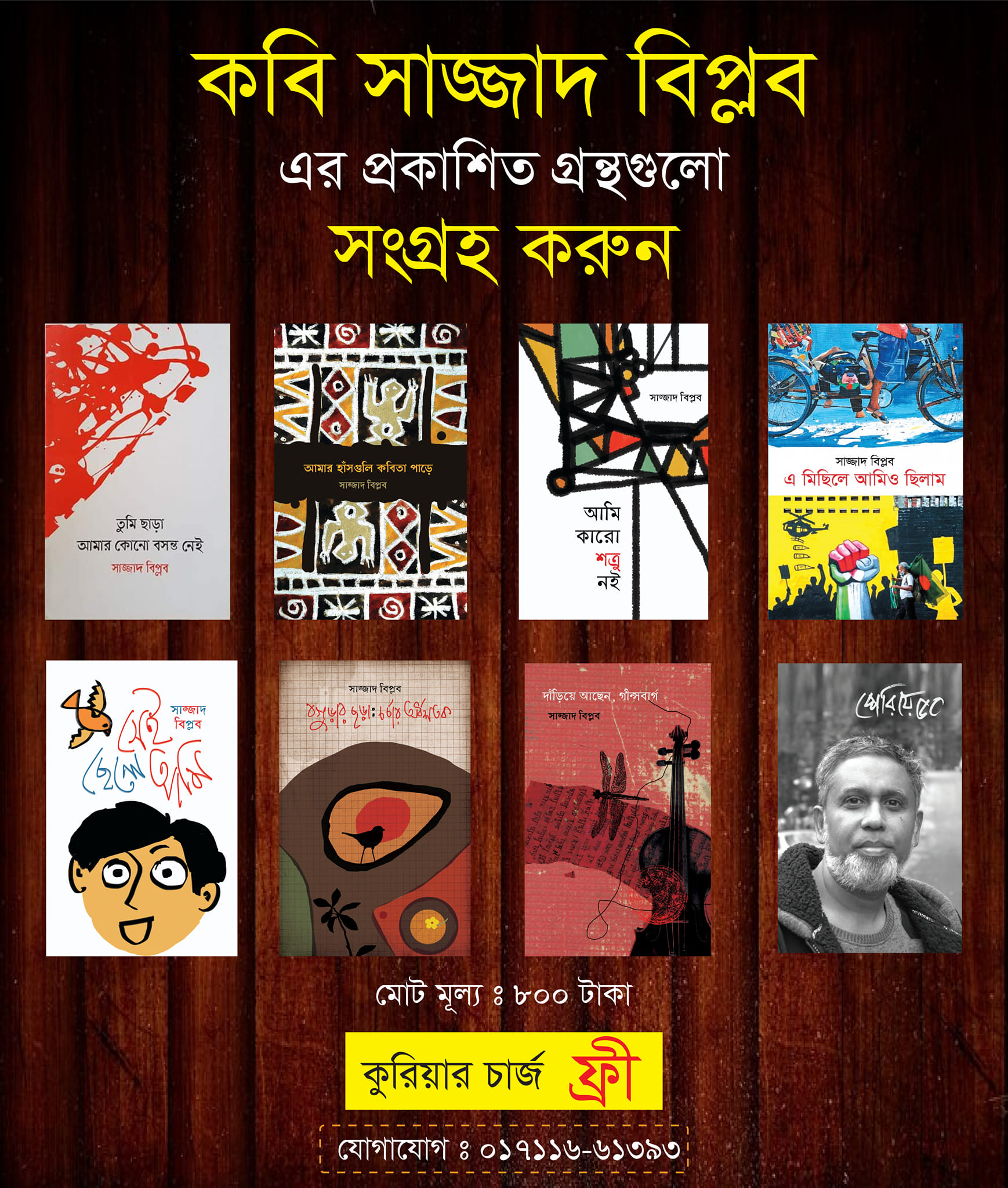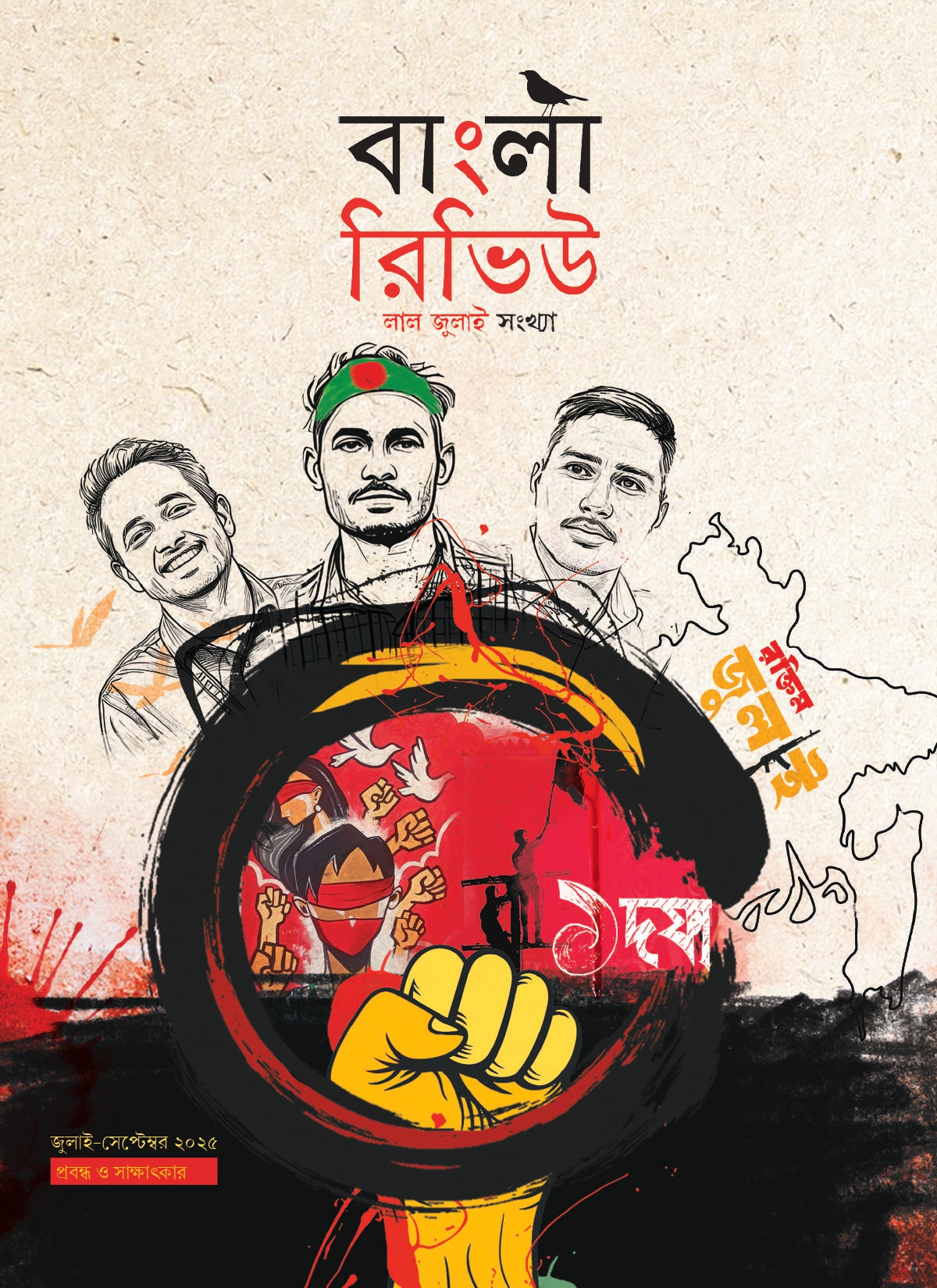ড. মাহবুব হাসান
তখন প্রায় তিনটা বেজেছে। আমরা খেয়ে-দেয়ে বাংলা একাডেমির সবুজ চত্তর থেকে বেরিয়ে যাবো ভাবছি। কাছেই আমার দ্বিতীয় বাড়ি জাতীয় প্রেসক্লাব। সেখানে যাবো। আমরা কয়েকজন বন্ধু একাডেমির পুরোনো বিল্ডিংয়ের পুবের রোয়াকে বসেছি। একটি তরুণ এগিয়ে এলো। চেহারা বেশ চেনা। কিন্তু নাম মনে করতে পারছি না।
আমি মহিবুর রহিম। থাকি ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ও আচ্ছা। আমি তো তোমাকে চিনতে পারিনি। বহুবছর ধরে দেশের বাইরে থাকি তাই তোমার চেহারা মনে নেই।
রহিম ভাটি বাংলার মানুষ। তার একটি বই তুলে দিলেন আমার হাতে।
একঝলকেই বুঝলাম, তিনি হাওর-বাওর এলাকার জনজীবনের রূপকার। যাকে আমি বলি লোকবাংলার কবি। লোকজ কবি, উত্তর আধুনিকতার একজন রূপকার। এই উত্তর আধুনিকতা নিয়ে আমি নীরবে কাজ করেছি। কখনোই বলিনি যে আমাদের বৃহত্তর লোক সংস্কৃতিই আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।ইশারফ এবং তার ওই মনোলগের কর্মকার, নিজেদের উত্তর আধুনিক আন্দোলনের কর্মী মনে করে। গত শতকের আট-এর দশকে তারা এই আন্দোলনের সুচনা করে। এক দল তরুণের এই প্রয়াসকে আমি মনে মনে স্বাগত জানাই।
বললো, ইশারফ বলেছে, আপনি দেশে ফিরেছেন। আমরা, ইশারফসহ বেশ কিছু তরুণ কবি একাডেমির নতুন লেখক প্রকল্পের কবি, কাজ করেছি। নতুন চিন্তার। মনের ভেতরে চিন্তগুলোর ঝাপ্পুরি। সবুজ পাতার ভেতরে, ওরা সেখানেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
আমি খুশি হলাম। ওর বইটি ঝোলায় রেখে বললাম পড়বো।
২.
ইশারফ হোসেন থাকেন মালয়েশিয়ার কুয়ালা লামপুরে। কি কাজ করেন, জানি না। তবে শুনেছি, তিনি কবিতা লেখার চেযে একজন থিংকট্যাংকের চিন্তক হিসেবে নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছেন।
হঠাৎ এক ভোরে, মানে সকাল দশটার দিকে ফোন করলেন ইশারফ। বললেন আপনাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যেতে হবে। আমি তো অবাক। কেন?
সেখানে একটি বক্তৃতার আয়োজন করেছে আমার বন্ধু কবি মহিবুর রহিম। বিষয় উত্তর আধুনিকতা। তখনও পুরোপুরিভাবে উত্তর আধুনিকতা নিয়ে বক্তৃতা দেবার মতো উপাত্ত আমার হাতে নেই। আমার ভাবনার জালে আছে থিসিসের একটি ছোটো সাংস্কৃতিক চ্যাপ্টার। সেই সাত এর দশকে কিছু বাংলা-ইংরেজি বই পড়েছিলাম। বিশেষ করে কলকাতার আমার বন্ধু কবি অমিতাভ গুপ্তসহ বেশ কয়েকজনের। তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তিনি আমার একটি চটি বই ‘নির্জন জানালা’ অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন। সেই বইটির কবিতাগুলোর মাল-মশলাকে তিনি মহাকবিতা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেছিলেন সেই অনূদিত The Window Desolate-এর। একবার কলকাতায় তার যোধপুর পার্কের বাড়িতে নিয়ে গিযেছিলেন কবি রফিকুল ইসলাম। তিনি কলকাতারই মানুষ। অমিতাভ গুপ্ত উপহার দিয়েছিলেন আমাকে তাদের The Uttaraadhunik নামের একটি ইংরেজি সংকলন। ওই সংকলনের সূচি তুলে দিলাম না, তবে এই সংকলনের কবি তাত্ত্বিকগণের প্রতি আমার দৃঢ় একটি ছায়া অর্জন করেছিলাম।
তবে, আমি নিজেকে ওই শ্রেণিভুক্ত করতে কখনোই চাইনি। ইশারফ বললেন, আমি তো কয়েকটি আর্টিকেল পড়ছি আপনার। সেই সুবাদে কাউকে বলেছিলাম যে আপনার থিসিসের একটি কপি পাঠাতে। সেখানে আমি আপনাকে পেলাম নতুন এক কবি ও বিশ্লেষক হিসেবে। সেই বইয়ের শেষ অধ্যায়ের শিরোনাম পড়ে ইশারফ হোসেন উত্তেজিত। ‘লোকজ উপাদান এবং উত্তর-আধুনিক কবিতার সংশ্লেষণ’। ২০০৫ এ বেরিয়েছিলো বইটি বাংলা একাডেমি থেকে। সেই থেকে ২০২০ পর্য়ন্ত কোনো চিন্তাশীল পাঠক বইটি ছুঁয়ে দেখেননি। রিভিউ করবেন এমন কেউই দেশে, আমার বন্ধুকুলের মধ্যে আছে, আমার একবারও মনে হযনি। থাকলে তারা সেই দায়িত্ব পালন করতেন।
তো, একদিন ভোরবেলায় আমাকে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিলেন কামরুজ্জামান স্বপন, পলিয়ার ওয়াহিদ, নোমান প্রধান, ফারুক মোহাম্মদ ওমর, তরুণ প্রকাশক আমার মিঠু কবির এবং আরো কেউ কেউ।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌছে দেখি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন কবি মহিবুর রহিম এবং শাদমান শাহিদ। এরা দুজনই কলেজের অধ্যাপক। সাহিত্য পড়ান। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করলেন প্রবীণ প্রাবন্ধিক ও কবি জয়দুল হোসেন। সেই প্রথম তাকে দেখলাম।
এর মধ্যেই বেশ কিছু সংকলনে এ-দুজনের কবিতা পাঠ করেছি। এবং আমি অবাক হয়ে জানলাম এরা বাংলাদেশের ভাটি এলাকার লোকজ উপাদানই কেবল তাদের কবিতায় ব্যবহার করছেন না, তারা আল মাহমুদের মানবিক ও সাংস্কৃতিক চেতনারও অনুসারী।
আমার প্রিয় কবি আল মাহমুদও তো এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ। যারা তার কবিতার নিবিষ্ট পাঠক তারা জানেন, আল মাহমুদের মানস সরোবর এখানেই এবং জনজীবনের যে সাংস্কৃতিক জীবনসংগ্রাম ও জীবনাচার, তার শেকড়বাকড় এখানেই পোতা আছে।
একটু পেছনে ফেরা জরুরি।
শিকাড়ায়নের ব্যানারে একটি বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন ইশারফ। সেখানে এক তরুণ তাত্ত্বিক ও কবি বাপ্পা আজিজুল বক্তৃতা করতে এসেছিলেন সিলেট মেডিকেল কলেজ থেকে। আমি ছাড়াও বক্তৃতা করেছিলেন ড. উপল তালুকদার। কথাকার জাকির তালুকদার এবং আরো কয়েকজন। উপল আসলে তার উত্তর আধুনিকতা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। আর কথা বলেছিলেন মহিবুর রহিম, তার ভাটি বাংলার সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের আলোকে বাংলা কবিতায় তার প্রভাব নিয়ে। সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বব্যাপী যে ধনী-গরিবি ব্যবধান এবং কিভাবে ধনবানেরা শোষণ চালু রাখে তার গরিব প্রতিবেশির ওপর, ইতালিয়ান বামচেতনার সমাজ বিশ্লেষক অ্যান্তনিও গ্রামসীর চিন্তার আলোকে সাংস্কৃতিকভাবে শোষণের পথটি চিনিয়ে দিয়েছেন। কেন্দ্র ও প্রান্তিকের মধ্যে মেরুদূর ব্যবধান কেবল শোষণের রাজপথ ধরেই হচ্ছে না, সাংস্কৃতিকভাবে সেই শোষণের একটি মিহিন ও মসৃণ ধারাও কেন্দ্র চালু রাখে। আমিও সেই আলোকেই কথা বলেছিলাম, মনে পড়ে।
এ-সব কথা বলা সহজ, তার বাস্তব রূপ দেখানো কঠিন। এটাই কালচারাল হেজেমনির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ কারুকাজ। আমরা আমাদের লোকজ গ্রামীণ পোশাককে ঘৃণা করে তাকে ফেলে দিয়ে ইউরোপিয়ান পোশাক প্যান্ট পরেছি। একে আমরা প্রগতির সঙ্গে এক করে দেখি আজ। কিন্তু ভেতর থেকে আমাদের চিন্তাকেও যে শাসন করছে ইউরোপ তা চিন্তা করে দেখি না। আমাদের হাজার বছরের শ্রমজীবনের প্যাটার্ণকেও যে বদলে দিযেছে আধিপত্যবাদি ইউরো চেতনা, তা কল্পনা করি না। এটা আমাদের বুঝতে হবে।
আমার চিন্তা হচ্ছে উত্তর উপনিবেশায়নের ধারাবাহিকতায় শোষণ কিভাবে চালু রেখেছে ইউরোপ-আমেরিকা। আমি ‘অনন্য’ নামের সাহিত্য পত্রিকার ব্যানারে সাংস্কৃতিক পরাধীনতাকে চিহ্নিত করে শোষণ ও শাসনকে কিভাবে চালু রেখেছে পশ্চিম, সেই বিষয়ে সচেতন করে তোলার কাজটি করি। কেবল চিন্তার ক্ষেত্রেই নয়, ইউরোপ তাদের কালচারাল হেজেমনি বা সাংস্কৃতিক আধিপত্য বজায় রেখেছে, তা চিহ্নিত করে এর মূল উৎপাটন করা জরুরি।
সেই মহিবুর রহিম ফোন করে জানালো ভাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসতে হবে আমাকে। আমি জিজ্ঞেস করিনি কিসের অনুষ্ঠান।
সেখানে গিয়ে দেখি ওই দিনটি মহিবুরের জন্মদিন। আমি অনেকটাই চমকে গেলাম। আমি তো ওর সম্পর্কে কিছু শিখে আসিনি। চলনসই যে সব কথা আমরা বলে থাকি, সেই রকম কথা বললাম তার উদ্দেশে। ঢাকায় যতবার তিনি এসেছেন ততবারই দেখা হয়েছে। একবার বাংলা একাডেমিতে বই কেনার সময় দেখা হলো। জয়দুল হোসেন সঙ্গে ছিলেন
এর পর আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।
আমার আগেই মৃত্যু তার সঙ্গে দেখা করে নিয়ে গেছে তাকে চিরদিনের জন্য।
ফুটনোট :
মহিবুর রহিমের বেশ কয়েকটি লেখার কোটেশন আমাকে পাঠিয়েছেন ইশারফ হোসেন। পড়ে দেখি, সেগুলো বেশ কয়েকবারই আমি ব্যবহার করেছি। তার থেকে একটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
উত্তরাধুনিকতাকে বাংলা ভাষী লেখক পাঠকের কাছে প্রণিধানযোগ্য এক ডিসকোর্সে রূপ দিতে যারা নব্বই দশকের শুরু থেকে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন উত্তরাধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ইশারফ হোসেন। সে সময়ে আমিও এই চিন্তা চেতনার সহযোগী ছিলাম। সাহিত্যের একজন আগ্রহী ছাত্র হিসেবে আমি এখনো মনে করি বাংলা কবিতা বা সামগ্রিক সাহিত্যে একটি নতুন ডাইমেনশন আনার জন্য এই চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিতে হবে। যারা নতুনভাবে এই উদ্যোগটি এগিয়ে নিতে অগ্রসর হয়েছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।