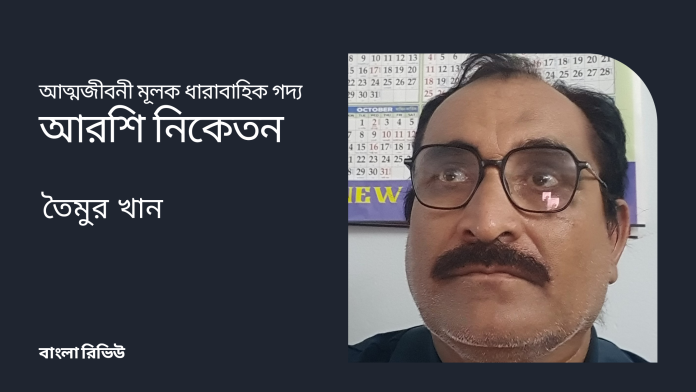তৈমুর খান
৫ভাঙা আয়নার মুখ —————————————————–
গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুল থেকে পাস করে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হই পাশের গ্রামের আয়াস হাইস্কুলে। এই স্কুলে এসে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। মনে হয় এতদিন আমি যেন এক কুয়োর ব্যাং হয়েই ছিলাম। এবার আমার মুক্তি ঘটল বিরাট এক দিঘিতে এসে। এই আয়াস হাইস্কুলেই চতুর্থ শ্রেণিতে একবার বোর্ডের পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম। এখানে তখন সেন্টার হতো। সেই সময় এখানকার শিক্ষক মশাইরা এতই ধমক দিয়েছিলেন যে, ভয়ে কয়েক ফোঁটা পেচ্ছাবও প্যান্টে করে ফেলেছিলাম। সেই পরীক্ষায় পাশ করা খুব শক্ত ছিল। তবু আমি প্রথম শ্রেণি পেয়েছিলাম।
তারপর এই ১৯৮২তে নবম শ্রেণি। ১৯৮৩ তে মাধ্যমিক। সেই বছরই আমার দাদার মৃত্যু ঘটে। দাদার মৃত্যু আমাকে অনেকটাই শূন্য করে দেয়। কেননা দাদার সঙ্গে প্রথম শহরে আসা, বিভিন্ন গ্রামে উৎসবে অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া এমনকি পিসি-মাসিদের বাড়ি গেলেও দাদার সঙ্গে যাওয়া। নিজে না খেয়ে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দাদা আমার খোঁজ করতেন। ঢিলেঢালা জীবনযাপনের মানুষটি হয়ে উঠেছিলেন আমার জীবনের আদর্শ। মাঠে ছিল তাঁর জোগানদারের কাজ। মাথায় একটা বড় পাগড়ি বেঁধে একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে হাতে একটা বড় লাঠি নিয়ে সারারাত ফসল আগলাতেল। কখনো গান গাইতেন, কখনো গল্প বলতেন। হাটেবাজারে গ্রামেগঞ্জে তাঁর কাছে সবাই ছিলেন আপনজন। কখনো হাঁসের ডিম, আখ, তিল-তিসি, খুচরো মাছ বেঁধে নিয়ে শহরে যেতেন। পরিচিত বিভিন্নজনকে সেগুলো দিতেন। বিনিময়ে তাদের বাড়িতে চা খেতেন। অতিরিক্ত চা পছন্দ করতেন। বিশেষ করে নবান্নের সময় বিভিন্ন বাড়িতে পালা করে আমাকেও নিয়ে যেতেন নবান্ন খেতে। দুর্গাপূজায় দশহারার দিন মুড়িমুড়কিতে আঁচল ভরে যেত। সেই দাদাকে হারিয়ে আমি যারপরনাই অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলাম। দাদা নিজের নাম ‘নবির খান’ বড় বড় অক্ষরে সই করতেন। তাঁর পিতার নাম ‘গরিব খান’ও লিখতে পারতেন। জহরলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী এবং কোনো কোনো ব্রিটিশদের কর্মকাণ্ড বিভিন্ন প্রসঙ্গে গল্প করতেন। পুরনো দিনের বহু কথা তাঁর মুখ থেকেই জেনেছিলাম। মাধ্যমিকে বই কেনার জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন হলে দাদা তাঁর একমাত্র সম্বল এক আনা পুকুর বিক্রি করে আমাকে শো-তিনেক টাকা দিয়েছিলেন। অবশ্য তার আগেই পাঁচ কাঠা জমি আমার নামকরণের সময় লিখে দিয়েছিলেন। যা পরবর্তীকালে আমিও বিক্রি করে দিয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ধানের সময় মাঠে যেতাম ধান কুড়াতে। ঝরে পড়া ধানের শিষ ঝুড়িতে একটা একটা করে কুড়িয়ে জমা করতাম। আবার মাঝে মাঝে একটা কোদাল নিয়েও মাঠে যেতাম। চাষিরা ধান কেটে বাড়ি নিয়ে গেলে জমিতে বা আলে দেখতে পেতাম ইঁদুরের গর্ত। তখন মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ইঁদুরগর্তের ধান তুলতাম। সোনালি ধান মাটির তলায় থেকে থেকে বাদামি রং ধারণ করত। মা বলতেন, এই ধানের মুড়ি ভালো হয়। তখন তা মুড়ির জন্য দিতাম। ইঁদুরগর্তে ধান তুলতে গিয়ে ধান আছে কিনা হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করার সময় কতবার যে ইঁদুরের কামড় খেয়েছি তার হিসাব দিতে পারব না। রক্তাক্ত আঙুল নিয়ে নিমের পাতা চিবিয়ে দেখতাম তার তেতো স্বাদ বদলে গেছে কিনা। শুনেছিলাম সাপে কামড়ালে জিভে আর স্বাদ থাকে না। তবে একবার সেই তেতো স্বাদ পাইনি। তখন ওঝার কাছে গিয়েছিলাম বিষ আছে কিনা পরীক্ষা করাতে। সে যাত্রা বেঁচে ছিলাম, কারণ সাপটি বিষাক্ত ছিল না। দাদা এসব দেখতেন তাই মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন মাঠে আর গেরস্থ চাষিকে বলতেন, “আমার পোতাকে দু-আঁটি ধান দাও পিঠা খাবে।”
ধান কুড়িয়ে কুড়িয়েই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতাম, আবার কিছু ধান বিক্রি করে দোকানে খাবারও কিনতাম। দাদা ও বাবা দুজনেই করতেন মাঠের জোগানদারের কাজ। মাঠ থেকে কিছু ধান এনে রাতের বেলায় তা বিক্রি করে চা ও পাউরুটি কিনতেন। প্রায় নিয়ম করেই আমিও তাঁদের সঙ্গে বসে যেতাম। একেক দিন ঘুমিয়ে থাকলে আমার জন্য রাখা থাকত। সকালে উঠে তাই খেতাম। এভাবেই শীতকালে আমাদের খাবারে জোগাড় হতো। তবে গায়ে দেবার তেমন কাপড় ছিল না। একখানা সুতি গেঞ্জি কোনোরকম জোগাড় করতে পারলেও চাদর কিনতে পারতাম না। মা তখন তাঁর পরনের কাপড় ভাঁজ করে গলায় জড়িয়ে বেঁধে দিতেন। এতেও শীত যেত না। দাদা তখন খড় জড়ো করে আগুন পোহাতেন। আমরাও সেখানে গিয়ে শামিল হতাম। তারপর কখনো কখনো সূর্য ওঠার অপেক্ষা করতাম। কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে থাকলে ঘর থেকে বেরোতে পারতাম না। তবে সেই সময় আমার বাবা আরেকটি কাজও করতেন। খেজুর গাছে হাঁড়ি বেঁধে প্রতিদিনই খেজুরের রস পাড়তেন। যার খেজুর গাছ তাকে অর্ধেক রস দিয়ে বাকি অর্ধেকে আমাদের চা হতো। খেজুর রসের চা-এর স্বাদ অপূর্ব। দাদার ছোট ভাই অবির খানও চা খেতে চলে আসতেন আমাদের বাড়ি। চা খেতে খেতেই গল্প হতো কী করে চাষবাস হবে। কী কী ফসল এ বছর লাগানো যাবে। আমি একটু বেলা হলে একটা ঝুড়ি ও কোদাল নিয়ে বের হয়ে যেতাম ইঁদুরের ধান তোলার উদ্দেশ্যে। কোনো কোনো দিন আমার বাড়ি ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যেত।
১৯৮২ ও ৮৩ এই দুটি বছর ছিল আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময় আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে রামপুরহাট থেকে ব্রহ্মাণী নদীর ব্যারেজের ওপর দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছিল যা ঝাড়খণ্ড অবধি গেছে। এই রাস্তার মাটি কাটার কাজে প্রচুর শ্রমিকের দরকার হতো। আমাকে নিয়মিতই শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে হতো। সারাদিন মাটি কেটে ছয় থেকে আট টাকা রোজগার করতাম। সহপাঠীদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সদ্য নির্মিত হওয়া রাস্তার পাশ দিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে দেখতাম। তখন লজ্জায় মাটি বহন করা ঝুড়ি দিয়ে নিজের মুখখানা আড়াল করতাম। কাজের চাপে প্রায়ই উপস্থিত হতে পারতাম না ক্লাসে । সারাদিন মাটি কাটার কাজ করে বাড়ি ফিরে এসে রাত্রিবেলায় বই খুলে আর পড়াও করতে পারতাম না। মাথার ঠিক মাঝখানে চাঁদিতে দপদপ শব্দে একটা সংকোচন হতো আর মাথাটা অসম্ভব ব্যথা করত। বুকের ওপর বই নিয়েই তখন ঘুমিয়ে পড়তাম। তবে মাটি কাটার কাজ গ্রীষ্মকাল ছাড়া অন্য সময় হতো না। জমিতে ধান পোঁতা হয়ে গেলে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে নিড়ানি দেওয়ার কাজ শুরু হতো। ভ্যাপসা গরমে ধানের জমিতে আগাছাগুলো তুলে ফেলতাম। একদুপুর কাজ করে গেরস্থ বাড়ি থেকে পেতাম তিন কেজি খুদ। এই খুদগুলি চালুনে চেলে মা দু’ভাগ করতেন। একটু মোটা মোটাগুলি যাতে ভাত রান্না করে খাওয়া যায় সেগুলি জমাতেন। আর ছোট ছোট খুদগুলি জাউ রান্না করতেন। প্রতিদিন শাকপাতা অথবা কদম রান্না হলে তা দিয়েই আমরা সেই জাউ খেয়ে নিতাম।
গেরস্থ বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে কোনো কোনোদিন গেরস্থ হুকুম দিতেন গোরুর সেবাযত্ন করতে হবে, কারণ মাহিন্দার কাজে আসেনি। তখন মাঠে না গিয়ে খড় কেটে জমা করতাম এবং গরুর পাতনায় পাতনায় তা ভরে দিয়ে খোল-জল দিয়ে গোরুর খাবারের উপযোগী করে দিতাম। গোয়াল ঘরের গোবরগুলি ঝুড়ি ভরে এক জায়গায় জমা করতাম আর ঝাঁটা দিয়ে পুরো গোয়ালঘরটি পরিষ্কার করতে হতো। এইসব কাজ করতে প্রায় সারাদিনই লেগে যেত। মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম সেইসব গেরস্থ বাড়ির সুন্দরী নারীদের। চকিতে এসে কোনো কিছু এনে দেওয়ার তারা আবদার করত। কখনো চাল থেকে লাউ পেড়ে দেবার, তো কখনো টিউবয়েল থেকে জল তুলে বাথরুমের চৌবাচ্চায় ভরে দেওয়ার। তাদের দিকে তাকাতে গিয়ে অনেকবারই খড় কাটতে কাটতে নিজের আঙুলকেও ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতাম। এরা কেন এত সুন্দরী হয়? এদের ঘামও কি সুগন্ধী হয় তবে? তখন এসব নিয়ে খুব ভাবতাম। কিন্তু তখনই আশ্চর্য হতাম, এদের এত সুন্দরী বউ-বিটি থাকতেও মুনিষ খাটতে আসা কোনো অল্পবয়সী মেয়েকে গেরস্থ যখন-তখন নিজস্ব ঘরে একাকী ডেকে নিয়ে গিয়ে দিন দুপুরে দরজা বন্ধ করতেন। অথবা দেখতাম কাজের মাথায় গেরস্থ দাঁড়িয়ে অনেক হাসি তামাশার মধ্যে দিয়ে নিষিদ্ধ কোনো ইচ্ছার কথাও তাকে জানিয়ে দিচ্ছেন। কিছু প্রলোভন দেখালেই এইসব মেয়েদের যে সহজেই পাওয়া যায় তা বহুবার প্রমাণ পেয়েছি।
নানা রকম ভাবনার মধ্যে দিয়ে আমার চেতনা যে জটিল হয়ে উঠছে এই সময়ই তার টের পাই। একদিকে অন্যায়ের প্রতি প্রবল প্রতিরোধ, অন্যদিকে দারিদ্র্যের প্রত্যাঘাত এক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে চলেছে। ধনীদের অসংযমী প্রবৃত্তির বেলেল্লাপনা ভোগঐশ্বর্যে জীবন কাটানোর বোহেমিয়ান সুখ দেখতে দেখতে যেন অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। আমার মধ্যে প্রতিবাদী সত্তা থাকলেও তাকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছি। কেননা এসব করার মতো সামর্থ্য আমার নেই। তাই যতবার মননের আয়নায় নিজ রূপের প্রতিফলন ঘটছে ততবারই নিজেকে খণ্ড খণ্ড মনে হচ্ছে। নিজের পূর্ণ রূপের পূর্ণতা কখনোই দেখতে পাচ্ছি না।