আবু তাহের সরফরাজ
ষাট ও সত্তরের দশক পেরিয়ে আশির দশকে বাংলা কবিতার ভাঙচুরের খোঁজ-খবর আমরা কম-বেশি জানি। এই দশকে আগের দশক থেকে কবিতাকে নতুন আঙ্গিকে রূপ দিতে সচেষ্ট হন একঝাঁক কবি। কী বিষয়-আঙ্গিকে, কী ভাষাশৈলী, সবদিক থেকেই কবিতার শরীরকে আমূল বদলে দেয়ার প্রয়াস এই দশকে আমাদের চোখে পড়ে। এই প্রয়াস মূলত দানা বেঁধে ওঠে ছোটকাগজ কেন্দ্রিক কাব্যচর্চার মধ্যদিয়ে। সে সময়ে গোষ্ঠিভিত্তিক ছোটকাগজ আন্দোলন গড়ে ওঠে। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যপাতার মোড়লি আস্ফালনকে পাশ-কাটিয়ে তরুণ কবিদের এই যাত্রা বাংলা কবিতায় সত্যিই যে নতুনত্ব এনে দিয়েছিল, সন্দেহ নেই। কী ছিল আশির দশকের কবিতার প্রবণতা? কী-কী বৈশিষ্ট্য তারা আসলে ধারণ করতে চেয়েছিলেন তাদের কবিতায়? এ বিষয়ে পাঠ নিতে আমাদেরকে পড়তে হবে ওই দশকের একঝাঁক তরুণ কবি কর্তৃক উত্থাপিত কবিতার সমগ্রবাদী ইশতেহার। তো চলুন, ইশতেহারে একটু চোখ বোলানো যাক:
১. প্রচলিত পঙ্ক স্রোত থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে।
২. কবিতার শব্দ হবে এমন যা পাঠকের চেতনায় আছড়ে পড়বে হাতুড়ির মতো; গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে চৈতন্যের ইট।
৩. আমরা এবং একমাত্র আমরাই নির্মাণ করবো শব্দের অভিব্যক্তিক সংরক্ত চরিত্র।
৪. পাঠকের জন্য কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা হবে মৃত্যু-যন্ত্রণার মতো। শাণিত কৃপাণের মতো কবিতা ঢুকে যাবে পাঠকের মনোরাজ্যে; আর পাঠক আর্ত ঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে দেশকাল পেরিয়ে পৌঁছে যাবে এক আতীব্র বোধের চূর্ণিত জগতে।
৫. থুতু ছুড়ি তথাকথিত সুন্দর ও কুৎসিতের স্থূল কাব্য-বন্দনায়। কেবল আমাদের অভিজ্ঞানে রয়েছে রহস্যময় সংবেদনের আবর্ত।
৬. এইমাত্র জন্মান্তর ঘটেছে প্রাজ্ঞ অশ্বত্থের, তার অনন্ত শিকড় শুষে নেবে প্রতিটি রসকুম্ভের আত্মা। আর তার মহাবিস্তৃত প্রশাখার করতল অধিকার করে নেবে সমগ্র বিশ্ব ও অবিশ্বকে।
৭. চাই চামড়া ছাড়ানো দগদগে আদিমতা আর রক্তের ফেনময় ঘূর্ণিনাচ।
৮. ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করে কবিতায় প্রয়োগ করতে হবে হিন্দুবাদী প্রক্রিয়া।
ওপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে মোটামুটি অনুসরণ করে আশির কাব্য-আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, সকল বৈশিষ্ট্যই যে সকল কবি সফল উপায়ে কবিতায় শিল্পিত করেছেন, তা কিন্তু নয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতো করে বিগত দশকের বলয় ভেঙে কবিতায় স্বকীয়তা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে ইশতেহারে বর্ণিত কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হলেও কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য সুষ্পষ্ট থেকে গেছে কারো কারো কবিতায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে আর যাই হোক, কবিতা লেখা সম্ভব নয়। তবে আগের দশকের কবিতা থেকে নতুন শিল্পশৈলীর কবিতা নির্মাণে আশির দশকের কবিদলের যে যাত্রা, সেই যাত্রা বাংলা কবিতার ইতিহাসে স্বরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে রিফাত চৌধুরীর কবিতা উত্তর-প্রজন্মের কবিতার পাঠকের কাছে বিশেষভাবে আদরণীয়। এর প্রধান কারণ রিফাতের ভাষার সাবলীল গতি। রিফাতের কবিতা পড়লে মনে হয় তিনি যেন কবিতা নয়, সামনে বসে কথা বলছেন। প্রতিদিনের যাপিত জীবনে আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি একে অন্যের সাথে কথা বলতে, রিফাতও সেই ভাষায় তার কবিতার শরীর নির্মাণ করেন। তার কবিতা বুঝতে শব্দ নিয়ে পাঠককে নাড়াচাড়া করতে হয় না। সহজে সহজ উপায়ে কিভাবে কবিতা লেখা যায়, রিফাতের কবিতা না-পড়লে পাঠকের হয়তো জানাই হতো না। আমাদের প্রতিদিনের যাপিতজীবনের টুকরো-টুকরো ছবি নানা ব্যাঞ্জনায় শিল্পিত মাত্রা পায় রিফাতের কবিতায়। বলার কথা খুব সহজেই ছোট্ট পরিসরে কবিতার ভেতর বলে ফেলেন রিফাত। এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারে রিফাত বড়ই মিতব্যয়ী। কবিতার শরীরকে দীর্ঘ করার প্রবণতা তার ভেতর নেই। বলা যায়, বিন্দুতে রিফাতের কবিতা সিন্ধু ধারণ করে। আটপৌরে জীবনের অন্তর্লীন সহস্র স্রোতধারায় উৎসারিত জীবন-অভিজ্ঞতার সারাৎসার রিফাতের কবিতা। শিল্প যেহেতু প্রতি-বাস্তবতা সেহেতু রিফাত বিচিত্রমুখি প্রতীকে সেই অভিজ্ঞতাকে ভাগাভাগি করে নেন পাঠকের সাথে। আসলে কবি হিসেবে রিফাতের অন্তর্গত বোধের প্রকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সহজবোধ্য শব্দের নির্মাণে গভীর অন্তর্বোধের প্রকাশ। এই লক্ষ্যেই তিনি আরম্ভ করেন তার কাব্যযাত্রা। এবং এ যাপত ওই বৈশিষ্ট্যে একাগ্র রয়েছেন। ‘আশা’ কবিতাটি পড়া যাক:
রংচটা ধুলোমাখা তোবড়ানো পুরনো
পরপর দাঁড় করানো কয়েকটি রিকশা
এক নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।
একটা রিকশার পিছনে বেগম খালেদা জিয়ার মুখ আঁকা।
স্প্রিং বের হওয়া ফাটা চামড়ার সিটে
অলসভাবে বসে আছে রিকশাচালক।
রিকশার চাকা দুটো টাল খাওয়ানো।
ওপরের কবিতা যেন কবিতা নয়, একটি ফটোগ্রাফ। পথ-চলতি কবি যেন শব্দের ক্যামেরায় ক্লিক করে একটি দৃশ্যকে ধরে রেখেছেন। আমাদের চারপাশে কত কতই তো দৃশ্য হরহামেশা আমরা দেখতে পাই। বিত্তবানদের ঝা-চকচকে রমণীদের রঙচটা মুখ ও দেহ-সৌষ্ঠব আমাদের চোখে খুবই কমনীয়। হয়তো তাতে শিল্প-সুষমাও রয়েছে। কিন্তু রিফাতের চোখে বিত্তবানদের জৌলুস থেকে দারিদ্র-পীড়িত দৃশ্যই বেশি শৈল্পিক। কারণ, রিফাত সারা-জীবন জীবিকার সংগ্রামে যুদ্ধরত একজন মানুষ। সমাজের এক্কেবারে নিচুতলার মানুষের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশেছেন। একইসঙ্গে মিশেছেন ধনীক-শ্রেণির মানুষের সঙ্গে। ধনীদের মুখের মুখোশ দেখেছেন, একইসঙ্গে দেখেছেন তাদের প্রকৃত মুখ। তিনি আরও দেখেছেন, জীবন সংগ্রামে লড়তে লড়তে পিঠকুঁজো হয়ে যাওয়া মানুষদের মুখে মুখোশ পরার মতো সময় নেই। দেহের সৌন্দর্য বাড়াতে মেকাপেরও সময় নেই। তারা প্রতিমুহূর্তে ভাগ্যের বিরুদ্ধে ফাইট দিচ্ছে। সুতরাং, গণমানুষের শ্রমে ও ঘামে যে জীবনদৃশ্য আঁকা, সেই দৃশ্যের প্রতিই রিফাতের প্রগাঢ় মমতা। এই মমতা প্রকাশে তার কোনো ভনিতা নেই। শিল্পের কাঁধে দায় চাপিয়ে কবিতাকে শিল্প করে তোলার বাগাড়ম্বর নেই। সহজকে সহজ উপায়েই তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। যা তুলে ধরেন সেই দৃশ্যের গভীরে গেলেই পাঠক বুঝতে পারেন, জীবনবোধের কত সূক্ষ্ম অবলোকন রিফাত তার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এখানেই রিফাতের কবিতার শৈল্পিক কারুকাজ। বলা দরকার, রিফাতের কবিতায় চিত্তগ্রাহী কোনো অনুষঙ্গ আমরা পাই না। যা কিনা ওপরে উল্লিখিত ইশতেহারের প্রস্তাবনা ছিল। রিফাতের কবিতা পাঠমাত্রই এক ধরনের যন্ত্রণা পাঠকের ভেতর অনুভূত হতে থাকে। এই যন্ত্রণা মূলত জীবনের ভেতর লুকিয়ে থাকা অন্তঃসার-শূন্যতা আবিষ্কারের জন্য। রিফাতের কবিতা আমাদের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে দগদগে ঘা বের করে দেখায়। তার মতো এভাবে আশির আর কোনো কবি দেখিয়েছেনে কিনা, খুঁজে দেখতে হবে।
ছেঁড়া জামা পরা এক কিশোর
ছেঁড়া জামা তার প্রতিভা
আলো-ছায়া ঘেরা আকাশের নিচে
বোরখা পরা প্রার্থনারত মহিলা,
বোরখা তার প্রতিভা
আয়না হাতে একটা বেশ্যা
আয়না তার প্রতিভা।
(মেঘের প্রতিভা)
চমকটা কোথায়, ধরা যাচ্ছে কি? কবিতার ভেতর দিয়ে যেসব কথা রিফাত বলেছেন সেসব কথা খুবই সহজ। কিন্তু ওইসব কথার মানে বুঝতে হলে জীবনকে খুঁড়ে দেখতে হয়। জীবন-অভিজ্ঞতার খুব ভেতরে গিয়েই সেই গভীরতার তল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। প্রতিভা শব্দটি আমরা সাধারণত বিশেষ বিশেষ গুণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। কিন্তু রিফাত চৌধুরী শব্দটিকে সর্বজনীন করে তুলেছেন। মানে, যার যা আছে তা-ই তার প্রতিভা। প্রতিভার আলাদা কোনো চাকচিক্য নেই। জৌলুশ নেই। যে ছেলের গায়ে ছেঁড়া জামা সেই ছেলের প্রতিভার স্মারক ওই ছেঁড়া জামা। প্রার্থনারত পর্দানশীন নারীর প্রতিভা তার পর্দা। আবার, বারবণিতার প্রতিভা তার হাতের আয়না। যে আয়না সে তার রূপকে খদ্দেরদের চোখে আকর্ষণীয় করতে ব্যবহার করে। এই কবিতায় আমরা তিনটে চরিত্র পাই। ওইসব চরিত্রের বিশেষ একটি দিক উল্লেখ করে কবি তাদের প্রতিভাকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু আমরা পাঠক হিসেবে ওই তিনটে চরিত্রের বিশদ জীবনকে উপলব্ধি করতে পারি। অবশ্য তা রিফাতের ইঙ্গিতের সূত্র ধরেই। কবিতার চমকটা তো এখানেই থাকে। কবি কোনো একটি ইঙ্গিত প্রকাশ করেন কবিতায়। এরপর পাঠক তার সূত্র ধরে বোধের গভীরে পৌঁছতে পারে। লক্ষ্যণীয় যে, রিফাত চৌধুরীর কবিতার পরিসর সংক্ষিপ্ত। যা বলার দরকার সোজাসাপ্টা বলে দেন। এরপর পাঠক কবিতার ভাবাবুলতায় আচ্ছন্ন হয়ে জীবনের চিত্র-বিচিত্র জীবনের রঙ্গশালায় প্রবেশ করেন। জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।
আড়ম্বরহীন সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত রিফাত চৌধুরী। কথাবার্তায় সহজ ও সরল। চতুরালি কোনো ভাবভঙ্গি তার ভেতর নেই। তার চরিত্রের এসব বৈশিষ্ট্য প্রভাব ফেলেছে তার কবিতায়। ঢাকা শহরের গোছানো রোবটিক বাস্তবতাকে তিনি পাশ-কাটিয়ে চলেন। গ্রাম্য সরলতা তাই তার কবিতাকে করে তুলেছে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। তার কবিতায় কোথাও আরোপিত কোনো কিছুই নেই। যা আছে সবই যেন প্রাকৃতিক। নদীর স্রোতের মতো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ফুলের গন্ধের মতো সহজাত। আর এ কারণেই রিফাত চৌধুরীর কবিতা এখনো যে কোনো তরুণ কবি আগ্রহ সহকারে পাঠ করে। দীক্ষা নেয় কবিতার শৈলী নির্মাণের। কবিতার বিষয়ে রিফাত চৌধুরীর ভাষ্য, “কবিতা কেবলমাত্র আবেগের জায়গা দখল করে না, সাথে সাথে চারপাশের অস্তিত্বের সংকটকেও ধারণ করে। আমার কাছে কবিতা অনেকটা এরকম— প্রথমে তা ছবির মতো ভেসে ওঠে, আর ধীরে ধীরে ফিল্টারিং হয়ে গেলে হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি শোনার অবস্থা তৈরি হয়— একটা জান্তব চিত্রের সান্নিধ্যে আসতে পারি তখন আমি।” আমরা জানতে পারলাম, রিফাত চৌধুরীর কাছে কবিতা কেবল বোধের অনুরণন নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতাও এর সাথে জড়িত। কবিতার বিষয় তার কাছে নৈর্ব্যক্তিক নয়, বরং মূর্ত। যে কোনো বোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি প্রথমে ছবির মতো কিছু একটা অন্তর্চোখে দেখতে পান। এরপর ওই ছবিটা নানা স্তরে নানা মাত্রিক সংকেত তৈরি করে প্রক্রিয়াজাত হয়। এরপরই হৃদপিণ্ডে মৃদু কাঁপুনি দিয়ে শব্দের বুননে নির্মিত হয় কবিতা। এখানে পরিষ্কার যে, রিফাত চৌধুরী তার জীবন-অভিজ্ঞতাকেই আসলে কবিতায় মূর্ত করেন। যে অভিজ্ঞতা তার চারপাশের মানুষজনেও অভিজ্ঞতা। যাপিত-জীবনের নানা বাঁক বদলের অভিজ্ঞান।
রিফাত চৌধুরীর বেশির ভাগ কবিতা বর্ণনাধর্মী। অনেকটা আমাদের কথা বলার ভঙ্গির মতো। ছোট ছোট বাক্য। আমরা যেমন এক-একটি বাক্য এক নিশ্বাসে বলি, তেমনই রিফাতের কবিতার এক-একটি বাক্য এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। এরপর ওইসব বাক্যের সম্প্রসারণ ঘটে পাঠকের অন্তর্জগতে। দীর্ঘ সময় পাঠককে তা আবিষ্ট করে রাখে। ‘ব্রাইট ফর্ম’ কবিতাটি পড়া যাক:
আমি
এই যে আমি
একটা কবিতা লিখব
সত্যিই লিখব কবিতা।
সেই কবিতায় থাকবে না কোনো
ভাব-ভাষা-ছন্দ-অর্থ।
থাকবে শুধু শাদা পাতা।
ওটাই কবিতা।
একটা নতুন ধরনের কবিতা,
যা এ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন ভাবেনি।
একটা নতুন ফর্ম।
ব্রাইট ফর্ম।
বয়েস কম।
এই আমার কবিতা—
যাতে ভাব নেই, ভাষা নেই, ছন্দ নেই, অর্থ নেই,
চিহ্ন নেই, সংকেত নেই, প্রতীক নেই।
আছে শুধু শাদা পাতা।
নিজের কবিতার রূপ-বৈশিষ্ট্য পাঠকে বোঝাতে গিয়েই যেন রিফাত চৌধুরী এই কবিতাটি লিখেছিলেন। বয়েস কম তরুণ কবিদের মতো নতুন কোনো ফর্মে কবিতা লিখতে চাওয়ার ঝোঁক রিফাত চৌধুরীর। নিজের বয়েস কম বলে দাবি করলেও রিফাতের কবিসত্তা যে প্রাজ্ঞ, তার পরিচয় আমরা পাই তার নতুন কবিতার পরিচিতিতে। নতুন কবিতায় কিছুই থাকবে না। থাকবে কেবল শাদা পাতা। বিষয়টি সাদামাটা হলেও শাদা পাতার ধু-ধু শূন্যতায় কত কিছুই যে লুকিয়ে থাকতে পারে, তা রিফাতের মতো কবিতার মনোযোগী যে কোনো পাঠকই জানেন। শাদা পাতাকেই কবিতা হিসেবে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার খায়েশ থাকলেও রিফাত তা কিন্তু করেন না। অবশ্য সেরকমটা করাও সম্ভব নয়। আর তাই হয়তো তিনি ছোট ছোট বাক্যে সহজ শব্দের ও ভাবের অভিব্যক্তি দিয়ে ভরে তোলেন শাদা পাতা। সেই ভাব সংক্রমিত হয় পাঠকের ভেতর। গভীর থেকে গভীরতম নির্জনতায় ডুবে যেতে যেতে পাঠক অনুভব করেন জীবনের ক্লেদ-কুসুম।
আমি যেন ফুটপাথের কিনারায় ফেলে দেওয়া আইসক্রিমের কাপ।
তাতে একটু আইসক্রিম লেগে আছে।
কোনো ভিখারি আঙুল দিয়ে তুলে এনে চেটে চেটে খাচ্ছে।
নিজেকে কতটা ফতুর ভাবলে মানুষ আইসক্রিমের কাপের সাথে তুলনা করতে পারে! আমরা প্রত্যেকেই আসলে ফুটপাথের কিনারে ফেলে দেওয়া আইসক্রিমের কাপ। যতই আমাদের বিত্ত-বৈভব থাক, আমরা আসলে আইসক্রিমের কাপ। বৈভবের চাকচিক্যে সেই সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু নিজের ভেতরের গহন নির্জনে ডুব দিয়ে নিজের দিকে তাকালে আমাদের চোখ করুণ হয়ে আসবে। দীনহীন মানুষের চেয়েও কত যে গরিব আমরা, সেই সত্য উদ্ঘাটন হবে। আসলে আমাদের গোটা জীবনটাই নিজেকে ভুলে থাকার জাকজমকপূর্ণ আয়োজন। জীবনের উপরিভাগে ভাসা-ভাসা জীবন কাটিয়ে আমরা ভাবছি, এই তো জীবন। কিন্তু জীবনের গভীরে ঢুকে রক্ত-মাংসের জীবনকে আমরা কেউই সেইভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। অবশ্য এই সংকট সবচেয়ে বেশি সমাজের ওপর তলার মানুষদের। কেননা, যার অবস্থান সমাজের যত নিচু তলায় সে তত বেশি ওপরের তলা দেখতে পায়। নিঃস্ব-রিক্ত ওই মানুষটা নিজের অসহায়ত্ব তখন কার্যকরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। জীবন-উপলব্ধির ক্ষেত্রে ধনী-গরিবের এই যে পার্থক্য, সেটা রিফাত চৌধুরীর অনেক কবিতাতেই আমরা দেখতে পাই। এই হিসেবে তাকে সাম্যবাদী ধারার কবি হিসেবে দেখলেও দেখা যেতে পারে। কিন্তু রিফাত চৌধুরী নিজেকে হয়তো সেইভাবে পরিচিত করতে চান না। তিনি জীবনকে দ্যাখেন জীবনেরই গভীর উপলব্ধি থেকে। গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিলে যেমন বেরিয়ে পড়ে দগদগে ঘা, একইভাবে রিফাতের কবিতার ওপরের ছাল তুলে নিলে বেরিয়ে পড়ে জীবনের দগদগে ঘা। দেহের যন্ত্রণার মতোই জীবনেও যন্ত্রণা আছে। রিফাতের কবিতা তাই জীবন-যন্ত্রণার শৈল্পিক উপলব্ধি। আশির দশকে বাংলা কবিতায় রিফাতের মতো জীবনকে আর কোনো কবি এভাবে উপলব্ধি করেননি। রিফাতের কাছে জীবনটাই একটা যন্ত্রণাকাতর কবিতা। যা বারবার আমাদের পাঠ করে যেতে হয়। যেন এটাই মানুষ কিংবা পাঠক হিসেবে আমাদের অনিবার্য নিয়তি।



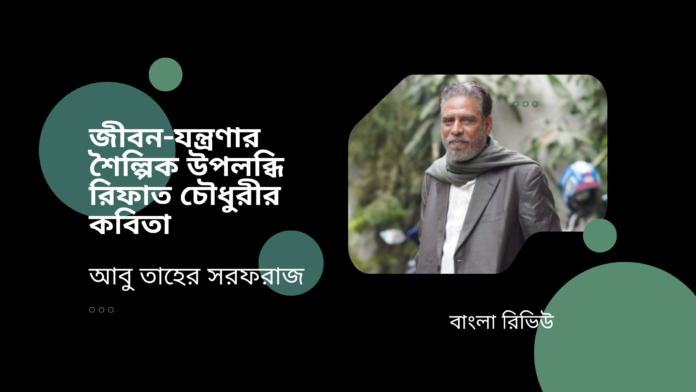
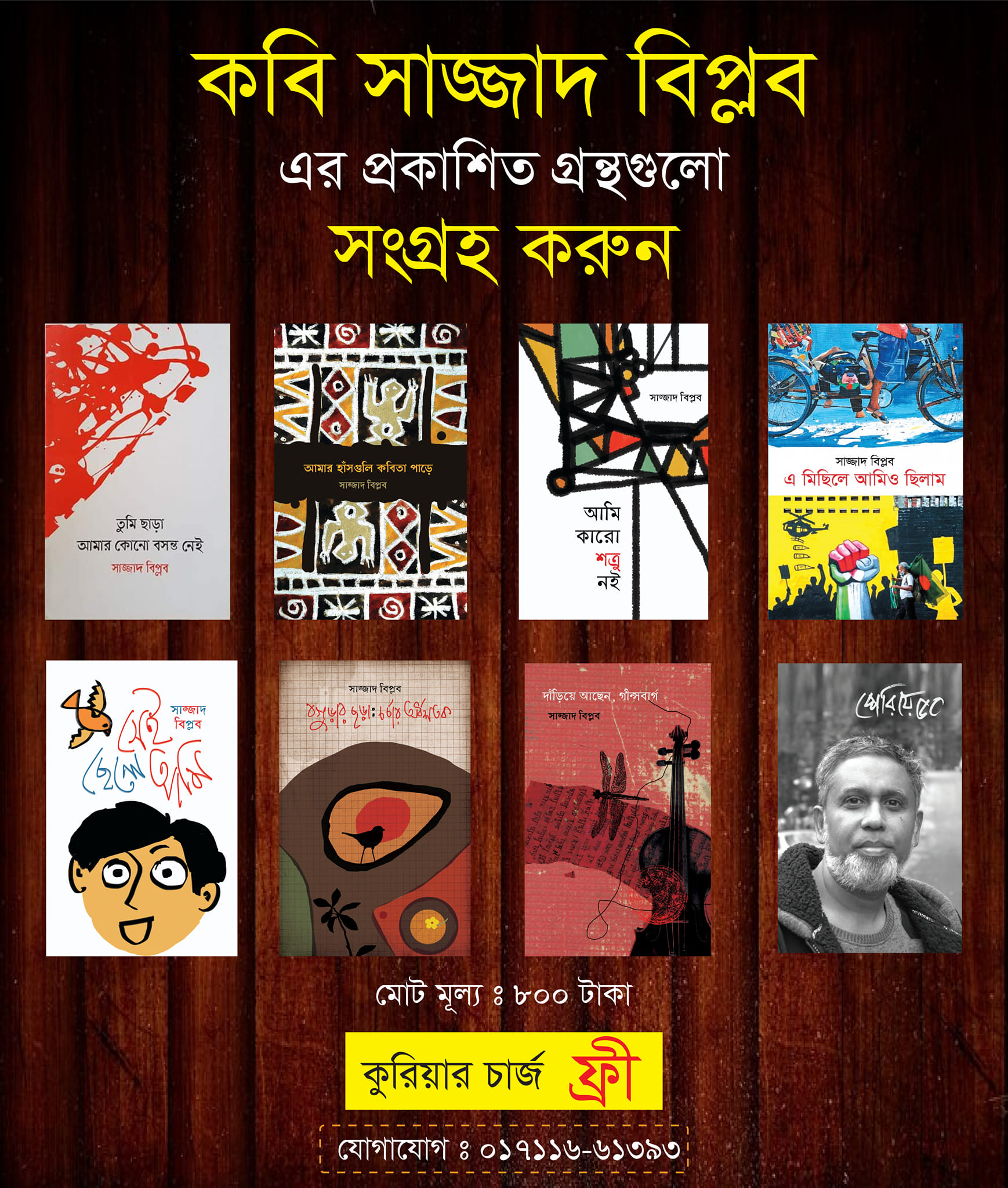
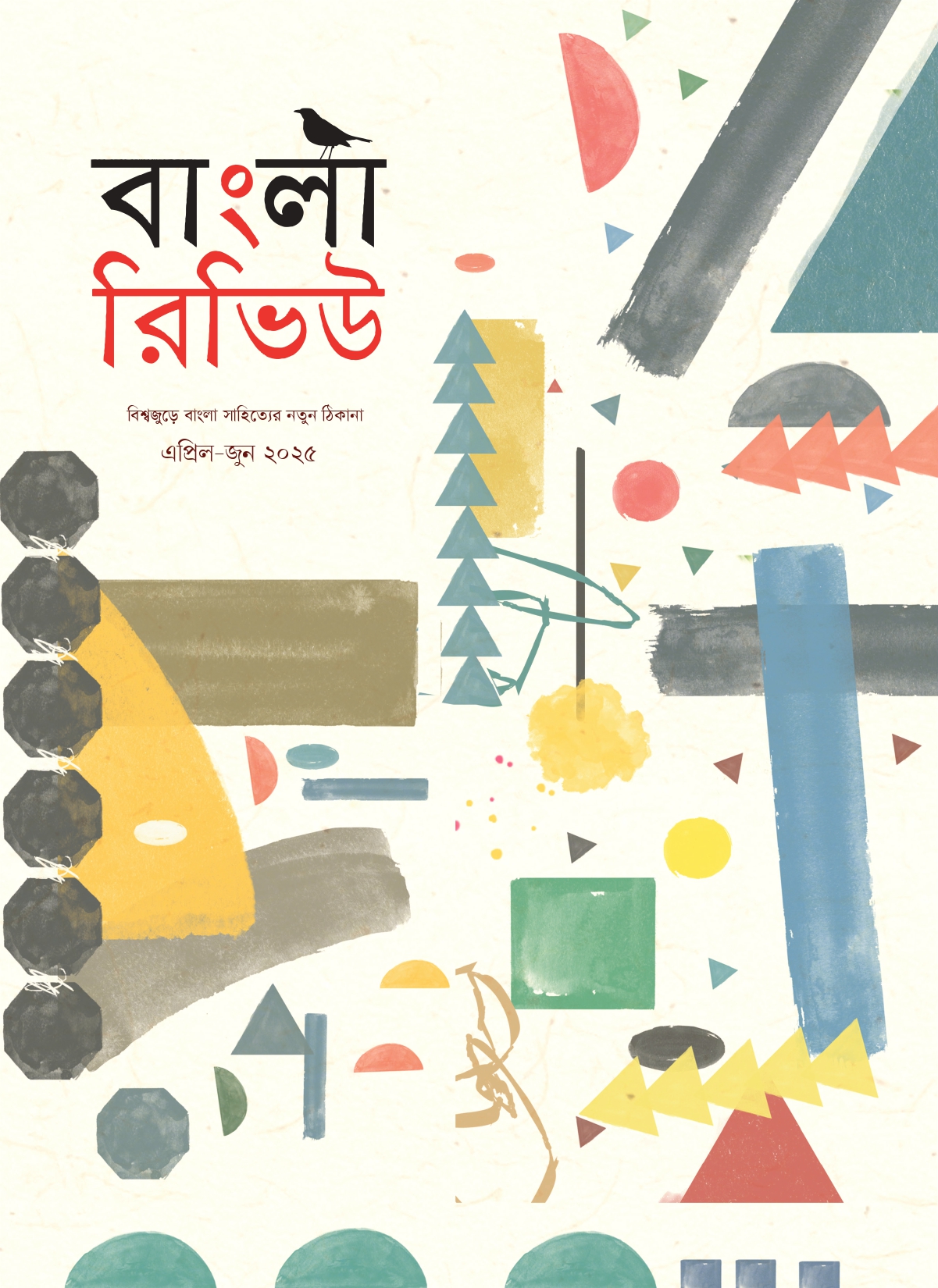


অসাধারণ বিশ্লেষণ।