ফরহাদ মজহার
আপনি কি জানেন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান নি, পেয়েছেন নিজের কবিতা নিজে ইংরেজিতে অনুবাদ করবার জন্য, নোবেল কমিটি যাকে বলেছে “… a part of the literature of the West”। অর্থাৎ সেই অনুবাদ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্তর্গত, বাংলা সাহিত্যের নয়।
নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথের পূজা-অর্চনা করতে করতে পশ্চিম বাংলার শিল্পসাহিত্য স্রেফ ক্যারিকেচারে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মজা আছে, অবশ্যই, কিন্তু সর্বসাকুল্যে ঐ এক রবীন্দ্রনাথ! শুধু তাঁর মাথাতেই জীবনদেবতার মুকুট। তাঁকে ঈশ্বর বানাতে গিয়ে পশ্চিম বাংলা বাংলা ভাষায় রচিত অন্যান্য যেসকল সাহিত্য ও শক্তি উপেক্ষা করেছে সেইসব কবিতা নয়। গদ্য। গদ্য উপেক্ষার ক্ষতি অপরিসীম। যেমন বিভূতিভূষণ, কমলকুমার কিম্বা অমিয়ভূষণদের আমরা প্রায় চিনি না বললেই চলে। কারন তাদের নিয়ে আমাদের কোন ভাবনাচিন্তা যোগ-বিয়োজন নাই, পর্যালোচনা নাই। আরো নাম যোগ করা যায়। করুন।
কবিতা বাঙালির অসুখের আরেক নাম। পদ্য ও কবিতার সর্দি কাটিয়ে উঠতে না পারা এবং সমাজকে সাহিত্য কথাটার ব্যাপকার্থ বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ার কুফল মনোগঠন ও রাজনীতিতেও ব্যাপক ভাবে পড়ে। বাংলা বিভক্ত। সাহিত্য একটা কারন। দ্বিতীয়ত পশ্চিম বাংলা কলোনিয়াল স্টুপিডিটি থেকে আজ অবধি মুক্ত হতে পারে নি। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ আবার মনে করে শিল্প-সাহিত্য, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি কোন কিছু নিয়ে না ভাবলেও ক্ষতি নাই। কারণ মোশাররফ করিম, জয়া আহসান এবং ভারতীয় দূতাবাস আছে।
শুনুন। ত্রিশের কেরানি সাহিত্যের সওদাগরি সত্ত্বেও জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কাব্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই যে বললাম, এতে অনেক রবীন্দ্রবিশারদ রেগে মেগে তেড়ে আসবেন। অন্য বিষয় বাদ দিন। ‘বুর্জোয়া’ বা ব্যক্তি কিম্বা স্বাধীন ব্যক্তি সত্তা কি জিনিস তার স্বাদ জীবাবনন্দ পেয়েছিলেন। কবিতায় যেমন, নিজের জীবনেও। আসলেই। বুর্জোয়া ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র কি জিনিস সেটা ‘বধু শুয়ে ছিল পাশে শিশুটিও ছিল” — কিন্তু জ্যোৎস্নায় সে কি এমন ভূত দেখল যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল এই প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা তুলতে পারার মধ্যে নিহিত রয়েছে। তার কোন কারন খুঁজতে যাওয়া বৃথা। হেগেল তাই দবি করেছিলেন মানুষ স্বাধীন, কারন আত্মহত্যা করবার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। নিজের জীব-জীবন নিজে হরণ করে মানুষ প্রমাণ করতে পারে জীবের জীবন আর মানুষের জীবন বা কর্তাসত্তা আলাদা।
মানুষ কেন আত্মহত্যা করে এই জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নাই। তাই আটবছর আগে একদিনে জীবনানন্দের সমাধান হচ্ছে এই জিজ্ঞাসা জারি থাক, কিন্তু উত্তর না দিয়ে বরং আরও দুই একটা ইঁদুর ধরতে পারার সাধনা উত্তম। জীবনানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন।
কিন্তু ঠাকুরের পক্ষে এই পোস্ট-কলোনিয়াল কন্ডিশান বুঝতে পারা ছিল অসম্ভব। ব্যক্তি বঙ্গে ঐতিহাসিক ভাবে হাজির, কিন্তু তার বিকাশের সকল সম্ভাবনা রহিত। তখন গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া নিজেকে স্বাধীন প্রমাণ করবার পথ কি?
মুশকিল হোল গল্প বা উপন্যাস বাদ দিলেও ঠাকুর সবাইকে তাঁর গান দ্বারা টেক্কা মেরে রেখেছেন। এটা অবনত মস্তকে মানি। তবে যেভাবে পূজারি ভাবভঙ্গী নিয়ে ঠাকুরকে গাওয়া হয়, সেটা বাজে লাগে। অন্যদিকে সর্দি ভাব না থাকলে ভিন্ন স্বাদের রুচি তৈরি হলে নজরুল রবিকে ছাড়িয়ে যান।
ভুল বলছি? আমি পদ্য শুনতে চাইলে রবীন্দ্রনাথের গানই বাছি, কিন্তু গান, কাব্য, দর্শন ও রাজনীতি একসঙ্গে শুনতে চাইলে নজরুলের দ্বারস্থ হই। কেন বললাম? নজির দাখিল করছি। দেখুন।
যদি মেটাফোর, দার্শনিকতা, শিব ও কৃষ্ণের ফারাক এবং বাঙালিয়ানার পক্ষে আর্গুমেন্ট শুনতে চাই তাহলে ‘অরুণকান্তি কেগো যোগী ভিখারি’ অসাধারণ। সম্ভবত এমন অসাধারণ কাব্যবস্তু সম্পন্ন গান খুঁজে পাওয়া সম্ভব না যা একই সঙ্গে দার্শনিক পর্যালোচনা এবং রাজনীতি। ‘রাসবিলাসিনী আমি আহিরীণী, শ্যামল কিশোর রূপ শুধু চিনি”! আমি বাংলার মেয়ে, আমি শুধু শ্যামল কিশোরকে চিনি, তুমি আবার কে গেরুয়া কাপড় পড়ে সন্যাসী হয়ে সামনে দাঁড়ালে!’ — বিবেকানন্দকে এভাবে কেউ সমালোচনা করেছে শুনি নি। বাংলার গোয়ালিনীদের দর্শন যার অপূর্ব আশ্রয়, আহীর ভৈরবী — সেখানে দাঁড়িয়ে বাপের ব্যাটা নজরুল ইসলাম এই সমালোচনা করতে পেরেছেন। দুর্দান্ত।
এই প্রকার রচনা নজরুল ছাড়া অন্য কোন কবির পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব।এই যে নজরুলের আহিরিণী ভাব এটা একই সঙ্গে বাংলা এবং রাজনীতি। সাফ প্রশ্ন হচ্ছে শ্যামল কিশোর ও রাধারাণীর বাংলায় গেরুয়া কি করে ঢুকে পড়ল? ভাবুন। এবং এবারের ভারতের নির্বাচনে এই প্রশ্নটির জবাব সন্ধান করুন। তাহলে নজরুলকে সর্ব ভারতীয় পরিসর থেকে বুঝবেন। হয়তো বাংলাদেশকেও। আমাদের লড়াইও ধর্মীয় জাতিবাদের বিরুদ্ধে। লড়াইয়ের মাঠে মিলের জায়গাটা মনে রাখবেন।
রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কি এরকম কাব্য, গান, দর্শনও রাজনীতি একসঙ্গে সম্ভব ছিল? না। কিন্তু তুলনা ঠিক না। জমিদার -পুত্র জানালা দিয়ে ‘রাঙা মাটির পথ’ দেখে অনুমানে যা লিখেছেন তাতেই আমাদের তৃপ্ত থাকা উচিত। তিনি বাংলার ভাবের জগতের তত্ত্বগত বিরোধের বিশেষ খবর রেখেছেন মনে হয় নি। জানতেনও না।
এই যখন অবস্থা তখন কলকাতা দেখুন। ঠাকুরের সঙ্গে ফকির লালন শাহের সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা সেটা ভেবে ভেবে তারা অস্থির। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় ছাড়া লালন নামক এতো বড় ঘটনা বাংলা সাহিত্যে কিভাবে ঘটল? তাদের ঘুম হারাম! এখন প্রমাণ করতেই হবে জমিদারের সঙ্গে ফকিরের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাই না?
না হয় নি। কিভাবে হবে? কলকাতা এখনও বাউল আর ফকিরের ফারাকই বোঝে না। বোটে কোন এক বাউলকে ধরে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রের কুৎসিৎ ড্রইংকে এখনও লালনের স্কেচ বলে দাবি করা হয়। আশ্চর্য!
নজরুল বাংলার খোঁজ খবর রাখতেন। কাব্যে ও গানে সেই সবের আকস্মিক ছটা আবিষ্কার করা সম্ভব। বাংলা রাধারাণী ও গোয়ালিনীদের দেশ। বাংলা কেন যোগী ভিখারি বেশ চায় না সেটা বিবেকানন্দদের বোঝাবার জন্য নজরুলের একটা গানই যথেষ্ট। এই কাব্য রচনা নজরুল ছাড়া অসম্ভব। তদুপরি বিবেকানন্দদের দশা দেখে রাধারাণীর বাংলাকে যিনি মহিমাময় করেন তিনিই আবার শাক্ত পদ বা ইসলামি গান রচনা করেছেন। লিখতে কুন্ঠা নাই, তিনি সমান পারঙ্গম। নজরুল বাংলাকে শত হাতে এক জায়গায় জড়ো রাখতে চেয়েছেন। তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি বাংলা তাঁকে দেয় নি। এর কাফফারা একদিন বাংলাকে গুনতে হবে।
রবীন্দ্রনাথ, তথাপি বাঙালির ‘সিদ্ধিদাতা গণেশ!! । যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন। এই হোলো মুদি দোকানের সুবিধা। কিন্তু মুশকিলটা ঘটে কোথায়? অধিকাংশ বাঙালি জানে না রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার পান নি। নোবেল তোহফা অনুবাদের জন্য। জ্বি। বাংলা সাহিত্যের জন্য বাঙালির কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নাই। এটা ট্রাজিক বাস্তবতা, যা অনেকের বুকে শেলের মতো বাজতে পারে, কিন্তু এটাই ছহি।
অথচ দেখুন, নোবেল প্রাইজ পাওয়াকে কলোনিয়াল হীনমন্য মিডল ক্লাস এতো বিশাল ব্যাপার ধরে নিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক নয়, বাঙালি আদতে নোবেল প্রাইজেরই পূজা করে। রবীন্দ্রনাথের জন্য খারাপ লাগে। তাকে আমরা ঠিক ভাবে ভালবাসতে পারলাম না। তার পুরস্কারকে বৃহৎ ব্যাপার ধরে নিয়েছি।
শালার কলোনিয়াল ময়লা থেকে পয়দা হওয়া জীব সকল! ইহারা জানে না কি করিতেছে! হায় আল্লাহ এদের মাফ করে দিও।



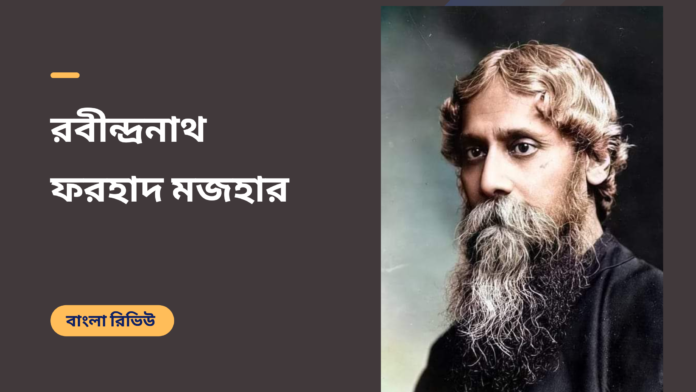
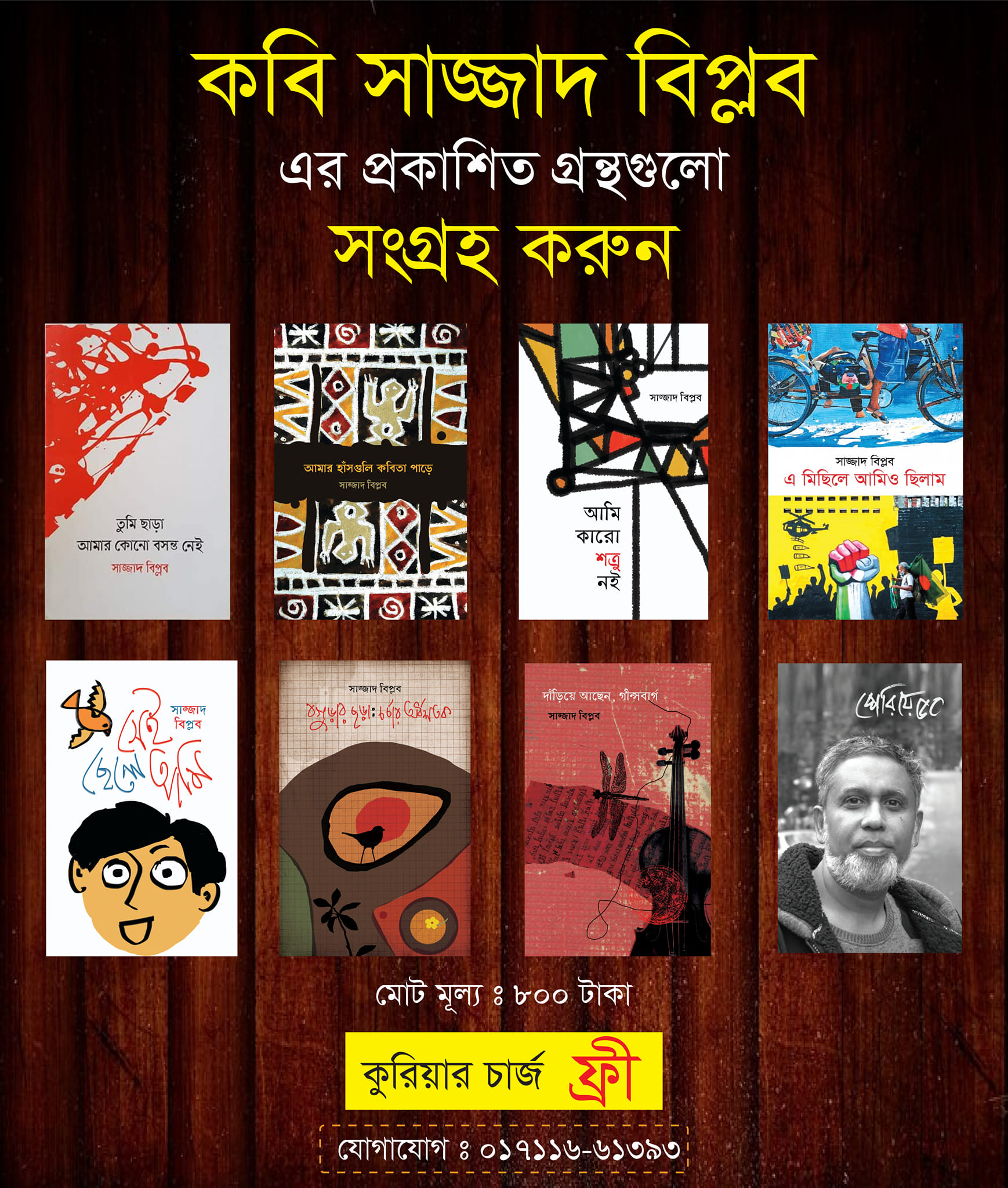


খুব ভালো লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথকে এভাবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করা যায় তা আপনি জানিয়ে দিয়েছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।
চমৎকার একটা বিশ্লেষণ। পক্ষে বিপক্ষে মত/কথা থাকতে পারে কিন্তু এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে চিন্তা করার একটি বিশাল দরোজা খুলে দেয়।
ফরহাদ মজহারের আলোচনা বরাবরই মনোযোগ দাবি করে।