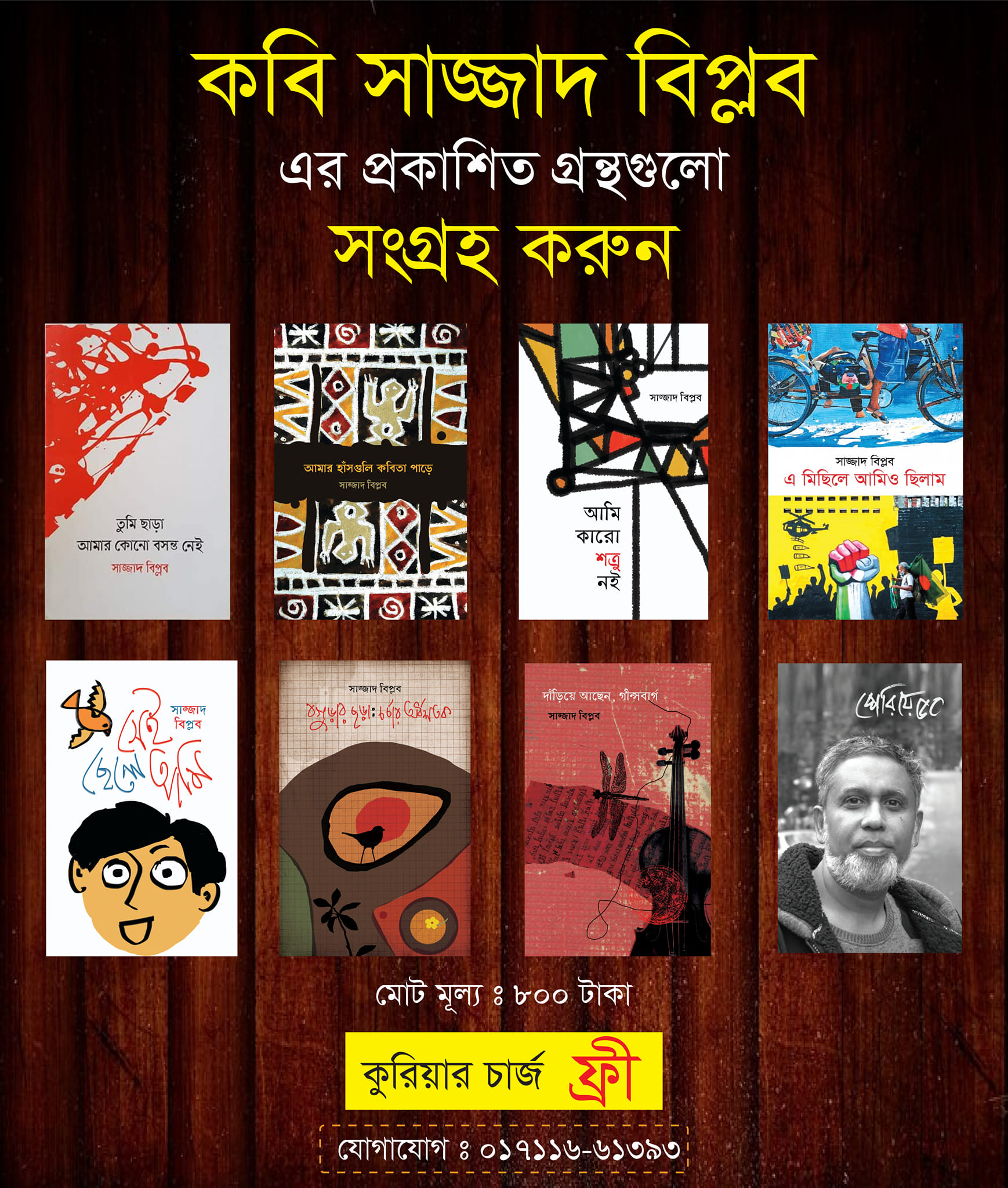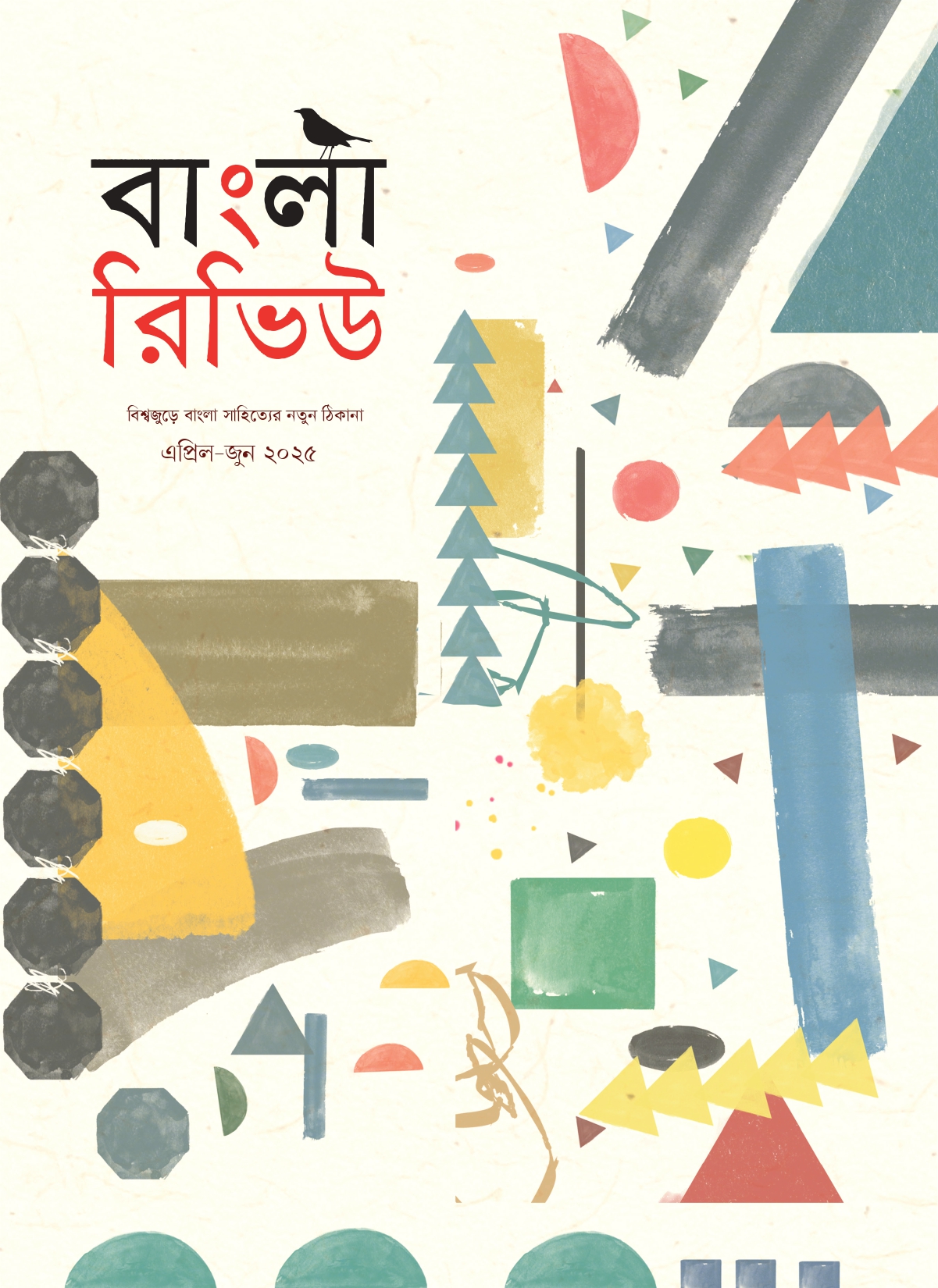তৈমুর খান
৩
মারের দাগ রয়ে গেল পিঠে
গ্রামের বিদ্যালয়টির নাম দাদপুর বাতাসপুর জুনিয়র হাই স্কুল। ১৯৭৮ সালে এখানেই পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হই। ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা বিশাল বটগাছ সংলগ্ন এই স্কুলটি। আলে আলে ঘাসের উপর দিয়ে পা ফেলে হেঁটে যেতে হয়। স্কুলের দরজা না খোলা পর্যন্ত বট গাছের শিকড়ে গিয়ে বসে থাকি। গাছের ডালে বহু রকম পাখি বটফল খায় আর অনবরত কিচিরমিচির শব্দ করে ডাকতে থাকে। সেদিকেই উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। ইতিহাস ভূগোল অথবা বিজ্ঞানের পড়া মুখস্থ করতে হয়। কখনো কখনো সেসব পড়াগুলিও একবার চোখ বুলিয়ে নিই। বই-খাতা গুছিয়ে আমরা হাতে করে নিয়ে যেতাম। না, সে সময় বিদ্যালয়ে ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার চল ছিল না। জোর একটা পলিথিনের প্যাকেট। আমার কাছে সেটাও ছিল না। একটু পরেই ঢং ঢং শব্দে ঘন্টা বেজে উঠলে প্রার্থনার লাইনে গিয়ে দাঁড়াতাম। শুরু হতো বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন।
এই বিদ্যালয়ে আসার দু’বছর আগেই কাজী নজরুল ইসলাম দেহত্যাগ করেছেন। তাঁকে নিয়ে লেখা একটা ছোট্ট জীবনী সেবছরই পঞ্চম শ্রেণিতে দ্রুতপঠন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্লাসের বই না পড়ে ওই বইটির প্রতিই আমি বেশি মনোযোগী হয়ে উঠি। অভাবগ্রস্ত জীবনে নজরুলের বাল্যকাল আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর লেটো দলে গান করা, রুটির দোকানে কাজ করা এবং কিছুদিন রান্নার কাজে যোগ দেওয়ার সংবাদটিই বারবার আমি পড়তে থাকি। ‘দাও মোরে গৃহ ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে’ এই লক্ষ্যেই যে সাহস নিয়ে নজরুল গৃহত্যাগ করেছিলেন—সেই ইচ্ছার জন্ম আমার মধ্যেও দেখা দেয়। বইটিতে মাঝে মাঝে নজরুলের কবিতার উদ্ধৃতিগুলি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। তখন থেকেই খিদেকে উপেক্ষা করতে শিখি। নিজের অজান্তেই মাঝে মাঝে বলতে থাকি:
“হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান কন্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ’ল তরবার!
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি’ সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি’ কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!”
এত জোরালো, এত সাহসী, এত তীব্র, এত প্রাচুর্য সেদিন আর কোনো কবি আমাকে দিতে পারেননি। একটাই জামা, হাফপ্যান্ট কত জায়গায় রিফু করা, খালি পা, রুক্ষ শুষ্ক চেহারা তবু যেন প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা। কবিতা যেন এক মন্ত্রের মতো, এক ধারালো অস্ত্রের মতো, শক্তিবর্ধক কোনো খাবারের মতো আমার মনন জগৎকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। ‘মনোয়ারা’ উপন্যাসের নায়কটির মতো আমিও যেন অকূল পাথারে ভেসে চলেছি। কখনো বাবার বইয়ের বিনোদের কোড়াপাখি ধরার গল্পও আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। যে বিনোদ পাখি ধরতে গিয়ে সাপের ছোবলে মৃত্যুবরণ করে। বাড়িতে তার বিধবা মা এবং বউ সে খবরও জানতে পারে না। আবার কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ‘আদুরী’ কবিতাটিও মনে দাগ কাটে। অজয় নদের বন্যায় হাঁসগুলি ভেসে গেলে আদুরী ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলিকে রক্ষা করতে চায়।পানির তোড়ে কিন্তু সেও ভেসে যায়। পরদিন পাওয়া যায় তার লাশ। বাবার মুখে যেমন এই কবিতাগুলি শুনতাম তেমনি পুরনো বইটিতেও তা বারবার পড়তাম। আর পড়তে পড়তেই তাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ করে নিয়েছিলাম। হৃদয় কেঁদে উঠত। অদ্ভুত বিক্রিয়ায় এক সংকোচন হতো। তাদের নিয়ে ভাবতে থাকতাম। শীতকাল এলে স্কুল যাবার পথে জমিতে অজস্র সরষে ফুল ফুটতে দেখতাম। আর সেসব নিয়েই খাতার এক এক পৃষ্ঠা ভরে যেত কবিতায়। সেদিনের সেসব কি কবিতা ছিল?
“সরিষা ফুলের হলুদ গানে
আমায় কেন এত টানে?
দেখতে দেখতে পথ হাঁটি ভাই
জানি নাকো তাহার মানে।”
কখনো বটফল নিয়েও দু-চার লাইন লিখে ফেলতাম:
“বটফল যদি খাবার হত
আমিও হতাম পাখি
প্রাণটা মোর জুড়িয়ে যেত
না খেয়ে কি আর থাকি?”
কখনো শোষক অত্যাচারী সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করেও লিখেছিলাম:
“গরিবদের ঘৃণা করে কী সুখ তুমি পাও
মানুষ তো সবাই সমান জানো না কি তাও?”
অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে পড়েছিলাম। মুদির দোকানে একটি ছেঁড়াখোঁড়া বাংলা অভিধান পুরনো খাতা বদল করে নিয়ে এসেছিলাম। সেখান থেকে কিছু কিছু শব্দ শিখতাম রোজ। আর সেসব দিয়েই কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। যেমন—
“শিবার মতো মানুষগুলি
দিবায় মাখে মুখে কালি”
‘শিবা’ আর ‘দিবা’ আমি প্রথম শিখেছিলাম। এর আগে অবশ্য আমার বাবা বেশ কিছু শব্দ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। যেগুলো উচ্চারণেও কঠিন ছিল এবং বানানও বেশ শক্ত। কুজ্ঝটিকা, ভৌগোলিক, পৌরোহিত্য, সাঙ্গোপাঙ্গ, রাক্ষস, শাশ্বত, বজ্রপাত, নির্ঘোষ, ইতস্তত, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি আরও বহু শব্দ।
একবার স্কুল যাবার পথে এক কৃষকের কয়েক ঝাড় ছোলা তুলে খেতে খেতে যাচ্ছিলাম। সেদিন আমি একা নয়, সঙ্গের ছেলেরাও এই কাজ করেছিল। বহু দূর থেকে সেই কৃষক ছোলা তোলা দেখে ফেলেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ছুটে এসে গোরু তাড়ানো হালের পাঁচন দিয়ে আমাদের বেদম প্রহার করেছিলেন। সারাপিঠে প্রহারের দাগ বসে গেছিল। সেদিন বাড়ি ফিরে গায়ে থাকা নীল রঙের জামাটি আর খুলতে পারিনি। অনেক পরে এই স্মৃতি মনে রেখেই লিখেছিলাম একটি গল্প ‘নীল জামা’ নামে। আসলে নীল রঙের জামাটি গায়ে ছিল বলেই প্রহারের রক্তাক্ত দাগগুলি কেউ আর দেখতে পায়নি।
আমাদের পড়াকালীন সময়ে এই বিদ্যালয়টির খুব বেশি বয়স ছিল না। সেইসময়ের শিক্ষিত যুবকেরাই বিদ্যালয়টি নির্মাণ করে শিক্ষার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য সরকারি অনুমোদনও কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। তখন শিক্ষা দানের মানও যথেষ্ট উন্নত ছিল না। শুধু ইতিহাসের শিক্ষক আব্দুল হামিদ স্যার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর কাছেই ফেভারিট হয়ে উঠেছিলেন। একাধারে ইংরেজি বাংলা ও ইতিহাসের পাঠ দান করতেন। মাঝে মাঝে বিজ্ঞান বিভাগও না-পছন্দ ছিল না। গল্পের আকারে ইতিহাসের বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপনা করতেন যে আমাদের আর বই পড়ার দরকার হতো না। তেমনি ইংরেজিতে ছোট ছোট বাক্য গঠন করে কিভাবে বড়লেখাও সম্ভব তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় বাংলা পাঠ্য বই ছিল ‘সাহিত্য চয়ন’। অষ্টম শ্রেণিতে এসে প্রথম ‘মেঘনাদবধ’-এর স্বাদ পাই। রাবণের রাজসভায় চিত্রাঙ্গদার আগমন এবং তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর অভিযোগ জানানোর বর্ণনাটিই পড়তে পড়তে মধুসূদন দত্তও মনের মধ্যে বিরাট স্থান দখল করে নেন।
চিত্রাঙ্গদার বর্ণনায় মধুসূদন লিখেছিলেন:
“হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বনসুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির—
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,”
কী অপূর্ব বর্ণনা, চমৎকার উপমা, বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের প্রয়োগ পড়তে পড়তে মনকে দৃঢ় করে তোলে। এক অলৌকিক শক্তির স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকি। তখন থেকেই মেঘনাদবধ পড়ার কৌতূহল সৃষ্টি হয়। যে কয়েক পংক্তি মনে থাকে তা সর্বদা আপন মনেই আবৃত্তি করতে থাকি। আমার এই আপন মনে অনুচ্চ কণ্ঠস্বর কেউ কেউ লক্ষ করে আমাকে পাগল আখ্যা দিতে থাকে। সেসব কথা কানেও নিই না। যেকোনো বই হাতে পেলে যেমন পড়ার ঝোঁক বেড়ে যায়, তেমনি গুরুগম্ভীর কবিতাগুলিও নাটকের সংলাপের মতো মুখস্থ করে ফেলি। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আড়াই টাকা পরীক্ষার ফি একবার দিতে পারছিলাম না। বাড়ি এসে টাকার জন্য ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে কেঁদে চোখ দুটোকে ফুলিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন আমার এক বিধবা পিসি বহু কষ্টে যোগাড় করা তাঁর টাকা থেকে আড়াই টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় পরীক্ষার ফি এর জন্য আমাকে আর কান্নাকাটি করতে হয়নি। কেননা তখন আমি মজুর খাটতে শিখে গেছিলাম। মাত্র তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা মজুরি ছিল। কখনো মাটিকাটা তো কখনো ধানের বীজ তোলা। কয়েকদিন স্কুল কামাই করলেই সহজেই তার উপায় করতে পারতাম। তখন আমরা দুঃখ-কষ্ট বুঝতে শিখে গেছি। না খেতে পেয়ে কান্না করে রাগের মাথায় মায়ের হাতে চ্যালা কাঠের মার আর খেতে হতো না। অবশ্য সেসব মারের দাগ এখনো পিঠে রয়ে গেছে।