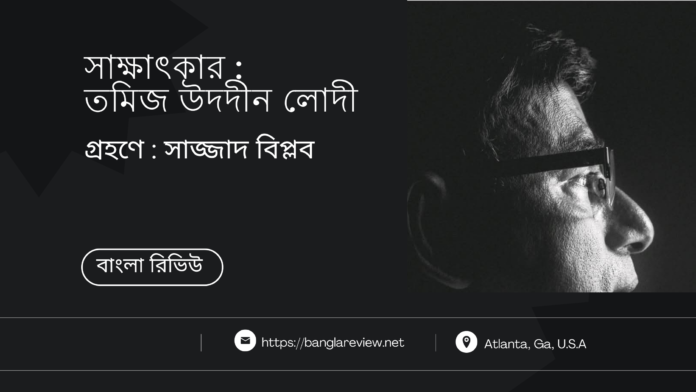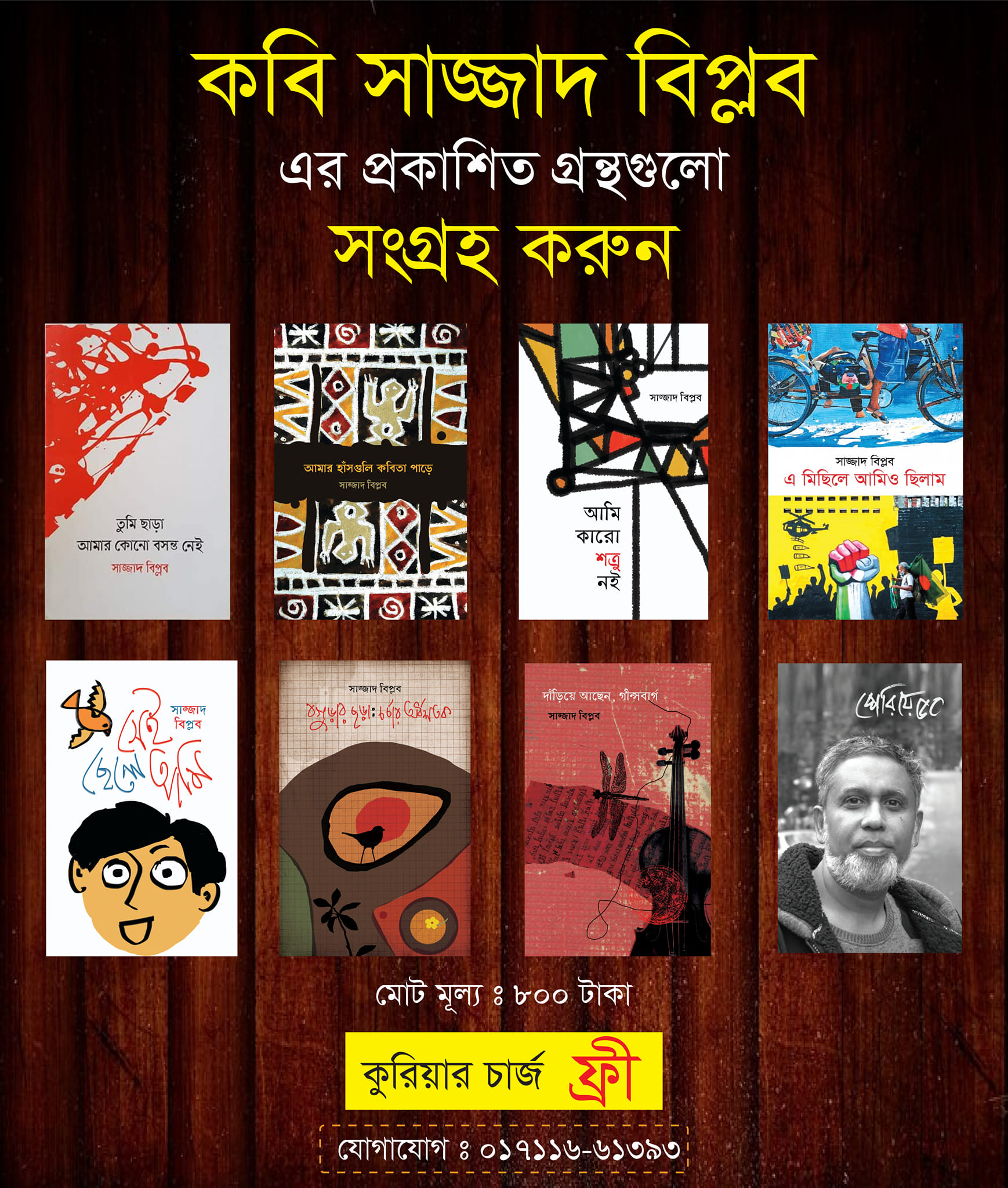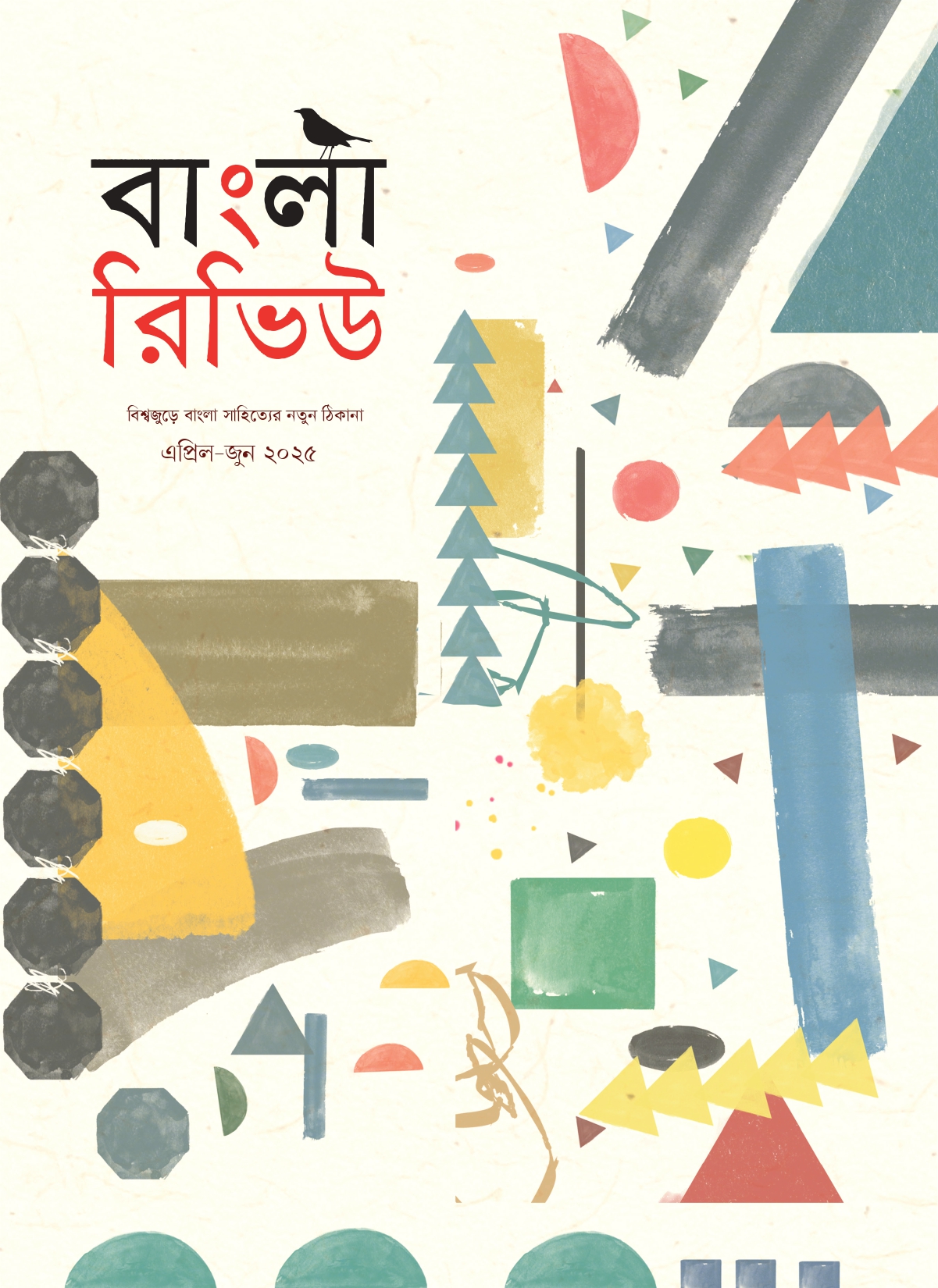সাক্ষাৎকার : তমিজ উদদীন লোদী
বাংলা রিভিউ : জীবন কি? আপনার বর্তমান জীবন, অবস্থান– যা হতে চেয়েছিলেন বা যা হয়েছেন–এসব নিয়ে কোন আক্ষেপ, অনুশোচনা বা গর্ব হয়?
তমিজ উদদীন লোদী : জীবনের একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা আছে। এটি হল ‘ জীবন বা প্রাণ এমন একটি অবস্থা , যা একটি জীবকে জড় পদার্থ ( প্রাণহীন ) ও মৃত অবস্থা থেকে পৃথক করে ‘ । কিন্তু জীবন এখানেই সীমাবদ্ধ নয় , জীবন সুনির্দিষ্ট কিছু সময়ের সমষ্টি ।
সে জন্য জীবন ফুরিয়ে যায় । ফুরানো ও সুনির্দিষ্ট এ জীবনকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করার নামই জীবন । জীবনকে আমি এভাবেই দেখি । শেষেরটাই আগে বলি , গর্ব করার আসলে কিছু নেই , গর্ব বিষয়টাই একটি নেতিবাচক অভিব্যক্তি , যা মানুষকে মানুষ থেকে আলাদা করে দেয় । জীবনের সব অবস্থাকেই আমি সন্তুষ্টির সাথে মেনে নেই , বর্তমানকেও আমি মেনে নিয়েছি । না কোন আক্ষেপ নেই , অনুশোচনাও নেই ।
বাংলা রিভিউ : আপনার শৈশব-কৈশোর কোথায় কেটেছে? কীভাবে কেটেছে? কোন অব্যক্ত কথা বা স্মৃতি কি মনে পড়ে? তাড়িত করে?
তমিজ উদদীন লোদী : আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে গ্রামে । সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে । সরল অথচ বৈচিত্র্যময় , প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধের একটা গাঢ় বিশেষত্ব ছিল । ছিল অফুরন্ত আনন্দকে সুন্দরভাবে সংহরণ করার স্বতঃস্ফূর্ততা । গাছপালার , তৃণের , শস্যের , পাখিদের মুখরতা ,উড্ডয়ন । জলচর পাখিদের বাসা বুনন , নানা পদ্মের ,শাপলার বিভা , গাছপালার একধরনের নিশ্চেতন করা গন্ধ আমাকে আপ্লুত করে রাখতো । এ সময় আমার জীবনে ঘটে সবচেয়ে বিয়োগান্তক ঘটনা , আমার আব্বার হঠাৎ মৃত্যু । যা এখনো আমাকে তাড়িত করে ।
বাংলা রিভিউ : সাহিত্যে এলেন কেন? কীভাবে এলেন? অর্থাৎ শুরুটা কীভাবে? কোথায়?
তমিজ উদদীন লোদী : তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে দেশ । ১৯৭২ সাল , আমি তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র । আমাদের বাড়ির পুকুরপাড়ে পোস্ট অফিস । নানা পত্রিকা আসতো ডাকযোগে । ঢাকার কাগজগুলো আসতো এক বা দুদিন পর । সিলেটের প্রাচীন সাপ্তাহিক কাগজ যুগভেরী আসতো নিয়মিত । এগুলো খুলে পড়ার একটি সুযোগ ও আনন্দ পেয়ে বসে আমাকে । ওইসব কাগজে নিয়মিত দুটি পাতা ছাপা হতো , একটি বড়দের সাহিত্য পাতা , অন্যটি শিশুদের জন্য । তখন বয়সজনিত কারণে শিশুদের পাতার প্রতিই অধিক মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছিল । ছড়া এবং ছোটদের গল্প নিয়মিত পড়া হতো । সৃজন সম্ভাবনার কোন বিষয় তখনো দানা বাঁধেনি । কিন্তু হঠাৎ একদিন রাতের বেলা কোনোরূপ ছন্দ না জেনেই অন্তমিল দিয়ে কয়েকটি ছড়া লিখে ফেললাম । এবং সাহস করে এগুলো পাঠিয়ে দিলাম সাপ্তাহিক যুগভেরিতে । এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে কয়েক সপ্তাহ পর আমার একটি ছড়া ছাপা হয়ে গেল কাগজটিতে । এটা অনেকটা ঝড়ে বক মরার মতো । তখনকার ছোটদের পাতার সম্পাদক বিশিষ্ট ছড়াকার মাহমুদ হক ঐ একটি ছড়াতেই হয়তো ছন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন । অবশ্য ছন্দ বিষয়টি জেনেছিলাম আরও অনেক পরে । এর মধ্যে দুটি ছোটদের উপযোগী গল্প লিখে ফেলেছিলাম বিপুল উৎসাহে । এ দুটোও পাঠিয়েছিলাম যুগভেরীতে । তার একটি গল্প পরের সপ্তাহেই ছাপা হয়ে গেল যুগভেরীর ছোটদের পাতায় ।
এভাবেই শুরু আমার সাহিত্যযাত্রার ।
বাংলা রিভিউ : বাংলা ভাষার তথা বাংলাদেশের প্রধান কবিবৃন্দ যেমন : ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, শহীদ কাদরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবিদ আজাদ প্রমুখ– তাদের সাহিত্যকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? আর কার-কার সঙ্গে আপনার সখ্যতা বা বন্ধুত্ব বা ঘনিষ্ঠযোগাযোগ গড়ে উঠেছিলো বা আছে? তাদের সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা বা তাদের সাহিত্য নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।
তমিজ উদদীন লোদী : সাতচল্লিশের দেশভাগের পর চল্লিশের প্রধান কবিরা , যেমন ফররুখ আহমদ , আহসান হাবীব , সৈয়দ আলী আহসান , আবুল হোসেনরা আমাদের প্রধান প্রতিকৃতি। আমরা জানি সাহিত্যের ইতিহাসও নিজস্ব পুরাণকে নিজের মধ্যে সুন্দরভাবে সংহরণ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে , গ্রীক কাব্যগুলি তার প্রমাণ । ফররুখ এরাবিয়ান নাইটস-এর চরিত্র সিন্দাবাদ কিংবা আরবি পুরানের হাতেম তাঈকে উপজীব্য করে ইসলামী রেনেসাঁকে উজ্জীবিত করেছেন , সংহত করেছেন । তাঁকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়নি আমার । আহসান হাবীব এবং সৈয়দ আলী আহসানের সাথে আমার একাধিকবার দেখা ও কথা বলার সুযোগ হয়েছিল , আবুল হোসেনের সাথে আমার একবারই দেখা হয়েছিল । আহসান হাবীব এবংসৈয়দ আলী আহসান এ দুজনের কবিতার আমি মুগ্ধ পাঠক । গভীর জীবনবোধ, আত্মমগ্নতা , স্বদেশলগ্নতায় স্থিত আহসান হাবীব তুলে ধরেছেন সমকালীন সময়ের চালচিত্র, সমাজ ও জীবনের বাস্তবতা , কাব্য নিরীক্ষা , দার্শনিকতা ঋদ্ধ নতুন বোধ ও শিল্পরীতি । সৈয়দ আলী আহসান আধুনিক গদ্য কবিতার সার্থক রূপকার , প্রকৃতির বা নিসর্গের রূপকে তিনি অনন্য শব্দচয়নে উপস্থাপন করেছেন যা তার নিজস্বতায় ভাস্বর । উপমা ও শব্দ ব্যবহারে নতুনত্ব তাঁকে সম্পূর্ণ আলাদা ও অনন্য করে তুলেছে । তাঁর বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ । শামসুর রাহমান , আল মাহমুদ , ফজল শাহাবুদ্দীন , শহীদ কাদরী ,দিলওয়ার, ওমর আলী–পঞ্চাশের এইসব কবিদের সাথে আমার দেখা হবার সৌভাগ্য হয়েছিল । এদের মধ্যে আল মাহমুদ , শহীদ কাদরী , ফজল শাহাবুদ্দীন , দিলওয়ারের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে কেটেছে আমার অনেক দীর্ঘ সময় । তাঁদের স্নেহের আঁচ এসে লাগে এখনো গায়ে। এদের সকলের কবিতাই আমাকে কমবেশি মুগ্ধ করেছে । কারো কারো কবিতার আমি ছিলাম নিমগ্ন পাঠক । মানান সৈয়দ এবং আবিদ আজাদের সাথে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । মান্নান সৈয়দ অত্যন্ত মেধাবী একজন কবি ছিলেন, তিনি সাহিত্যের প্রায় সব শাখায়ই সমান আগ্রহে বিচরণ করেছেন । বয়সের বাঁধাকে অতিক্রম করে আবিদ ভাইয়ের সাথে আমার অনেকটাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । তিনি তাঁর প্রকাশনা শিল্পতরু থেকে আমার একটি কাব্যগ্রন্থ ‘চাঁদভস্ম ‘ প্রকাশ করেছিলেন । আমার মতে তিনি পঞ্চাশ ও ষাটত্তোর কবিদের পর সবচেয়ে মেধাবী ও উল্লেখযোগ্য কবি । যার কবিতার বৈচিত্র্য একজন বড় কবিকে চিহ্নিত করে ।
বাংলা রিভিউ : আপনি একাধারে একজন কবি ও সাহিত্য বিশ্লেষক–অর্থাৎ বহুমাত্রিক। আপনার অভিজ্ঞতা ও বিচরণ ক্ষেত্র ব্যাপক ও বর্ণিল। বিচিত্র। এই সামগ্রিক সত্তাকে কিভাবে দেখেন? কিভাবে উপভোগ করেন?
তমিজ উদদীন লোদী : কবিতার পাশাপাশি আমি ছোটগল্প এবং দুএকটি উপন্যাস লিখেছি , তবে সাহিত্য বিশ্লেষক বলা যাবে না । যদিও কিছু প্রবন্ধ ও সমালোচনা আমি করেছি । কবিতা ও কথাসাহিত্যে আমি সমান স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছি । যখন গল্প লিখেছি , তা আনন্দের সাথেই করেছি । একই কথা কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ।
বাংলা রিভিউ : আদি বাংলা তথা চর্যাপদ থেকে আজ অবধি বাংলা সাহিত্য কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে–আপনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণে?
তমিজ উদদীন লোদী : বিশাল এই প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা মুশকিল । চর্যাপদ , বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া সিদ্ধাচার্য কবি- সাধকদের প্রতীক গ্রথিত গীতিকবিতায় জটিল যৌগিক ধর্মচিন্তার পরিচয়বাহক যে কবিতার যাত্রা তা নানা সূত্র , চিন্তা , পাশ্চাত্য প্রভাব প্রভাবিত হয়ে এ সময় পর্যন্ত এসেছে । মধ্যযুগের কবিতা যা সুরাশ্রিত ছিল তা থেকে কবিতাকে সরিয়ে এনে প্রথম ছন্দোমুক্তির দরজা খুলে দিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত । মূলত তিনিই প্রথম আধুনিক কবি । তারপর রবীন্দ্রনাথ , কাজী নজরুল ইসলাম , তিরিশের কবিরা । এবং বিগত দশকের চল্লিশ , পঞ্চাশ , ষাট , সত্তুর , আশি ও নব্বুই দশকের কবিরা নানা বাঁকবদলের চেষ্টায় অবিরত সচেষ্ট ছিলেন । তবে বিরল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সেরকম কোনো ডাইমেনশন তৈরি হয়নি । একটি স্থিতিশীল ধারাবাহিকতা লক্ষনীয় ছিল । এখনো একই ধারাবাহিকতা আছে বলেই মনে হয় ।
বাংলা রিভিউ : সাম্প্রতিক বাংলাদেশে, শিল্প-সাহিত্যচর্চায় কোন-কোন চ্যালেঞ্জ বা সুবিধা-অসুবিধা আছে বলে আপনার মনে হয়? কীভাবে এগুলি মোকাবিলা করেন?
তমিজ উদদীন লোদী : সাম্প্রতিক সময়ে শিল্পকর্মের অন্তঃশীল সূত্র আবিষ্কার করার আগ্রহে অনেকটাই ভাটা পড়েছে বলে মনে হয় । এক ধরনের হালকা উপপ্লবী মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠার প্রবণতা লক্ষণীয় । যে কারণে আমাদের সমালোচনা সাহিত্য ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে । বরং বলা চলে অনেকটাই ক্ষীয়মান । দৈনিক কাগজগুলোতে আজকাল আর আহসান হাবীব , সিকানদার আব জাফর , রুকনুজ্জামান খান , বেলাল চৌধুরী, আল মুজাহিদী , আবুল হাসনাত , রফিক আজাদ , হেলাল হাফিজ , ইউসুফ শরীফ , নাসির আহমেদ–এর মতো সিনিয়র কবিদের দেখা মেলে না । যারা কবিতা কিংবা লেখা সম্পাদনার যোগ্যতা রাখতেন । এখন কোটারি স্বার্থটা প্রবল হয়ে উঠেছে বলে শোনা যায় । তবে এখন আর দৈনিক , সাপ্তাহিক ইত্যাদি নির্ভর সাহিত্য নয় বলেই লেখালেখির পরিসর বিস্তৃত হয়েছে ।
বাংলা রিভিউ : আপনার প্রথম প্রকাশিত বই কোন টি? কবে প্রকাশিত হয়েছিলো? প্রথম বই প্রকাশের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি কেমন ছিলো?
তমিজ উদদীন লোদী : আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি হলো ‘কখনো নিঃসঙ্গ নই’ । বেরিয়েছিল ১৯৮৫ সালে । সম্পূর্ণ নিজের খরচেই বের করেছিলাম সেটি । প্রথম বই প্রকাশের অনুভূতি অনির্বচনীয় । বিষম এক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটেছিল সময় ।
বাংলা রিভিউ : সাহিত্যে আপনি কার উত্তরাধিকার বহন করেন?
তমিজ উদদীন লোদী : এককভাবে কারো উত্তরাধিকার বহন করছি বলে মনে হয় না । তবে নানা সময়ের নানা কবি ও তাদের কবিতা আমাকে নিয়ত আলোড়িত করেছে ।
বাংলা রিভিউ : এ যাবৎ সর্ব মোট আপনার কতটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে? এর মধ্যে কোনটি বা কোন-কোন কাজকে বা কোন বইকে আপনি আপনার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলে মনে করেন?
তমিজ উদদীন লোদী : এ পর্যন্ত আমার ১৫ টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । তার মধ্যে নয়টি কাব্যগ্রন্থ , তিনটি গল্পগ্রন্থ , একটি নির্বাচিত কবিতা , একটি নির্বাচিত গল্প এবং একটি অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে । সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ এমন যে তাকে পৃথক করা খুব মুশকিল । তবু ‘ অনিবার্য পিপাসার কাছে ‘ , ‘ আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা ‘ কাব্যগ্রন্থগুলো আমার অধিক ভালোলাগার । তাছাড়া আমার গল্পগ্রন্থগুলোর প্রতি আমার দুর্বলতা রয়েছে ।
বাংলা রিভিউ : সম্প্রতি প্রকাশিত আপনার নতুন বই সম্পর্কে বলুন।
তমিজ উদদীন লোদী : আমার সর্বশেষ বইটি বেরিয়েছে গত বছর অর্থাৎ ২০২৩- এর বইমেলায় । এটি কাব্যগ্রন্থ । ‘নার্সিসাস কিংবা প্লেটোনিক ‘ । নানা ধরনের কবিতা রয়েছে এতে । মোট ৬৭ টি কবিতা । আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন ।
বাংলা রিভিউ : আপনি নিজেকে কোন দশকের কবি-লেখক বলেন? কেন?
তমিজ উদদীন লোদী : আমার লেখালেখির শুরুটা হয়েছিল সত্তর দশকে , তা অনেকটাই অনিয়মিত ছিল । আশির দশক থেকে তা নিয়মিত হয়ে ওঠে । প্রথম বইটিও বেরোয় আশির দশকে । সে হিসেবে আমি আশির দশকের কবি হিসেবেই বিবেচিত ।
বাংলা রিভিউ : আপনার সমকাল নিয়ে বলুন।
তমিজ উদদীন লোদী : আমার সমকাল নানা দিক থেকেই উজ্জ্বল ছিল । এক ধরনের রহস্যময়তা ছিল । ছিল এজন্য যে আমরা একটি অদৃশ্যময়তার মধ্যে ছিলাম । কাগজে কলমে লিখে খামে ভরে লেখাটি পাঠাতাম বিভিন্ন কাগজে। লেখাটি বের হবার আগে কিছুতেই জানতে পারতাম না এটি ছাপা হবে কিনা । আর সাহিত্য পাতার সম্পাদকরাও ছিলেন দেশের প্রথমসারির কবিরা । তাদের হাতে লেখাটি বেরোবার আনন্দই ছিল আলাদা । জীবন ছিল সরল , চাহিদা ছিল সীমিত । পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার ছিল , স্কুলে ছিল স্কুল লাইব্রেরি ।পড়ার আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকা যেতো । প্রকৃতির উপরে এতো অত্যাচার হয়নি তখনো । প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অফুরন্ততার মধ্যে আমরা সময়টা উপভোগ করেছিলাম ।
বাংলা রিভিউ : আপনি কবিতায় মিথ, ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ ব্যবহার করা বিষয়ে কি ভাবেন? বিশেষত ইসলামিক বিষয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি ব্যবহার করা বিষয়ে।
তমিজ উদদীন লোদী : কবিতায় মিথ বা পুরাণের ব্যবহার দীর্ঘকালীন । আমাদের কবিতায় মিথ সবসময়েই ব্যবহৃত হয়েছে । একটা সময় এটি খুব প্রবল ছিল । ভারতীয় পুরাণ, যেমন মহাভারত , রামায়ণ । রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণী আত্মস্ত করেছেন , ব্যবহার করেছেন । তবে বহুল ব্যবহার হয়েছে মহাভারত । গ্রীক পুরাণ হোমারকৃত ইলিয়াড ও অডিসি ব্যবহৃত হয়েছে। শামসুর রাহমানের কবিতায় এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায় । ফররুখ আহমদের কবিতায় আরবী পুরাণ ও ইসলামী অনুষঙ্গ সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের কবিতায় এখনো নানা মিথের ব্যবহার লক্ষ করা যায় । এমনকি ইসলামিক বিষয়ও । আমাদের কবিতায় অন্যান্য মিথ ব্যবহার হলেও ইসলামিক মিথ ব্যবহারে এক ধরনের জড়তা লক্ষ করা যায় । যার কোনো কারণ নেই । মিথ ব্যবহারে সকল জড়তা ত্যাগ করে অবারিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি ।
বাংলা রিভিউ : আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতা বলতে আপনি কি বোঝেন? বাংলাদেশের কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।
তমিজ উদদীন লোদী : ইতোপূর্বে এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে । তবে আমি বরং আধুনিকতা বিষয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুবকে উদ্ধৃত করতে পারি ‘ আধুনিকতার ধারণা স্বভাবতই গতিশীল , ধাবমান । সেকালের যৌবনমদমত্ত আধুনিকতা একালে লোলচর্ম , পলিতকেশ ; আবার একালের ঝকঝকে আধুনিকতা পঁচিশ , পঞ্চাশ কি একশো বছর পরে বেজায় সেকেলে হয়ে যাবে ‘ । সুতরাং আধুনিকতা একটি বহমান প্রক্রিয়া কিংবা বিষয় । তবে আধুনিকের অন্যতম মূলভিত্তি জাতীয়তার ধারণাই আর টিকছে না , বহুজাতিক , বিশ্বায়নের ধারণা আসছে — অর্থনৈতিক কাঠামোকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে । আমাদের উত্তর আধুনিকতা যার থেকে উদ্ভব সেই ‘পোস্টমডার্ন ‘ সম্পর্কে প্রথমত বলা যায় । এ সম্পর্কে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘পোস্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য ‘ গ্রন্থে এর বিবরণ দিয়েছেন এভাবে –‘১৯১৭- য় Rudolf Panwitz একটি বইতে নিহিলিজম ও সে সময়কার ইয়োরোপে সব মূল্যবোধ ভেঙে যাওয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে শব্দটি ব্যবহার করেন । নীতসেকে অনুসরণ করে , তিনি নতুন পোস্টমডার্ন মানুষের কথা বলেন , যার দেখা পাওয়া যায় স্পষ্ট ভাবে ফ্যাসিবাদে । … নতুন পোস্টমডার্ন -এর প্রতিশ্রুতিময় ও ভীতিজনক দিক , দুইই ধরা দেয় , পোস্টমডার্ন বিশ্ব হয় সব কিছু দেয় , নয় কিছুই দেয় না ‘। এ নিয়ে এক একজন এক একরকম ব্যাখ্যা করেছেন । কেউ আধুনিকবাদ ও উত্তর আধুনিকবাদকে বিপরীত মেরুতে বসাচ্ছেন , কেউ আধুনিকতার সমালোচনা আধুনিকবাদেই আছে – এ সূত্রে উত্তর আধুনিকবাদ আধুনিকবাদেরই ধারাবাহিকতা ভাবছেন । এ এক দীর্ঘ আলোচনা । আমি শুধু বলবো আধুনিকতার যেমন শেষ হয়ে যায়নি তেমনি উত্তর আধুনিকতার বিষয়টিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই । বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেও একই বিষয় প্রযোজ্য ।
বাংলা রিভিউ : আপনার লেখালেখিতে দেশি-বিদেশি কবি/ সাহিত্যিকদের কারো কোন প্রভাব কি আছে?
তমিজ উদদীন লোদী : কবি শহীদ কাদরী প্রায়শই বলতেন, পৃথিবীর আদি কবি যে কবিতা লিখেছিলেন সেটিই শতভাগ মৌলিক কবিতা । তারপরে যিনি লিখেছেন তিনি কোনো না কোনোভাবে ঐ প্রথমজন দ্বারা প্রভাবিত । সে অর্থে প্রভাব থাকাটাই তো স্বাভাবিক । তবে এককভাবে কারো প্রভাব আছে বলে মনে হয় না ।
বাংলা রিভিউ : কোথায় আছেন? কি করছেন? পারিবারিক পরিচিতি জানতে চাই।
তমিজ উদদীন লোদী : গত প্রায় দেড় যুগ থেকে আমি প্রবাস জীবন যাপন করছি । যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আছি। ফেডারেল সরকারের অধীনে একটি চাকরি করছি । আমাদের তিনটি সন্তান । দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে । সবাই পড়ালেখা শেষে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত আছে ।
বাংলা রিভিউ : আপনি কখনো কি কোন পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিন অথবা সংকলন সম্পাদনা করেছেন? বিস্তারিত বলুন ।
তমিজউদদীন লোদী : হ্যাঁ , আমি একটি লিটল ম্যাগাজিন ‘ প্রপঞ্চ’ সম্পাদনা করেছি । এটি নিউইয়র্ক থেকে মূলত কবি শাহীন ইবনে দিলওয়ার-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল । কোভিডকালীন সময়ের কারণে এর পরবর্তী সংখ্যা আর বের করা যায়নি । তাছাড়া এখানকার সাপ্তাহিক ‘বাংলা পত্রিকা’র সাহিত্য পাতাটি দীর্ঘদিন থেকে দেখছি । এর আগে সাপ্তাহিক ‘ নিউইয়র্ক’-এর সাহিত্য পাতাও সম্পাদনা করেছি ।
বাংলা রিভিউ : লিটল ম্যাগাজিন এর সংজ্ঞা কি? এ নিয়ে আপনার ভাবনা বলুন।
তমিজ উদদীন লোদী : লিটল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞাটি এরূপ–‘শিল্পসাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে চলমান ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারা ও মতামত ব্যক্ত করার মুদ্রিত বাহনকে বলা হয় লিটল ম্যাগাজিন’ ।
এ ম্যাগাজিন সম্পর্কে বলা হয় –‘এ ম্যাগাজিন অনেকটা অনিয়মিত এবং অবাণিজ্যিক। লিটল ম্যাগাজিন প্রতিনিধিত্ব করে একটি ছোট সমমনা নব্য গোষ্ঠীর যার চিন্তা-ভাবনা-দর্শন চলমান ধারা থেকে ভিন্ন এবং অভূতপূর্ব। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় লিটল ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু।
ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাস মতে লিটল ম্যাগাজিনের অভিযাত্রা শুরু হয় Ralph Waldo Emerson ও Margaret Fuller সম্পাদিত The Dial (Boston, 1840-1844)-এর মাধ্যমে। ইমার্সনের নতুন দর্শন Transendentalism-এ যারা সমর্থক তাঁরাই শুধু Dial ম্যাগাজিনে লিখতেন। লিটল ম্যাগাজিনের আরেক প্রভাবশালী পত্রিকা ছিল ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত Savoy। ভিক্টোরীয়ান পুজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার উদারপন্থী ও সাম্যবাদী লেখকদের প্রধান বাহন ছিল এটি। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশ শতকের গোড়ার দিকে সবচেয়ে নামী লিটল ম্যাগাজিন ছিল Poetry: A Magazine of Verse (Chicago 1912)। এর সম্পাদক ছিলেন হেরিয়েট মনরো ও এজরা পাউন্ড।’
পাশ্চাত্যের আদলে বঙ্গদেশে প্রথম লিটল ম্যাগাজিন প্রবর্তন করন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র (১৯১৪)-কে আধুনিক লিটল ম্যাগাজিনের আদিরূপ বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (১৮৭২) বাংলা ভাষায় প্রথম লিটল ম্যাগাজিন।
আমি মনে করি নতুন কিছু কিংবা বৈপ্লবিক নবচেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য লিটল ম্যাগাজিনের কোনো বিকল্প নেই । এ ধারাটি শিল্প সাহিত্যের নবতর অগ্রগতির জন্য অব্যাহত রাখা প্রয়োজন । তাছাড়াও সমকালীন মেধাবী ও সৃষ্টিশীল তরুণ লেখকদের উচ্ছ্বাস, আনন্দ, চিন্তাভাবনার প্রতিফলনের জন্যও লিটল ম্যাগাজিনের প্রয়োজন অপরিহার্য ।
বাংলা রিভিউ : অনলাইন ম্যাগাজিন বা ওয়েব ম্যাগাজিন চর্চাকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন?
তমিজ উদদীন লোদী : এখনকার অন্যতম বাস্তবতা অনলাইন ম্যাগাজিন বা ওয়েব ম্যাগাজিন । হালে এমন সব ওয়েব ম্যাগাজিন লক্ষ করা যায় যেসব শিল্প সৌকর্যে , সমৃদ্ধ লেখায় দৃষ্টিনন্দন হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে । এটি প্রচলিত কাগজের বাইরে আলাদা একটি জগৎ সৃষ্টির প্রয়াসী । এই চর্চা অব্যাহত রাখা সময়েরই দাবী ।
বাংলা রিভিউ : “বাংলা রিভিউ” পড়েন? কেমন লাগে বা কেমন দেখতে চান–আগামীতে?
তমিজউদদীন লোদী : পড়ি এবং ভালো লাগে । এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি ।
বাংলা রিভিউ : ভবিষ্যতে কেমন পৃথিবী কল্পনা করেন?
তমিজ উদদীন লোদী : যদিও জানি এ হয়তো সম্ভব নয় , তবু বলি ভবিষ্যতের পৃথিবী হোক শান্তিময় । ধর্ম , বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক । মানবিকতায় উজ্জীবিত ও চর্চায় নিবিষ্ট হোক মানুষ ।
………
সাক্ষাৎকার গ্রহণে : সাজ্জাদ বিপ্লব
ডিসেম্বর ২৮, ২০২৪